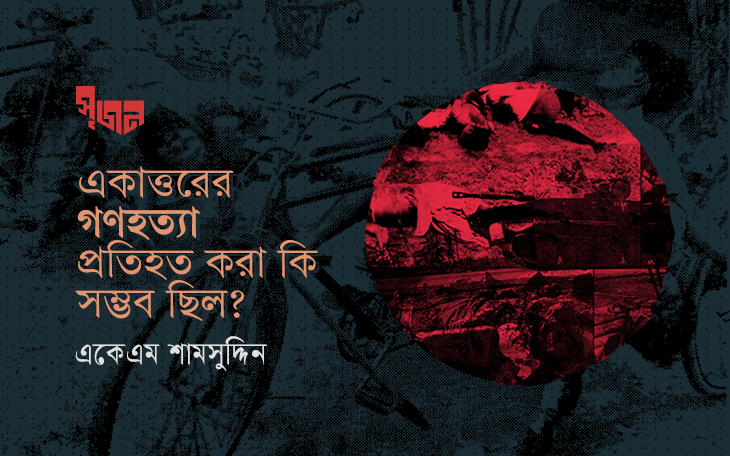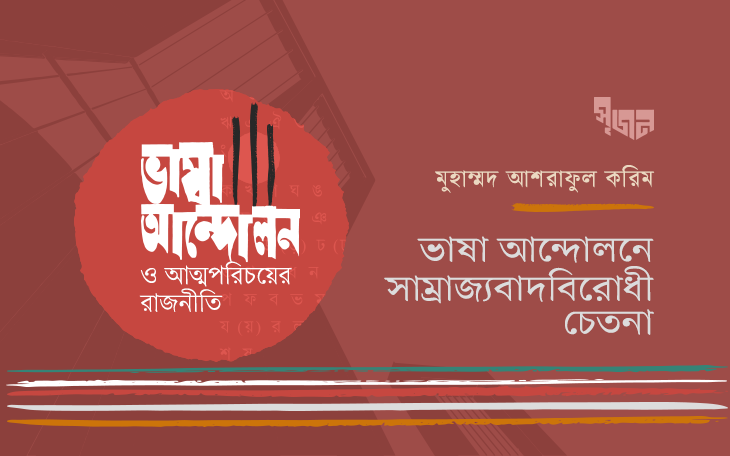গৌতম ঘোষের ‘পদ্মানদীর মাঝি’র চলচ্চিত্রায়নটি দেখে উপন্যাসটিকে আবার পাঠ করা গেল এবং আবারও বুঝলাম যে, যেমন বিষয়স্তুতে তেমনি উপস্থাপনায় এর দ্বিতীয়টি বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যাবে না। মানের দিক থেকে এটি বিশ্বমাপের। আমরা জানি যে, যত ভাষায় এই উপন্যাসের অনুবাদ হয়েছে, ততটা অন্য কোনও বাংলা উপন্যাস অনূদিত হয়নি। অধুনা-পরিচিত বিখ্যাত ল্যাটিন উপন্যাসগুলোর সঙ্গে এটি তুলনীয়।
তবু ‘পদ্মানদীর মাঝি’ যে অত্যন্ত অধিক পরিচিতি লাভ করেছে তা নয়। এর প্রধান কারণ বোধ করি এই যে, স্বদেশেই এ উপন্যাস যথোপযুক্ত মর্যাদা পায়নি। নিজের দেশেই যে অবহেলিত বিশ্ববাসী তাকে চিনবে কী করে? বাঙালির এ সম্পদটিকে জনপ্রিয় করার দায়িত্ব ছিল সাহিত্য সমালোচক, সম্পাদক ও সাহিত্যের অধ্যাপকদের। সে-দায়িত্ব পালনে অবহেলা ঘটেছে।
এ অবহেলা কেন ঘটল সে-ব্যাপারে অনিসন্ধিৎসু হলে আমরা উপন্যাসটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কাছে চলে যেতে পারব। সেটি হচ্ছে এর মৌলিকত্ব। পদ্মানদীর মাঝিরা প্রান্তবর্তী মানুষ। অবিভক্ত ভারতে পূর্ববঙ্গ নিজেই ছিল প্রান্তবর্তী, পদ্মার একেবারে গা-ঘেঁষে যে গরিব মানুষদের অবস্থান ও জীবনযাপন তারা একেবারেই শেষ প্রান্তের ঝুলন্ত মানুষ, তাদের ব্যাপারে ভদ্র বাঙালির কৌতূহলটা ছিল খুবই সামান্য। ভদ্র বাঙালি পদ্মার সুস্বাদু ইলিশ মাছের ব্যাপারে অবশ্যই আগ্রহী ছিল। কিন্তু জলে ভিজে ও ঘামে সিক্ত হয়ে অর্ধনগ্ন খেটে-খাওয়া যে মানুষরা ওই মাছ সরবরাহ করে সেই মানুষদের বিষয়ে কোনও ধরনের কৌতূহল অনুভব করেনি। মাছ কলকাতাতে যেত, কলকাতা মাছের স্বাদটা খুবই পছন্দ করত। কিন্তু জেলেদের গায়ের দুর্গন্ধ সহ্য করবার মতো উদারতা দেখানো ভদ্রলোকদের জন্য নিতান্তই অশোভন ছিল। ওই জীবন সম্পর্কে কল্পনা করতে গেলেও তারা অস্বস্তিতে পড়তেন। আর এ জীবনকে নিয়ে যে সাহিত্য তৈরি তার পক্ষে উপেক্ষার পাত্র হওয়াটা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। যা প্রত্যাশিত ছিল তা-ই ঘটেছে।
তদুপরি মাঝিদের এই জীবনকে যে কৃত্রিম সৌন্দর্যে ভূষিত করে তুলবেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে তেমন কাজ মোটেই সম্ভব ছিল না। অসাধারণ অন্তদৃর্ষ্টি, শিল্পবোধ, মাত্রাজ্ঞান ও নিজস্ব ভাষার ব্যবহারের সাহায্যে জেলেদের অতিশয় জীবনকে তিনি অসামান্যরূপে জীবন্ত করে তুলেছেন। কিন্তু সে-জীবন যতই জীবন্ত হোক, মোটেই আকর্ষণীয় নয়। মাঝিদের জীবনের রূপায়নটি তাই উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। মানিক জানেন যে জেলেপাড়ার মানুষেরা ‘জীবনযুদ্ধে জয়-পরাজয়ের একেবারে মিলন-সীমান্তে’ বসবাস করে, যেখানে ‘মিত্র তাহাদের কেউ নাই’। এমনকি সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষেরাও তাদের মিত্র নয়।
জেলেপাড়ার মালিক জমিদার মেজকর্তা এদের উপকার করতে চায়, মানুষগুলোকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করতে তার আগ্রহ দেখা গেছে। কিন্তু তাতে করে ওই মানুষদের উপকার যত না হয়েছে অপকার হয়েছে তার চেয়ে বেশি। বদনাম রটে গেছে যে জেলেদের ঘরের মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই মেজকর্তার আসল উদ্দেশ্য। বিপদে আপদে হোসেন মিয়া পাশে এসে দাঁড়ায়, ঝড়ে ঘরের চাল উড়ে গেলে শন দিয়ে সেটি ছেয়ে দেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে কাগজে টিপসই নিয়ে নেয়, পরে কাজ দেবে ভেবে। জেলেদের অসুবিধাই হোসেন মিয়ার জন্য সুবিধা হয়ে দেখা দেয়। কেননা সাগরের একটি ছোট দ্বীপের সে মালিক, সেখানে চাষাবাদের জন্য লোক প্রয়োজন। অসুবিধায় না পড়লে কোনও মানুষ কিছুতেই সেই দ্বীপে যেতে চায় না। অথচ লোক পাঠাতে না পারলে হোসেন মিয়ার উপনিবেশের ভবিষ্যৎ কোথায়?
অসাধারণ অন্তদৃর্ষ্টি, শিল্পবোধ, মাত্রাজ্ঞান ও নিজস্ব ভাষার ব্যবহারের সাহায্যে জেলেদের অতিশয় জীবনকে তিনি অসামান্যরূপে জীবন্ত করে তুলেছেন। কিন্তু সে-জীবন যতই জীবন্ত হোক, মোটেই আকর্ষণীয় নয়। মাঝিদের জীবনের রূপায়নটি তাই উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। মানিক জানেন যে জেলেপাড়ার মানুষেরা ‘জীবনযুদ্ধে জয়-পরাজয়ের একেবারে মিলন-সীমান্তে’ বসবাস করে, যেখানে ‘মিত্র তাহাদের কেউ নাই’। এমনকি সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষেরাও তাদের মিত্র নয়।
উপন্যাসে উপমার ব্যবহার সীমিত। কিন্তু ‘পদ্মানদীর মাঝি’ পড়ার, এবং গৌতম ঘোষের চলচ্চিত্রায়নে তার সঙ্গে নতুনভাবে পরিচিত হওয়ার সময়ে একটি উপমা আপনা থেকেই তৈরি হয়, সেটা হল জালের। একটি নয়, একাধিক জালের যাদের ভেতরে মাঝিরা সবাই নানাভাবে বন্দি। পদ্মানদী তার বুকের ভেতর লালিত-পালিত ইলিশ মাছকে যেমন মুক্তি দেয় না, তেমনি আটক করে রাখে জেলেদেরও। এ জাল থেকে বের হয়ে যেতে হলে হোসেন মিয়ার মতো হতে হয়, যে লোকটি মাঝিদের সঙ্গেই ওঠাবসা করে বটে। কিন্তু এখন আর মাঝি নেই, পরিণত হয়েছে ব্যবসায়ীতে।
হোসেন মিয়া নিয়ম নয়, ব্যক্তিক্রম। সে সমুদ্র দেখেছে, জাহাজে ঘুরেছে এবং কেবল যে পণ্য বেচাকেনা করে তা নয়, তার প্রধান উপার্জন আফিমের চোরাচালান থেকে। তার মতো দুঃসাহসী মানুষ মাঝিদের মধ্যে দ্বিতীয়টি নেই। কাউকে সে ডরায় না, অন্যরা ভয়-ডরে সর্বদাই কম্পমান। অন্যসব জেলেরা সবাই বন্দি, তারা বড় জোর কেরায়া নায়ের মাঝি হতে পারে। কিন্তু তার বাইরে যে যাবে এমন সাধ্য তাদের নেই। প্রধান বন্ধন দারিদ্র্যের। জন্ম এদের দরিদ্র ঘরে, মৃত্যুও ঘটে দরিদ্র অবস্থায়। পদ্মা সমুদ্রের মতো বিশাল, কিন্তু অসহায় মাঝিদের কে সে তো মুক্তি দেয় না। মরসুম শেষ হয়ে গেলে পদ্মায় ইলিশ পাওয়া যায় না। ওদিকে নদী উঠে আসে ভূমিতে, বন্যা হয়ে; পদ্মার ঝড় জেলেপাড়ায় ঢুকে ঘরবাড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেয়, গাছ পড়ে উপড়ে, প্রাণহানি ঘটে মানুষের।
জমিদার আছে, আছে তার মুহুরি, যাদের তুষ্ট রাখতে হয়। নতুন একটি ঘর তুলতে গেলেও জমিদারের অনুমতি প্রয়োজন। তার দরবারে গেলে যুক্তকর ‘মুক্ত করিবার’ নিয়ম নাই। রাষ্ট্রের জালও কম শক্ত নয়। থানা আছে, রয়েছে দারোগা-পুলিশ। তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে এবং ছিদ্র পেলেই জেলেদের জীবনে প্রবেশ করে নানা ধরনের অনাসৃষ্টি ঘটায়।
স্বাভাবিক নিয়মেই মেয়েরা বন্দি দুই দফায়। প্রথমত জেলে পরিবারের মানুষ হিসেবে, দ্বিতীয়ত নারী হিসেবে। কুবেরের স্ত্রী মালা যেন সব ছেলেমেয়ের প্রতিনিধি। তার নিজের মধ্যে বহু গুণ আছে, সে প্রাণবন্ত, মা হিসেবে সম্পূর্ণ সফল, স্বামীর প্রতি কর্তব্য প্ররায়ণতায় একনিষ্ঠ। মালার ভেতরে চাঞ্চল্য আছে, সে চমৎকার গল্প বলতে পারে, কুবেরের পিসির সে যত্ন নেয়, মা-বাবা ভাইবোনের মঙ্গল চিন্তায় সে উদ্বিগ্ন থাকে। তার গায়ের রং অন্য মেয়েদের তুলনায় ফর্সা। কিন্তু সে পঙ্গু। বাইরের জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। ভেতরে আকাক্সক্ষা ডাক্তার দেখানোর, কিন্তু সে-সুযোগ তার ভাগ্যে নেই। অসুস্থ মেয়েকে ফেরত নিয়ে আসতে অন্যদের সঙ্গে নৌকায় করে সেও গিয়েছিল সদর হাসপাতালে, সেই ফাঁকে ডাক্তারকে নিজের পা’টা দেখানোর ইচ্ছা। সেই যাওয়া নিয়ে কুবেরের সে কী হম্বিতম্বি। মালাও জবাব দিয়েছে, যদিও ওই একবারই। কিন্তু ডাক্তার তো বলে দিয়েছে যে তার পা সারার নয়। মালা সেটা মেনে নিয়েছে। নিতেই হয়। কুবের তো শেষ পর্যন্ত ময়নাদ্বীপে পালাতে পারে, যদিও মুক্ত হতে নয়, হোসেন মিয়ার জালের ভেতর বন্দি হতেই, তবু তো চেষ্টাটা থাকে মুক্তির, মালার জন্য তেমন কোনও পথ খোলা নেই।

কিন্তু তার ছোট বোন কপিলা মেনে নেয়নি নিজের অবস্থা ও অবস্থান। তারও বিয়ে হয়েছিল অল্পবয়সে। দু’বছর আগে একটি সন্তানের জন্ম দেয় সে, আঁতুড় ঘরেই যার মৃত্যু ঘটেছে। স্বামী আবার বিয়ে করেছে, রাগ করে কপিলা চলে এসেছে বাপের বাড়িতে। দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী আবার তাকে নিয়ে গেছে। কিন্তু আবারও সে চলে এসেছে। এ উপন্যাসে সবচেয়ে প্রাণবন্ত মানুষটি হচ্ছে এই কপিলা। হোসেনের মতো সেও কাউকে ডরায় না। উপস্থিত বুদ্ধি তার অসাধারণ। পদ্মার মতোই তার স্বভাবে আছে রহস্যময়তা। সেবাতে সে নিপুণা। বচনে অদ্বিতীয়। ভগ্নিপতি কুবেরকে ঠাট্টা করে ভীতু বলে। চুরির অভিযোগে কুবেরকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ যখন ওঁৎ পেতে বসে থাকে; রাতের অন্ধকারে অন্য কেউ নয় সে-ই নদীর ঘাটে গিয়ে কুবেরকে সতর্ক করে দেয় এবং খুব সকালে কুবের যখন জেলখাটতে অসম্মত হয়ে হোসেন মিয়ার নৌকাতে ওঠে ময়নাদ্বীপ যাওয়ার জন্য, কপিলা তার সঙ্গী হয়, সেই ভয়াবহ অজানার পথে।
এ আবদ্ধ দশাতে মেয়েদের জন্য প্রধান সমস্যা বিয়ে। বিয়ের বাইরে তদের করার মতো কাজ নেই, বিয়ে নিয়েই তাদের মায়েদের যত চিন্তা এবং বিয়ের পরে মেয়েটি কেমন আছে সে-বিষয়ে উদ্বেগ। মাঝিরা ইলিশ মাছ ধরে, সে মাছ গুনে গুনে হিসাব করে চালান হয়। মেয়েরাও চালানের পণ্যের মতোই বিক্রি হয়ে যায়। তাদের দাম ওঠানামা করে, রূপ ও গুণের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। ক্রেতার সংখ্যা অল্প,তাই মেয়েটিকে নিলামে যে চাড়ানো হবে এমন উপায় নেই, দরকষাকষিটা চলতে থাকে পারিবারিকভাবে। মেয়েটির ইচ্ছা অনিচ্ছাকে কোনও দাম দেয়ার নিয়ম নেই। এমনই অসহায় তারা, এমনই সীমিত তাদর বিয়ের বাজার। রাতেরবেলা পুরুষেরা ঘরে থাকে না, তারা নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করে মহাজনদের কাছে, এমন মাঝির কাছেও যার একটি নৌকা আছে। এ রাজ্যে নৌকার খুব দাম। মালার মতো আকর্ষণীয় যদি হয় কোনও মেয়ে তা হলে তার পঙ্গুত্ব সত্ত্বেও, হয়তো-বা পুঙ্গত্বের কারণেই, তার নামে কানাঘুষা চলতে থাকে।
সব মিলিয়ে মনে হয় এ জীবন বড় আদিম। কিন্তু আদিম নয়, আসলে দরিদ্র। এরা গান বাঁধে, মিলিত কণ্ঠে গান গায়, উৎসবে যোগ দেয়, হাসপাতালে যায়, সদরে গিয়ে নিরুপায় হয়ে হোটেলে থাকে, বন্দর থেকে বন্দরে পণ্য ও মানুষ বহন করে। পরস্পরের প্রতি এদের সহানুভূতিতে কোনও সংকীর্ণতা থাকে না। কিন্তু এদের সামনে কোনও ভবিষ্যৎ নেই। শিক্ষা নেই, চিকিৎসা নেই। মুক্তির কোনও পথ জানা নেই। ভবিষ্যতের কথা ভাবে না, ভাবার মতো সাহস রাখে না। ডরায়।
গৌতম ঘোষকে অভিনন্দন তিনি একটি অতিপ্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ সম্পন্ন করেছেন। নইলে ‘পদ্মানদীর মাঝি’র এই চমৎকার চলচ্চিত্ররূপায়ণ থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম। সাহিত্যকে চলচ্চিত্রে নিয়ে আসার কাজটি সহজ নয়, ‘পদ্মানদীর মাঝি’র চলচ্চিত্রায়ন বিশেষভাবেই কঠিন। নদী এখানে সমুদ্রের মতো বিস্তৃত। কিন্তু মানুষের জীবন অত্যন্ত সংকীর্ণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যেমন মাঝিদের জীবনেও তেমনি বৈচিত্র্যের ভীষণ অভাব।
সময় তাই বলে স্থির থাকে না, সে বদলায়। জমিদারির তুলনায় ব্যবসায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জমিদার অনন্ত তালুকদার পিছু হটে যায়, সামনে এগিয়ে আসে হোসেন মিয়া, একদিন সে সামান্য মাঝি ছিল, এখন সে বড় ব্যবসায়ী। জেলে পাড়ায় হোসেন মিয়ার যে কদর জমিদার মেজকর্তা তার এক দশমাংশও পায় না। কেননা হোসেন মিয়ার কোনও মান-অভিমান নেই, অনায়াসে সে মিশে যেতে পারে মাঝিদের সঙ্গে, ঘুমিয়ে পড়তে সংকোচ নেই তাদের ঘরের চাটাইতে শুয়ে। তার থলিতে আছে কাঁচা টাকা, তা দিয়ে সে মাঝিদের খাটায়, দুচার পয়সা যে চুরিও যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল রাখার মতো সময় তার নেই। সে কাজের মানুষ। কিন্তু কাজের ফাঁকে মন ভালো থাকলে চমৎকার গান বাধে এবং গান গায়; প্রেমের গান নয়, ব্যক্তি মাঝির ঘুম-ভাঙানোর গান। সামন্তবাদের সীমানা ডিঙিয়ে পুঁজিবাদের যে অভ্যুদয় হোসেন মিয়া তার প্রতিনিধি। সে জমি কেনে না। সমুদ্রে দ্বীপ কেনে নিলামে এবং সেখানে একটি উপনিবেশ গড়তে চায়। দ্বীপটি নিচু, জঙ্গল ও পোকামাকড়ে আকীর্ণ। সেখানে সে বসতি গড়ে তুলবে, অসহায় মানুষদের জালে ফেলে ধরে নিয়ে গিয়ে। আমিনুদ্দি মাঝি একদা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিল যে সে কখনও ময়নাদ্বীপে যাবে না,Ñ ঘর ও স্ত্রী হারিয়ে সেও শেষ পর্যন্ত দ্বীপাভিমুখে রওনা দেয়। রাসু গিয়েছিল দ্বীপে, স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যাকে হারিয়ে কোনমতে জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছে কেতুপুরে। কুবেরের একমাত্র মেয়ে গোপাকে বিয়ে করে যে সংসার পাততে চায়, কুবের তার মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দেয়াতে প্রতিশোধ নেয় নিজের মামার বাড়ি থেকে চুরি-করা টাকা-পয়সা জমানোর পিতলের ঘটিটি কুবেরের পিসির ঘরে লুকিয়ে রেখে। খবর পেয়ে থানা থেকে পুলিশ আসে। কে জানে হোসেন মিয়াই খবরটি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছিল কিনা; কুবেরকে তো তার খুবই দরকার তার উপনিবেশে। হোসেন মিয়া মোটেই পাষাণ হƒদয় নয়, কিন্তু জাল ফেলে মাছ ধরার বেলায় মাঝির তো মাছের প্রতি ভালোবাসা দেখানোর সুযোগ থাকে না। হোসেন মিয়াই ত্রাতা হয়ে দেখা দেয় কুবেরের জন্য; থানা পুলিশ সে-ই সামলাবে, কুবেরের পরিবারের দেখভাল করার দায়িত্বও তাই। মেয়েদের ভেতর যেমন কপিলা, পুরুষদের ভেতর তেমনি হোসেন মিয়াও অদ্বিতীয়। কিন্তু কপিলা যেহেতু নারী তাই তার ক্ষমতা অনেক কম, সেজন্য হোসেন মিয়া দ্বীপে গিয়েই তাকে আশ্রয় খুঁজতে হয়।
হোসেন মিয়া নিজে অধার্মিক নয়। কিন্তু তার উপনিবেশ যে সম্পূর্ণ হবে অসাম্প্রদায়িক সে-সিদ্ধান্ত সে অটল। সেখানে মসজিদ মন্দির থাকবে না, মোল্লা-পুরোহিতের প্রয়োজন দেখা দেবে না। হোসেন মিয়া ধর্মীয় সাম্প্রদয়িকতার বিভাজন তৈরিতে সাহায্য করবে না। উপনিবেশে সে সাম্প্রদয়িক বিভেদ চায় না, ঠিক সেই কারণে যে-কারণে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকেরা ভারতে সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহিত করেছিল। কারণটি হচ্ছে উপনিবেশ গড়ে তোলা ও তাকে রক্ষা করা। তার দ্বীপে এমনিতেই অনেক ঝগড়া-ফ্যাসাদের আশংকা, সেখানে ধর্মীয় কলহের আমদানি তার জন্য ক্ষতিকর হবে, এটা সে বোঝে; ঠিক যেভাবে ব্রিটিশরা বুঝেছিল যে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষীয়দের ভাগ করে ফেলা গেলে তারা নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ বাধাবে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিবর্তে। হোসেন মিয়া পদ্মাকে ডরায় না, ওই নদীকে সে তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। সাহসের দিক থেকে কপিলা ভিন্ন অন্য কেউ তার সঙ্গে তুলনীয় নয়। কথাবার্তায় এ দু’জনেই সর্বাধিক উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। কিন্তু কপিলা যেহেতু নারী তাই তার জন্য জয়ের সম্ভাবনা হোসেন মিয়ার তুলনায় সংকীর্ণ হতে বাধ্য। বাস্তবেও সেটাই ঘটে। হোসেন মিয়ার উপনিবেশই শেষ পর্যন্ত কপিলার জন্য গন্তব্যে পরিণত হয়। হোসেন মিয়া ক্ষমতাধর, কেননা তার হাতে টাকা আছে এবং সে পুরুষ। ঘরে তার দ্বিতীয় বউ।
বড় মাপের শিল্পকর্ম দর্শক-পাঠক-শ্রোতাকে কেবল যে আনন্দ দেয় তা নয়, চিন্তিতও করে। চলচ্চিত্রে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ আমাদের উপভোগের আনন্দ দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত করে তবে ছাড়ে। ছবিটি দেখে উপন্যাসটি আবার পড়ার আগ্রহ তৈরি হয়, যেমনটি আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ বারবার পড়ার মতো রচনা। এখানে মাঝিদের জীবনের গভীর বেদনা ও সীমিত স্বপ্নের যে রূপায়ণ ঘটেছে তা আমাদের নাড়িয়ে দেয়।
গৌতম ঘোষকে অভিনন্দন তিনি একটি অতিপ্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ সম্পন্ন করেছেন। নইলে ‘পদ্মানদীর মাঝি’র এই চমৎকার চলচ্চিত্ররূপায়ণ থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম। সাহিত্যকে চলচ্চিত্রে নিয়ে আসার কাজটি সহজ নয়, ‘পদ্মানদীর মাঝি’র চলচ্চিত্রায়ন বিশেষভাবেই কঠিন। নদী এখানে সমুদ্রের মতো বিস্তৃত। কিন্তু মানুষের জীবন অত্যন্ত সংকীর্ণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যেমন মাঝিদের জীবনেও তেমনি বৈচিত্র্যের ভীষণ অভাব। এ জীবনে দুঃখ-হাসির ছোট ছোট ঘটনা আছে। কিন্তু নাটকীয়তা নেই, অতিনাটকীয়তা যে জায়গা করে নেবে সে সুযোগ একেবারেই অনুপস্থিত। লেখকের ভাষা অত্যন্ত যথাযথ। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আড়ম্বরহীন। তার আছে সেই অন্তদৃর্ষ্টি, কৌতূহল এবং শিল্পের বোধ যার সাহায্যে তিনি চরিত্রগুলোকে পুরোপুরি জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। গৌতম ঘোষও ঠিক সেই কাজটিই করেছেন। তার রচিত চিত্রনাট্য উপন্যাসের বাইরে যায়নি। যে সংলাপগুলো যোগ করা হয়েছে সেগুলো যদি ঔপন্যাসিক নিজেও লিখতেন তবে ভিন্ন রকমের হতো না। চিত্রগ্রহণের দক্ষতা চলচ্চিত্রটিকে একই সঙ্গে জীবন্ত ও গভীর করে তুলতে সহায়ক হয়েছে। বিশেষভাবে মনে পড়ে একটি দৃশ্য যেখানে কুবের মালার গায়ে জ্বলন্ত কলকে ছুড়ে মারে, মালা চীৎকার করে ওঠে এবং এক পায়ে ভর দিয়ে উঠে কুবেরের চুল ধরে টানতে থাকে। পরে বিছানায় শুয়ে কুবের মালার মাথায় হাত রাখে, মাফ চায় এবং মালাকে বুকে টেনে নেয়।
অভিনয়ের জন্য শিল্পী নির্বাচন যেমনটা ঘটেছে তার চেয়ে ভালো হতে পারত না। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হোসেন মিয়ার চরিত্রে উৎপল দত্তের অভিনয়। ওই ভাবুক, কল্পনাপ্রবণ এবং চতুর ও বাস্তববাদী মানুষটিতে তিনি যেভাবে উপস্থিত করেছেন তা ভুলার নয়। রাইসুল ইসলাম আসাদ, গুলশান আরা চম্পা ও রুপা গাঙ্গুলী সম্পূর্ণরূপে চরিত্রানুগ।
বড় মাপের শিল্পকর্ম দর্শক-পাঠক-শ্রোতাকে কেবল যে আনন্দ দেয় তা নয়, চিন্তিতও করে। চলচ্চিত্রে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ আমাদের উপভোগের আনন্দ দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত করে তবে ছাড়ে। ছবিটি দেখে উপন্যাসটি আবার পড়ার আগ্রহ তৈরি হয়, যেমনটি আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ বারবার পড়ার মতো রচনা। এখানে মাঝিদের জীবনের গভীর বেদনা ও সীমিত স্বপ্নের যে রূপায়ণ ঘটেছে তা আমাদের নাড়িয়ে দেয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল ইতিহাসকে নিয়ে আসেননি, ক্রান্তিকালের বিড়ম্বনাকেও তুলে ধরেছেন। জেলেদের পেশা বদল করতে হচ্ছে, মাছ ধরার ওপর আর নির্ভর করা যাচ্ছে না; জমিদার হটে যাচ্ছে এগিয়ে আসছে ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী যা পারে জমিদার তা পারে না। কিন্তু মাঝিদের মুক্তি নেই; না নদীতে না নদীর পাড়ে। তাদের নতুন আবাসেরও খোঁজ করতে হবে, দূর দেশে, অজানা প্রান্তে। কিন্তু তাদের জন্য মুক্তি আসবে না, বেষ্টনকারী জালগুণো যদি ছিন্ন করা যায়।