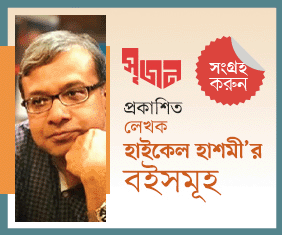যখন আমি মহাকাশ নিয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা দিই এবং হাবল স্পেস টেলিস্কোপ বা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (JWST) এর সর্বশেষ চমকপ্রদ ছবিগুলো দেখাই, তখন আমাকে সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্নটি করা হয় তা হলো—”এগুলো কি আসলে বাস্তবে এরকমই দেখতে?” এর সাধারণ অর্থ: আপনি যদি নিজ চোখে এই বস্তুগুলো দেখতেন, তাহলে কি এরকমই দেখাতো?
এর উত্তরটি প্রায় সবসময়ই “না” হয়ে থাকে। তবে এটা না যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ছবি জালিয়াতি করছেন! বরং ক্যামেরা (বিশেষ করে টেলিস্কোপের) এবং চোখ কাজ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে। আপনার স্মার্টফোনে তোলা ছবিসহ কোনো ফটোগ্রাফই পুরোপুরি চোখে দেখা দৃশ্যের প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে না। আমাদের প্রযুক্তি সর্বোচ্চ যা করতে পারে তা হলো চোখের দেখা দৃশ্যের কাছাকাছি কিছু তৈরি করা—আর কখনো কখনো আমরা সেটাও করতে চাই না।
মানুষের চোখের রেটিনায় দুই ধরনের কোষ থাকে—রড ও কোণ (কোন)। রড কোষ রং শনাক্ত করতে পারে না, তবে কম আলোতে কাজ করে (এজন্য অধিকাংশ নক্ষত্রের ম্লান আলো খালি চোখে সাদা দেখায়)। আর কোণ কোষ রং চিনতে সাহায্য করে, এবং এগুলো তিন ধরনের: প্রতিটি কোণ কোষ লাল, সবুজ বা নীল আলোর প্রতি সংবেদনশীল। কোনো বস্তু দেখার সময় আমরা যে রং অনুভব করি তা আসলে এই কোণ কোষগুলোর শনাক্ত করা আলোর মিশ্রণ। অবশ্যই, বাস্তব প্রক্রিয়াটি এখানে বর্ণনার চেয়ে অত্যন্ত জটিল, তবে সারমর্ম এটাই।
জ্যোতির্বিদ্যার ক্যামেরাগুলো সাধারণত পুরো দৃশ্যপটে বড় লাল, সবুজ ও নীল ফিল্টার ব্যবহার করে (স্মার্টফোনের পিক্সেল-ভিত্তিক ফিল্টারের বিপরীতে), কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল প্রায় একই। যাই হোক, এই ফিল্টারগুলো চোখের রং শনাক্ত করার ক্ষমতার সাথে পুরোপুরি মেলে না, তাই ছবিটি আপনার চোখের দেখা দৃশ্যের মতো হুবহু নয়। তবুও এটি খুব কাছাকাছি
ডিজিটাল ক্যামেরাও এই পদ্ধতির অনুকরণ করতে পারে। আলো-সংবেদনশীল জৈবিক কোষের বদলে এদের ক্ষুদ্র পিক্সেল থাকে, যা মূলত প্রতিটি ফোটন (আলোক কণা) গণনা করে এবং ইলেকট্রনিকভাবে সংরক্ষণ করে। এই সিস্টেমে, উজ্জ্বল বস্তু (যা বেশি আলো নির্গত করে) অধিক ফোটন ধারণ করে। তবে পিক্সেল নিজে থেকে রং আলাদা করতে পারে না। এগুলো শুধু ফোটন শনাক্ত করে রেকর্ড করে। রংয়ের তথ্য পেতে প্রতিটি পিক্সেলের ওপর একটি ফিল্টার বসানো হয়, যা লাল, সবুজ বা নীল বর্ণালির নির্দিষ্ট রঙের আলোই কেবল প্রবেশ করতে দেয়। কাঁচা পিক্সেল (ক্যামেরার সেন্সরে প্রতিটি পিক্সেল দ্বারা শনাক্ত হওয়া ফোটনের প্রাথমিক (অপরিশোধিত) ডেটা। এখানে “কাঁচা” বলতে কোনো প্রসেসিং ছাড়া সরাসরি ক্যামেরা সেন্সর থেকে পাওয়া ডেটা বোঝায়।) -ভিত্তিক ফোটন গণনার পর এই তথ্য বাছাই ও যোগ করে রঙিন ছবি তৈরি হয়।
একে “তিন-রঙের ছবি” বলা হয়, যা চোখে দেখা দৃশ্যের কাছাকাছি। জ্যোতির্বিদ্যার ক্যামেরাগুলো সাধারণত পুরো দৃশ্যপটে বড় লাল, সবুজ ও নীল ফিল্টার ব্যবহার করে (স্মার্টফোনের পিক্সেল-ভিত্তিক ফিল্টারের বিপরীতে), কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল প্রায় একই। যাই হোক, এই ফিল্টারগুলো চোখের রং শনাক্ত করার ক্ষমতার সাথে পুরোপুরি মেলে না, তাই ছবিটি আপনার চোখের দেখা দৃশ্যের মতো হুবহু নয়। তবুও এটি খুব কাছাকাছি।
এটি একটি সুন্দর ফটোগ্রাফ তৈরি করার জন্য যথেষ্ট—যদি আমরা চোখে দেখা দৃশ্যের অনুরূপ ছবি তুলতে চাই। আমরা এগুলিকে “সত্যিকারের রং” বলি, যদিও প্রযুক্তিগতভাবে এটি নামের ভুল প্রয়োগ, কারণ এটি আসলে একটি আনুমানিক ব্যাপার।
মহাজাগতিক বস্তুর এমন ছবি সুন্দর (এবং জনপ্রিয়) হলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এর ব্যবহার সীমিত। এর জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সাধারণত রং-ফিল্টার করা ছবিগুলো আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করতে পছন্দ করেন, সেগুলোকে তিন-রঙের ছবিতে মিশ্রিত করার চেয়ে।
কারণ, “রং” এর গুরুত্ব কেবল সুন্দর ছবি তৈরি করার চেয়ে অনেক বেশি। সূর্য বিস্তৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আলো বিকিরণ করে—যাকে আমরা অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী বলি। যখন আমরা একটি ফুল দেখি, এটি সেই আলোর বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মিশ্রণ প্রতিফলিত করে, যা আমরা রং হিসেবে দেখি। বেশিরভাগ নক্ষত্রও অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী নির্গত করে, তবে সব মহাজাগতিক বস্তু তা করে না।
উদাহরণস্বরূপ, একটি গ্যাসের মেঘে থাকা হাইড্রোজেন খুব নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে (সাধারণত ৬৫৬ ন্যানোমিটারে, যা বর্ণালীর লাল অংশে অবস্থিত) আলো বিকিরণ করে। এরকম নির্গমন একটি “রেখা বর্ণালী” (line spectrum) তৈরি করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যদি জানতে চান নীহারিকার মধ্যে হাইড্রোজেন কোথায় রয়েছে, তাহলে তারা “সংকীর্ণ-ব্যান্ড ফিল্টার” ব্যবহার করেন, যা শুধুমাত্র সেই নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকেই ডিটেক্টরে পৌঁছতে দেয়। এই ফিল্টারগুলোকে গ্যাসের মেঘে থাকা বিভিন্ন পরমাণু বা অণু থেকে নির্গত আলো শনাক্ত করার জন্য সামঞ্জস্য করা যায়, যার মাধ্যমে মেঘের গঠন, তাপমাত্রা, ঘনত্ব, কাঠামো ইত্যাদি পরিমাপ করা সম্ভব।
আপনি যেসব নীহারিকার ছবি দেখেন, সেগুলোর বেশিরভাগই এই সংকীর্ণ ফিল্টারের সমন্বয়ে তৈরি। তাই, এই ছবিগুলোর চেহারা আপনার খালি চোখে দেখা দৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—এমনকি যদি আপনি সেখানে ভেসে থাকতেন তবুও! ইমেজিং প্রক্রিয়া ভিন্ন, তাই ছবিও ভিন্ন দেখায়। আর এতে কোনো সমস্যা নেই! জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কাউকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন না। আসল কথা হলো, এই বস্তুগুলো এমনভাবে আলো বিকিরণ করে যা আমাদের চোখের অভ্যস্ত অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর মতো নয়। তবুও আমরা সেগুলো দেখতে চাই—এবং এই ছবিগুলো সেই উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়।
এই প্রক্রিয়াটির জন্য আমি কোনো সঠিক নাম পাইনি। “মিথ্যা রং” (false color) কিছুদিন জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু এটি এখন অপছন্দ করা হয়, কারণ এটি “জালিয়াতি”র ইঙ্গিত দেয়। “অস্বাভাবিক রং” (unnatural color) আরও খারাপ। যাই হোক, নামের সমস্যা সত্ত্বেও এই প্রযুক্তির মূল্য অপরিসীম, কারণ এটি বিভিন্ন ধরনের আলোকে ছবিতে রূপান্তর করতে সাহায্য করে। কিছু ক্যামেরা ডিটেক্টর অবলোহিত (ইনফ্রারেড) আলো শনাক্ত করতে পারে—এটি শুধু JWST-ই নয়, নতুন স্মার্টফোনেও থাকে। কিছু ডিটেক্টর অতিবেগুনি (আল্ট্রাভায়োলেট), এক্স-রে বা অন্যান্য অ-দৃশ্যমান আলো ধরতে পারে।
এভাবে তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালীর বিভিন্ন অংশ থেকে আলো মিশিয়ে ছবি তৈরি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি এমন ছবি বানাতে পারেন যেখানে অতিবেগুনি আলো নীল, দৃশ্যমান আলো সবুজ এবং অবলোহিত আলো লাল হিসেবে দেখানো হয়। স্যাটেলাইট ছবিতে এটা দেখা যায়: গাছপালা অবলোহিত আলো প্রতিফলিত করে, তাই সেগুলো চোখের দেখা সবুজের বদলে উজ্জ্বল লাল দেখায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছবিতেও একই রকম হয়—প্রায়ই আরও বেশি রং ব্যবহার করা হয়। যেমন, হাবলের অনেক ছবিতে পাঁচ বা ততোধিক ফিল্টার ব্যবহার করা হয়, যার প্রতিটিকে আলাদা রং বরাদ্দ করা হয়। এর ফলে চূড়ান্ত ছবি অত্যন্ত প্রাণবন্ত দেখায়, যদিও সেগুলো আপনার চোখের দৃষ্টিতে “সত্যিকারের রং” নয়।
শেষ কথা হলো, ফটোগ্রাফ তৈরির পদ্ধতি নির্ভর করে তার ব্যবহারের ওপর। কখনো বিজ্ঞানীরা একক ফিল্টার, আবার কখনো একাধিক ফিল্টার ব্যবহার করেন—বা কিছুই না—যা তারা পরিমাপ করতে চান তার ভিত্তিতে। আর আপনি বিশ্বজুড়ে (এবং মহাকাশে) থাকা টেলিস্কোপ থেকে যেসব ছবি দেখেন, সেগুলো নানাভাবে তৈরি করা হয়, তারপর সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাড়ানো হয়।
আপনি যুক্তি দিতে পারেন যে এগুলোর কোনোটিই “সত্যিকারের রং” ধারণ করে না। কিন্তু আবার, যদি সত্যিকারের রং হতো, তাহলে এগুলো বিভিন্ন অদৃশ্য আলো বিকিরণ বা প্রতিফলনকারী বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করতে পারত না। তাই এই অর্থে, এরা সবই সত্য!
মূল: মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান ব্লগার ফিলিপ ক্যারি প্লেইট ।
অনুবাদ: মেজবাহ উদ্দিন
সূত্র: সাইন্টিফিক আমেরিকান