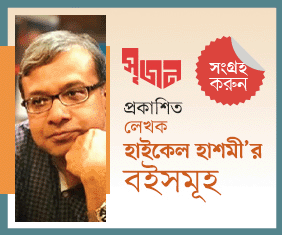অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি ভেনিসে পা রেখেছিলাম এক রৌদ্রোজ্জ্বল গ্রীষ্মের দুপুরে। যাত্রীবোঝাই পাবলিক বাসে চেপে যাত্রা করলাম সেন্ট মার্কোসের উদ্দেশে। সেন্ট মার্কোসে অবস্থিত বিখ্যাত স্থাপত্য ক্যাথেড্রাল। ক্যাথেড্রালের চারদিকের দেয়াল সুসজ্জিত কারুকার্যে খচিত। চিত্রকর্ম ও অক্ষরে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন কাহিনি মুগ্ধতা তৈরি করে। এখানেই ভেনিসের প্রাণভোমরা, সেই বিখ্যাত গ্র্যান্ড ক্যানেল যা যুক্ত করেছে শতাধিক জলরাশিকে। বিশাল খাল ভেনিসকে সাপের মতো পেঁচিয়ে আছে। এ খালের এক প্রান্তে সেন্ট মার্ক বেসিন, অন্য প্রান্তে সান্তা লুসিয়া রেলস্টেশন। ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এ জলরাশির পাশে অবস্থান নিয়েছে প্রায় ১৭০টি ভবন। এগুলো নির্মিত হয়েছে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝে। এ ভবনগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন পণ্যের দোকান। ভেনিসের ঐতিহ্যসম্পন্ন স্যুভেনির কেনার জন্য পর্যটকদের ভিড় সেখানে। ইতালীয় উচ্চারণে ভেনিস এখানে ‘ভেনেজা’।
বিস্ময়ের অলিগলি বেষ্টিত জলপথ ভেনিসকে পরিণত করেছে ‘সিটি অব লাভ অ্যান্ড লাইটস’ অর্থাৎ ‘ভালোবাসা ও আলোর নগরীতে’। তার বিস্তৃতিও ইউরোপের ৬টি বৃহত্তম নগরীর মধ্যে অন্যতম। অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলে ইতালির ভেনিটো অঞ্চলে বো ও পিয়াভব নদীর মিলনস্থলে প্রায় ৪১৭.৫৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত ভেনিস। ৩ লাখ নাগরিককে বুকে ধারণ করেছে ভেনিসের ১১৮টি ছোট ছোট দ্বীপ। ১৭৭টি খাল আর এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে হেঁটে যাওয়ার জন্য রয়েছে ৪০৯টি সেতু। আর তাই রূপের পসরা সাজানো ভেনিসকে ভাসমান নগরীও বলা হয়। পানির ভেতর থেকে গেঁথে তোলা সব বাড়ি। বাড়িগুলোর সামনেই স্বচ্ছ থৈথৈ জলের রাস্তা। বাড়িতে ঢুকতে গেলে বা কোথাও বেড়াতে গেলে বাহন হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী নৌকা ‘গন্ডোলা’। এখানে স্থলপথ নেই বললেই চলে। ইউরোপের একমাত্র মোটরগাড়িহীন ও একবিংশ শতাব্দীতেও গাড়ির ধোঁয়াহীন শহরের উদাহরণ ভেনিস।
প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনেই বাঁধা থাকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য ছোট নৌকা, স্পিডবোট বা গন্ডোলা। জলরাশির মধ্যে মাথা উঁচু করে আছে নানা রকম স্থাপত্যশৈলী। ইতালির মূল ভূখণ্ড থেকে একটি বিশাল চওড়া গ্র্যান্ড ক্যানেল শহরের প্রধান জলসড়ক। ভেনিসে ঢোকার পরে গ্র্যান্ড ক্যানেল উলটো করে লেখা বিরাট একটি ইংরেজি ‘এস’ অক্ষরের মতো। এ ক্যানেল ভেনিসের প্রধান জেলাগুলোর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে। ক্যানেলটি প্রায় ৩৮০০ মিটার দীর্ঘ আর ৩০ থেকে ৯০ মিটার প্রশস্ত। গড় গভীরতা প্রায় ৫ মিটার। সেই পথে চলে প্রমোদভ্রমণ, ছুটে চলে জলবাস, ভাড়া পাওয়া যায় প্রাইভেট ওয়াটার ট্যাক্সি কিংবা স্পিড বোট। এ পথ ধরেই এগিয়ে পৌঁছে গেলাম ভেনিসের রিয়ালটো সেতুতে। জলপথের দুই পাশে দেখা যায় বিভিন্ন দ্বীপে গড়ে ওঠা সুন্দর ও তাৎপর্য বহন করা সব স্থাপত্য। সান মারকো ও সান পলো জেলা দুটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গ্র্যান্ডক্যানেলের ওপর প্রাচীনতম সেতু ‘রিয়ালটো ব্রিজ’। ব্রিজ থেকে ক্যানেল বা খালের দৃশ্যটি অনিন্দ্য সুন্দর। প্রচলিত আছে প্রেমিক-প্রেমিকারা সূর্যাস্তের সময় ব্রিজের নিচে উপস্থিত হন। ক্যাম্পানাইল গির্জায় ঘণ্টাগুলো বাজার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরকে চুম্বনের মাধ্যমে তারা স্বর্গীয় ভালোবাসা লাভ করে। প্রচলিত এই মিথ আর খালের দুই পাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রূপ নকশায় সাজানো বাড়িগুলোর পর্যটকদের টানে অন্যরকম মাদকতায়। সেতুর নিচে গন্ডোলায় চড়ে ভ্রমণ করা প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছে পরম কাক্সিক্ষত।
ইতিহাস বলছে, চতুর্থ শতকে জলদস্যুদের কবল থেকে সুরক্ষার জন্য ভেনিসের বাসিন্দাদের পূর্বসূরিরা এখানে বসতি গড়ে তুলেছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর আলপসে হানা দেওয়া উত্তরের জলদস্যুদের কবল থেকে রক্ষা পেতে তারা এ জলমগ্ন এলাকাকে বেছে নিয়েছিলেন
ইতিহাস বলছে, চতুর্থ শতকে জলদস্যুদের কবল থেকে সুরক্ষার জন্য ভেনিসের বাসিন্দাদের পূর্বসূরিরা এখানে বসতি গড়ে তুলেছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর আলপসে হানা দেওয়া উত্তরের জলদস্যুদের কবল থেকে রক্ষা পেতে তারা এ জলমগ্ন এলাকাকে বেছে নিয়েছিলেন। শুরুতে গাছের গুঁড়ি দিয়ে পাইলিং করে এর ওপর ভবন নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পাইলিং করার সময় তা শুধুই অতলে দেবে যেতে থাকে। একটি ভবনের ভিত্তি গাড়তে গেলে কয়েকশ পাইল বা লার্স গাছের কাণ্ড মাটির গভীরে পুঁততে হতো। এভাবে নগর গড়ে তোলার পর ভেনিস নগর নির্মাণকারী কৌশলীরা পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় অগ্রসর হলেন। এতে সাফল্যও পেলেন তারা। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা তদারকির জন্য পোর্তো অ্যালে একিউ নামে একটি পদও সৃষ্টি করা হলো। তার তত্বাবধানে এসব খাল খনন ও নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কাজ করা হয়।
গ্র্যান্ড ক্যানেলের বয়স এক সহস্রাব্দ। এক অতি প্রাচীন নদী থেকে এর উৎপত্তি দশম শতাব্দীতে। সেই সময় থেকেই ব্যবসায়ীরা এখানে বসবাস শুরু করেন। আদি বাড়িগুলো তাদেরই তৈরি করা। মনে পড়ে গেল শেক্সপিয়রের বিখ্যাত নাটক ‘মার্চেন্ট অব ভেনিস’-এর কথা। ছোটবেলায় এ নাটক পাঠের মধ্য দিয়েই ভেনিসের সঙ্গে আমার পরিচয়। ব্যবসায়ী আন্টোনিও, ব্যাসানিও, সুদখোর ব্যবসায়ী শাইলক, বুদ্ধিমতী আইনজীবী পোর্শিয়া আমার স্মৃতিতে উঁকি মারে। দৃষ্টিমনোহর গ্র্যান্ড ক্যানেলে ঘুরে বেড়ানোর চমৎকার আয়োজন রয়েছে। ওয়াটার বাস, গন্ডোলায় চড়ে ঘুরছে অগণিত পর্যটক। মাথার উপর সূর্যদেবতার প্রখর তাপ। সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। গন্ডোলা নামক ময়ূরপঙ্খীসদৃশ নৌকার একটি রোমান্টিক আবহ রয়েছে। প্রেমিক-প্রেমিকা বা স্বামী-স্ত্রী পরম আবেগে গন্ডোলায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
এ বাহনটি একাদশ শতাব্দী থেকে প্রচলিত। চালকের পরনে নেভিব্লু-সাদা স্ট্রাইপের টি-শার্ট। যারা গন্ডোলা চালায়, তাদের বলে গন্ডোলিয়ার। একাদশ শতাব্দী থেকে বয়ে চলেছে এই পেশা। আগের দিনে ছই দেওয়া গন্ডোলায় চড়ে ধনীরা ভেনিসের খালপথে এখানে ওখানে যেতেন। মালপত্রও বহন করা হতো এ গন্ডোলা দিয়ে। একসময়ে ভেনিসে নাকি দশ হাজার গন্ডোলা ছিল। বর্তমানে স্বল্প পরিমাণে হলেও শুধু পর্যটকদের জন্য টিকে আছে গন্ডোলার ঐতিহ্য। অনেক পর্যটকের তো স্বপ্নই থাকে সুনসান জলপথে প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে গন্ডোলায় ঘোরার। এ গন্ডোলার মাঝি হতে গেলে মানতে হয় নিয়ম কানুন। লাইসেন্স পেতে গন্ডোলিয়ারদের একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হয়। আগত পর্যটকদের সঙ্গে সঠিকভাবে কথা বলতে শিখতে হয় বিদেশি ভাষা। জানতে হয় ভেনিস শহরের ইতিহাসের আদ্যোপান্ত। কেউ কেউ গান গেয়ে মুগ্ধ করেন গন্ডোলার যাত্রীদের। এটি অনেকটা শৌখিন পেশা। তাই তো মাঝি হওয়ার স্বপ্নও দেখেন অনেক যুবক। চার দশক আগে মুক্তিপ্রাপ্ত জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমা The Great Gambler -এর কথা মনে পড়ল। এ স্থানে রোমান্টিক গন্ডোলায় চড়ে অমিতাভ-জিনাত আমানের প্রেমদৃশ্য মূর্ত হয়ে উঠেছিল রাহুল দেব বর্মনের কালজয়ী গানে ‘দো লাফজো কি হায় দিল কি কাহানি’। সেই দৃশ্যে চালকের গায়ে যে পোশাক, আজকের চালকের গায়েও সেই একই পোশাক। অদ্ভুত ঐক্য দুই সময়ের মাঝে। অনৈক্য এখানে যে অমিতাভের মতো আমার কোনো সঙ্গী নেই। পূর্বপরিচিত এক শ্রীলংকান তরুণী আমাকে উৎসাহিত করেছিল তার গন্ডোলায় চড়তে। কিন্তু ‘মনে কী দ্বিধা’ থাকায় আমার আর চড়া হয়নি তার সঙ্গে এ ঐতিহাসিক যানে।

দুই সফরসঙ্গীর সঙ্গে পৃথক গন্ডোলায় চড়ি। প্রাসাদোপম বাড়িগুলো জলের ওপর ভাসমান। বেশ চেনা দৃশ্য। ছবিতে ও সিনেমায় এত দেখেছি তাদের যে একটুও নতুন মনে হয় না। ইতিহাস ও স্থাপত্যশৈলীর বিবর্তন যেন এক এক মিছিল করে চলে যায় সামনে দিয়ে। রোমান শেষ হতে না হতে আসে বাইজেন্টিয়াম। তারপর গথিক। গথিকের পাশেই দেখা যায় রেনেসাঁসশৈলীর প্রাসাদ। ব্যারাকের জাঁকজমকপূর্ণ শৈলী এসে দাঁড়ায় ভারিক্কি চালে। ভেনিস তার সংস্কৃতির সব শাখাতেই গ্রহণ করেছে অন্যের প্রভাব ও অন্য দেশের উপকরণ। ভেনিসের গথিক তার নিজস্ব গতিতে গড়ে উঠেছে। সেখানে বাইজেন্টিয়াম আর অটোমান তুর্কিদের স্থাপত্যশৈলীর মিশ্রণ ঘটেছে। একটি ভবন থেকে আরেকটি ভবন ভিন্ন দেখায়। কিন্তু সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তারা একই জায়গায় মিলেছে। ভবনগুলোর রঙও ভিন্ন। কিন্তু ভিন্নতার জন্য কোনো সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়নি। গ্রান্ড ক্যানেলের দুই পাশে দাঁড়িয়ে তারা যেন একটি বর্ণিল ছবির প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছে। ফ্লোরেন্স যেমন হলুদ আর পিঙ্গল রঙের রাজত্ব এবং প্রায় একচেটিয়া ব্যবহার ভেনিসে তেমন নয়। বর্ণিল ভেনিস বহু বর্ণ ধারণ করে।
ভবনগুলো যে জলের ওপর ভাসছে না, সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনও নয় যে, তাদের নিচের ভিত্তিসহ একতলা-দোতলা পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছে। বাড়িগুলো তৈরি হয়েছে অনেক কাঠের কলামের ওপর। ঘন করে নিচের বালি এবং মাটিতে পোঁতা কাঠগুলো অক্সিজেনহীন সমুদ্রের জলে পাথরে পরিণত হয়েছে। সেই পাথুরে ভিত্তির ওপর তৈরি হয়েছে বাড়ির ভিত্তি এবং তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে জলের ওপরকার বাড়ি, তিনতলা-চারতলা পর্যন্ত। সাত-আটশ বছর ধরে ভবনগুলো একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে, হেলে পড়েনি কিংবা ভেঙে পড়েনি।
বৈচিত্র্যময় স্বাদযুক্ত উৎকৃষ্ট আইসক্রিম উৎপাদনের জন্যও ভেনিস খ্যাতিমান। আইসক্রিমের স্বাদ নিতে গিয়ে উপরি পাওনা ইতালি ও ঘানার দুই তরুণীর বন্ধুত্ব লাভ। সেদিনই সন্ধ্যায় একটি পোশাক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে তাদের মডেল হিসাবে অংশগ্রহণ করার কথা। ভিন্ন সংস্কৃতির দুই তরুণীর সঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম ভেনিসের অলিগলিতে। হাঁটতে হাঁটতেই চোখ আটকে গেল এক বিক্রেতার পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজনে। কয়েক দশকের পুরোনো বিশ্বখ্যাত ইতালীয় চলচ্চিত্রের তারকাদের ছবি সংবলিত পোস্টার। সোফিয়া লরেন, মার্সেলো মাস্ত্রোয়ানি থেকে শুরু করে এ যুগের মনিকা বেলুচ্চি সেখানে উপস্থিত। আমার চোখ আটকে গেল ভিট্টোরিও ডিসিকার ‘বাইসাইকেল থিভস’ চলচ্চিত্রের পোস্টারে।
এ চলচ্চিত্রের প্রতি আমার দুর্বলতার একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। উপমহাদেশীয় তথা বাংলা চলচ্চিত্রের মুক্তিদাতা সত্যজিৎ রায় বিশ্ব চলচ্চিত্রের এই অন্যতম মাস্টারপিস দেখে তার অবিস্মরণীয় কীর্তি ‘পথের পাঁচালী’ নির্মাণের অনুপ্রেরণা পান। ‘বাইসাইকেল থিভস’ চলচ্চিত্রটিকে নিউরিয়ালিজম আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ফসল বলে গণ্য করা হয়। বেকার যুবক এন্টোনিওকে ঘিরে এই ছবির কাহিনি গড়ে উঠেছে। হতাশ এন্টোনিও দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একটি চাকরি পায়। তার কাজের জন্য প্রয়োজন একটি সাইকেল। তার কাজ রাস্তায় পোস্টার লাগিয়ে বেড়ানো। সাইকেলটি চুরি যায়― যার অর্থ চাকরি যাওয়া। এন্টোনিও তার ছোট ছেলেটিকে নিয়ে খুঁজে বেড়ায় হারানো সাইকেল। এ সূত্রেই রোমের অন্ত্যজশ্রেণি, ভবঘুরে, বাজার, রেস্তোরাঁ, বেশ্যালয় ঠাঁই পায় এ ছবিতে। ঠাঁই পায় দুস্থ জীবন থেকে মুক্তির উপায় জানার জন্য গণৎকারের কাছে ভিড়, চার্চের ভণ্ডামি। উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত এন্টোনিও একটি সাইকেল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে ও লাঞ্ছিত হয়। বিশ্ব চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত―চোর বলে লাঞ্ছিত এন্টোনিও আর তার ছেলেটির মধ্যে অপরাধবোধ, লজ্জা-অভিমান মিশ্রিত পাশাপাশি হাঁটা, আবার দুজন দুজনকে সহজভাবে ভালোবাসার আকাক্সক্ষা। শিল্পে কীভাবে মলিনতার মধ্যে, দুঃসহ জীবনযাত্রার গ্লানির মধ্যে নির্মল মনুষ্যত্বের মহিমা প্রকাশ করা যায়, কত সামান্য পরিসরে সৃষ্টি করা যায় মহৎ শিল্প তা ডিসিকা এ চলচ্চিত্রে সার্থকতার সঙ্গে দেখিয়ে দিলেন। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনে জরাজীর্ণ ভারতীয় বাস্তবতার এই চলচ্চিত্র রূপ কল্পনা করার আগে সত্যজিৎ রায় নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থীর মতো ‘বাইসাইকেলে থিভস’ বহুবার দেখেছিলেন। ১৯৪৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এ চলচ্চিত্রের সেই সময়ের পোস্টার আমাকে যেন ছয় দশক পেছনে নিয়ে গেল। সহচরী ইতালীয় তরুণী আমার বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারেনি। তাকে বললাম এই চলচ্চিত্র কীভাবে এক বঙ্গসন্তানকে বিশ্বজয়ী চলচ্চিত্রকারে রূপান্তরিত করেছে। ডিসিকার প্রতি সত্যজিতের হয়ে ঋণ স্বীকার করলাম সেই তরুণীর কাছে। তার ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি বুঝিয়ে দিল এজন্য সে গর্বিত।
জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অনুরাগী। এই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ছোঁয়া লেগেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় ও বিংশ শতাব্দীর ঢাকায়। এ সম্পর্কে বইপত্র বা তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি কখনোই আমার ছিল না। কিন্তু নিজের চোখে রেনেসাঁসের জন্মভূমিকে প্রত্যক্ষ করা―এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা
অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের মতো ভেনিসেও ইংরেজি বিদ্বেষ চোখে পড়ল। হোটেলে ফেরার পথে বাস থেকে নামার আগে এক ভদ্রলোক ইতালীয় ভাষায় আমাকে কিছু বললেন―শরীরী ভাষা দেখে বুঝলাম তার নজর আমার আসনের দিকে। বাস থেকে নামার আগে আসনটি যেন তাকে বুঝিয়ে দিই। এ যেন ঢাকার পাবলিক বাসে চড়ার অভিজ্ঞতা। সুপার মার্কেটে শপিং করতে গিয়েও একই বিপত্তি। রাত ৮টার মধ্যে মার্কেট বন্ধ হয়ে যাবে―এ কথাটিও বিদেশি পর্যটকদের তারা ইংরেজিতে বলতে অপারগ।
ভেনিস ছেড়ে আজ ফ্লোরেন্সের দিকে চলেছি। মাঝপথে পার হলাম মিলান। রাস্তায় লেখা কত দূরে রয়েছে রোম। এ নামগুলোর সঙ্গে পরিচয় শৈশবে―গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, সিনেমায়। তখন কি জানতাম এই নামগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটবে একদিন? পাহাড় কেটে দু’পাশে মনোরম প্রাকৃতিক বিন্যাস রেখে কীভাবে একটি মহাসড়ক তৈরি হতে পারে, এর আদর্শ উদাহরণ ফ্লোরেন্সের প্রবেশপথ। রেনেসাঁসের জন্মনগরী বলে খ্যাত ফ্লোরেন্সে কী আছে তা দেখার জন্য মুখিয়ে আছি। ইতালির সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালিনী নগরী ফ্লোরেন্স একসময় রাজধানী ছিল। রোমান দেবী ফ্লোরার নামে এ নামকরণ।
জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অনুরাগী। এই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ছোঁয়া লেগেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় ও বিংশ শতাব্দীর ঢাকায়। এ সম্পর্কে বইপত্র বা তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি কখনোই আমার ছিল না। কিন্তু নিজের চোখে রেনেসাঁসের জন্মভূমিকে প্রত্যক্ষ করা―এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ফ্লোরেন্স সেই উপহার আমায় দিয়েছে। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, ম্যাকিয়াভেলির শহর ইতালির ফ্লোরেন্স। চিত্রকলা আর মানুষের নান্দনিকতার প্রমাণ হিসাবে বিশালাকৃতির ক্যাথেড্রাল এবং বিশ্বখ্যাত জাদুঘর আর আর্ট গ্যালারিগুলো এখানে অবস্থিত। সেই সঙ্গে বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ভাস্কর্য মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ডেভিড!
রেনেসাঁস ছিল এক যুগান্তকারী সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং এর কেন্দ্রে ছিল শিল্পচর্চা। সেই শিল্পচর্চায় দেব-দেবীর পরিবর্তে আবার প্রাচীনকালের মতো সাধারণ মানুষকে চরিত্র হিসাবে এঁকে তার মর্যাদা ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এ সাংস্কৃতিক আন্দোলন ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে গিয়ে শুধু চিত্রকলা নয়, দর্শন, সাহিত্য, সংগীত, রাজনীতি, বিশ্বাস, ধর্ম এবং বুদ্ধিবৃত্তির অন্যান্য শাখাতেও এর প্রভাব বিস্তৃত হয়। রেনেসাঁসের পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তারা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইহজাগতিকতার ভিত্তিতে তাদের জ্ঞানের চর্চায় প্রয়োগ করেন। তাদের প্রভাবেই যুক্তিবাদিতা শুধু ইউরোপে নয়, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।
রেনেসাঁসকে বলা হয়েছে মানবসভ্যতার প্রথম বসন্ত। রেনেসাঁর বাণী এবং তার সংস্কৃতির গৌরব সারা ইউরোপেই ছড়িয়ে পড়ে। শিল্প-সংস্কৃতি এবং দর্শনে রেনেসাঁ যুগের সব কীর্তি এবং অর্জনের জন্যই এখনো ফ্লোরেন্স পৃথিবীতে আধুনিক মানুষের তীর্থস্থান হয়ে আছে। রেনেসাঁসের ভেতর দিয়ে ইউরোপ একদিকে বিশ্বজগৎকে এবং অপরদিকে মানবপ্রকৃতিকে আবিষ্কার করে। রেনেসাঁসের বিকাশ ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র ও প্রযুক্তিবিপ্লব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু রেনেসাঁসের মানস ঐশ্বর্য প্রথম বিচ্ছুরিত হয়েছিল ফ্লোরেন্সের শিল্পী ও চিন্তকদের মধ্যে।

স্বয়ং জুলিয়াস সিজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৫৯ সালে আরনো নদীর তীরে এ অপরূপা নগরীর গোড়াপত্তন করেন। শহরের প্রায় সব রাস্তার মোড়েই চোখে পড়া অতি প্রাচীন সব স্থাপত্য সেই সুপ্রাচীন গৌরবময় অতীতের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। বেশ খানিকক্ষণ অলি-গলি মাড়িয়ে বোঝা গেল আমরা শহরকেন্দ্রে এসে পৌঁছে গেছি। দৃশ্যপটে আবির্ভাব ঘটেছে ফ্লোরেন্সের প্রতীক বলে খ্যাত নয়নাভিরাম ফ্লোরেন্স ক্যাথেড্রালের। চোখের সামনের আকাশকে পর্যন্ত আড়াল করে দেওয়া বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম এই ক্যাথেড্রালটির মূল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় ১৫০ বছরে। তার বিশালাকার তোরণ, সুউচ্চ খিলান সেইসঙ্গে দানবাকৃতির গম্বুজ নিজের অজান্তেই মুগ্ধতায় মাথা নুইয়ে দেয় রেনেসাঁর সেই মহান প্রকৌশলী আর কারিগরদের প্রতি। প্রতিটি দরজায়ই কাঠ আর ধাতুর সমন্বয়ে অতি নিখুঁতভাবে বাইবেলে বর্ণিত নানা ঘটনার চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পঞ্চদশ থেকে প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত নবজাগরণের ঢেউ প্লাবিত করে ইউরোপের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারকে। মিকেলেঞ্জোলো, বতিচেল্লি, রাফায়েল, ভিঞ্চি, গ্যালিলিও―আরও কত শ্রেষ্ঠ মনীষীর কালজয়ী প্রতিভার উদাহরণ হয়ে আছে ফ্লোরেন্স নগরী। শত শত বছর আগের অপূর্ব স্থাপত্যশৈলী দেখে শ্রদ্ধাবনত হতে হয় এ অমর স্রষ্টা ও তাদের পূর্বসূরিদের প্রতি। মিকেলেঞ্জোলোর ‘ডেভিড’, ‘পিয়েটা’, ভিঞ্চির ‘মোনালিসা’, ‘দ্য লাস্ট সাপার’, বতিচেল্লির ‘দ্য বার্থ অব ভেনাস’-এর প্রভাব শহরের সর্বত্র। ‘The Springtime of Renaissance (1400-1620) Florence’ নামে এক চোখ ধাঁধানো প্রদর্শনীর মুখোমুখি হলাম। সেই সময়ের সেরা ভাস্কর্য, চিত্রকর্মের সমাবেশ। ফ্লোরেন্সে শিল্পবোদ্ধাদের জন্য জাদুঘরের অভাব নেই। মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে সেখানে ঢোকার টিকিট কাটছে দেখে খুব ভালো লাগল। রেনেসাঁসের স্রষ্টা ও তাদের সৃষ্টিকর্মের প্রতি দর্শকদের ভালোবাসা অফুরন্ত।
পরবর্তী গন্তব্য বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত আর্ট গ্যালারি ফ্লোরেন্সের উফিজি। অতুলনীয় এই শিল্পতীর্থে ৫০টির অধিক বিশালাকার কক্ষে অন্তত দেড় হাজার শিল্পকর্ম আছে, যার যে কোনো একটি পেলেই কোনো দেশ না জাদুঘর বর্তে যাবে। মূলত ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত মেদিচ্চি পরিবারের ব্যক্তিগত সংগ্রহই এখানে স্থান পেয়েছে, যা ১৭৪৩ সালে মেদিচ্চিদের শেষ বংশধর আন্না মারিয়া ল্যুদভিকো এই শর্তে দান করেন যে এই বিশ্ব সম্পদগুলো কখনোই তার ভালোবাসার শহরের বাইরে যাবে না! খানিকক্ষণ শিল্পসুধা উপভোগের পর সোজা ১৯ নম্বর কক্ষে চললাম, যেখানে বিশ্বের অন্যতম সেরা রেনেসাঁ চিত্রকর বতিচেল্লির উল্লেখযোগ্য ১৫টি কাজ স্থান পেয়েছে, সে এক অবাক করা অতুলনীয় গুপ্তধনের রাজ্য।
দরজা দিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল বতিচেল্লির অমর সৃষ্টি বিশালাকৃতির প্রিমাভেরা (বসন্ত)। দেয়ালজোড়া এ চিত্রকর্মে আছে বেশ কজন পৌরাণিক দেব-দেবী, আর এদের মাঝেই কোলের আচড় থেকে বসন্তের আগমনী দূত ফুল ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে যাচ্ছে বসন্তের দেবী। এর পাশের দেয়ালে চিত্রকরের সবচেয়ে বিখ্যাত সৃষ্টি বার্থ অফ ভেনাস! অসামান্য জাদু এই অপরূপ ক্যানভাসে, সমুদ্রে ভাসমান ঝিনুকের উপর দণ্ডায়মান ভেনাস-সুন্দরী দুই হাতে লজ্জা ঢাকতে ব্যস্ত, এলোচুল বাতাসে উড়ছে আলগোছে, মাথা মৃদু ডানদিকে কাত হয়ে আছে, চোখে অপার বিষণ্ণ দৃষ্টি। বাতাসের দেবতা জোরাল ফুঁ দিয়ে ঝিনুকটিকে ডাঙায় নিচে যাওয়ার চেষ্টারত, আর অন্যদেবী এগিয়ে আসছেন এক জমকালো বস্ত্রখণ্ড দিয়ে তাকে আবৃত করতে। ফ্লোরেন্সের উফিজি গ্যালারিতে পরম যত্নে সংরক্ষিত রয়েছে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম ‘বার্থ অব ভেনাস’। সৌন্দর্য ও প্রেমের অনবদ্য প্রতীক দেবী ভেনাস। ১৪৮২-৮৫ সালের মধ্যে সান্দ্রো বতিচেল্লি এ কালজয়ী চিত্রকর্মটি সম্পন্ন করেন। নগ্ন দেবী সমুদ্র থেকে উঠে আসছেন। তার বাম দিকে মৃদু বাতাস গোলাপের সুরভিতে রাঙিয়ে দিচ্ছে স্বর্ণালি কেশরাশি, ডানদিকে আরেক সুন্দরী অপেক্ষমাণ ভেনাসের নগ্ন দেহকে বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদন করার জন্য। এ আচ্ছাদন কি খুব জরুরি? বতিচেল্লি যেন এ প্রশ্নই করেছেন দর্শনার্থীদের। এ প্রশ্নের উত্তর আমি জানি। তবে নিজের ভাষায় নয়, রবীন্দ্রনাথের অনুপম গদ্যে উত্তরটি দেব। ‘য়ুরোপযাত্রীর ডায়রি’তে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর একটি চিত্রপ্রদর্শনীর অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেছেন। তখন তার বয়স উনত্রিশ এবং তার কন্যা বেলি তখনো শিশু। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন―
‘সেদিন French Exhibition-এ একজন বিখ্যাত artist-রচিত একটি উলঙ্গ সুন্দরীর ছবি দেখলুম। কী আশ্চর্য সুন্দর! দেখে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। সুন্দর শরীরের চেয়ে সৌন্দর্য পৃথিবীতে কিছু নেই―কিন্তু আমরা ফুল দেখি, লতা দেখি, পাখি দেখি, আর পৃথিবীর সর্বপ্রধান সৌন্দর্য থেকে একেবারে বঞ্চিত। মর্ত্যরে চরম সৌন্দর্যের উপর মানুষ স্বহস্তে একটা চির অন্তরাল টেনে দিয়েছে। কিন্তু সেই উলঙ্গ ছবি দেখে যার তিলমাত্র লজ্জাবোধ হয় আমি তাকে সহস্ত ধিক্কার দিই। আমি তো সুতীব্র সৌন্দর্য-আনন্দে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম, আর ইচ্ছে করছিল আমার সবাইকে নিয়ে দাঁড়িয়ে এ ছবি উপভোগ করি। বেলি যদি বড় হতো তাকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আমি এই ছবি দেখতে পারতুম। এই ছবি দেখলে সহসা চৈতন্য হয়―ঈশ্বরের নিজ হস্ত রচিত এক অপূর্ব পশু―মানুষ একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং এই চিত্রকর মনুষ্যকৃত সেই অপবিত্র আবরণ উদ্ঘাদন করে সেই দিব্য সৌন্দর্যের একটা আভাস দিয়ে দিলে।’
রেনেসাঁসকে বলা হয়েছে মানবসভ্যতার প্রথম বসন্ত। রেনেসাঁর বাণী এবং তার সংস্কৃতির গৌরব সারা ইউরোপেই ছড়িয়ে পড়ে। শিল্প-সংস্কৃতি এবং দর্শনে রেনেসাঁ যুগের সব কীর্তি এবং অর্জনের জন্যই এখনো ফ্লোরেন্স পৃথিবীতে আধুনিক মানুষের তীর্থস্থান হয়ে আছে
গোটা ফ্লোরেন্স জুড়ে যে কয়েকটি ভাস্কর্যের অবিকল ছবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের অন্যতম ‘পিয়েটা’। এর নির্মাতা মিকেলেঞ্জোলো। জগদ্বিখ্যাত এ শিল্পী একাধারে ছিলেন স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রকর এবং কবি। এ চার বিদ্যায় তার অতুলনীয় প্রতিভা শিল্পবোদ্ধাদের কাছে প্রচণ্ড বিস্ময়। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে অনন্য সৃষ্টি ‘পিয়েটা’ সমাপ্ত করেন। ভাস্কর্যটি রোমের সেন্ট পিটার ব্যাজিলিকায় রক্ষিত আছে। এটি তৈরি করার পর তিনি সগর্বে লিখেছিলেন, ‘রোমে যেসব ভাস্কর্য আছে তার মধ্যে এটি হবে সবচেয়ে সুন্দর, এরকম ভাস্কর্য আজকের দিনে কোনো জীবিত ওস্তাদ গড়তে পারবেন না।’ এমন অহংকার মিকেলেঞ্জোলোর মতো মহাশিল্পীকেই মানায়।
ভাস্কর্যটি হচ্ছে মাতা মেরি পা ঝুলিয়ে বসে আছেন, কোলে আড়াআড়ি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তার ছেলে যিশুর মৃতদেহ। তার ডান কোলে যিশুর মাথা। যিশুর ঘাড়ের তলায় মেরির ডান হাত, সেই হাত যিশুর বুকের পাঁজর পর্যন্ত প্রসারিত। যিশুর হাঁটু মেরির কোল পেরিয়ে মেরির বাঁ ঊরুর ওপর দিয়ে মেরির বাঁ দিকে ঝোলানো। যিশুর দেহ এমনভাবে নেতিয়ে পড়েছে যে মনে হয় প্রাণহীন ছবির শরীরের সব ভার মেরির কোলে। যিশুর ডান হাত মেরির ডান হাঁটুর সামনে দিয়ে ঝুলে পড়েছে। তার বাঁ হাত নিজের কোমর বরাবর এসে তার কোমরের পাশ দিয়ে মেরির কোলে উঠে মেরির শরীরের বাঁ দিকে পড়ে আছে। মেরি তন্ময় হয়ে সব পৃথিবী থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রিয়পুত্রের দিকে মুখ নত করে অর্ধমুদিত চোখ রেখে ভাবছেন। কী ভাবছেন তিনি? যিশুর নিয়তি নির্ধারিত জীবন, তার মাতৃত্বের নাটকীয় স্মৃতি, যিশুর মৃত্যু এরকম হবে বহু আগে তার ভবিষ্যদ্বাণী? এমন হৃদয়বিদারক, শোকাচ্ছন্ন, আত্মসমাহিত, সংযত মূর্তি কেউ আগে নির্মাণ করেননি। সন্তানের জন্য মায়ের শোকের এমন শৈল্পিক আবেগের প্রকাশ আর কোনো ভাস্কর্যে ঘটেনি, হয়তো ভবিষ্যতেও ঘটবে না।
মিকেলেঞ্জোলোর আরেকটি অমর সৃষ্টি ‘ডেভিড’। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে এটি তিনি নির্মাণ করেন। ‘ডেভিড’ কোথায় স্থাপিত হবে সেই স্থান নির্বাচন করেছিলেন ফিলিপিনো লিপ্পি, বতিচেল্লি, ভিঞ্চির মতো বিশ্ব কাঁপানো শিল্পীরা। ১৫০৪ সালের এপ্রিলে ‘ডেভিড’-এর নির্মাণ শেষ হলে তা স্থাপন করা হয় পালাৎসো ভেক্কিওর প্রবেশমুখের সামনের অঙ্গনে। একেবারে রাস্তার ওপরে থাকায় ভাস্কর্যটি বিভিন্ন আক্রমণের শিকার হলো। একটি অযাচিত দুর্ঘটনায় ভাস্কর্যের বাঁ হাত ভেঙে তিন টুকরো হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অবশেষে ভাস্কর্যটি ফ্লোরেন্সের আকাডেমিয়া দি বেলে আর্ট গ্যালারিতে রাখা হয় ১৮৭৩ সালে। এখনো সেখানেই আছে। আগের স্থানে ভাস্কর্যের অবিকল রেপ্লিকা রয়েছে।
এক বিশাল মূর্তি এই ডেভিড। বেদি বাদ দিয়ে মূর্তিটি সাড়ে তেরো ফুট উঁচু। ডান পায়ে শরীরের ভার রেখে, বাঁ হাঁটু আলগা করে নগ্ন দেহে দাঁড়িয়ে, বাঁ হাত বুকের কাছে উপর দিকে মুড়ে তার অবস্থান। কাঁধের ওপর গুলতি ফেলা, ডান হাত ডান ঊরু বরাবর সোজা করে ফেলা, ডান হাতে গুলতির পাথর। অপূর্ব ডেভিড গ্রিক পুরুষোচিত সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা, শরীরের প্রতিটি মাপ নিখুঁত, আদর্শ পুরুষের দেহের মাপ। দারুণ আত্মবিশ্বাসী এই ডেভিড। ডেভিড ছিলেন বালক, কিন্তু তার আকৃতি দানবের। এর ওজন নয় টন।
ডেভিড ক্লাসিক্যাল গ্রিক বা রোমান ভাস্কর্যের মতো শান্ত, সমাহিত বা সংযত নয়। শরীর প্রচণ্ড শক্ত সমর্থ, কোথাও এতটুকু মেদ নেই। দাঁড়ানোর ভঙ্গি, শরীরী অভিব্যক্তি, বিস্ফোরিত দৃষ্টি, কোঁচকানো ভুরু, ললাটে কুঞ্চিত রেখা―সবকিছু শরীরে ও মনে বেশ আলোড়ন তুলেছে। গুলতিটি কাঁধে এমনভাবে রাখা যে তিনি যে কোনো সময় গুলতি ছুঁড়তে সক্ষম। দেহে ও মনে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ডেভিড এ বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন যে আগামী দিনে তিনিই হবেন ফ্লোরেন্সের শৌর্যবীর্যের প্রতীক।
ফ্লোরেন্স আরনো নদীর ধারে অবস্থিত। ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে নদীর দু-পাশের মনোরম প্রকৃতিকে দেখা এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তখন গোধূলির গোলাপি আভা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কিছুক্ষণ পর রেনেসাঁসের শহর ফ্লোরেন্সের আকাশে পূর্ণ মহিমায় চাঁদ জেগে উঠল। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি পূর্ণ চন্দ্র উদ্ভাসনের। পূর্ণিমার আলোয় আরনো নদীর জলে অপূর্ব বিকিরণ। আলো ঝলমলে ফ্লোরেন্সের গায়ে অগণিত ভাস্কর্য, সুদৃশ্য ভবন অলংকারের মতো শোভা পাচ্ছে। আলোকের ঝরনাধারায়প্লাবিত এই শহরের সৌন্দর্য যেন নিংড়ে নিতে ব্যস্ত সবাই। শহরের কেন্দ্রস্থলে কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলাম। অদূরে ভিঞ্চি, ম্যাকিয়াভেলি, গ্যালিলিওর মতো যুগস্রষ্টা মনীষীদের ভাস্কর্য। তাদের কীর্তিধন্য ফ্লোরেন্সে আজ আমার মতো নগণ্য পথিক। বিশ্বাস করতে মন চায় না। অবিশ্বাসী মনকে সংযত করে গভীর রাতে ফ্লোরেন্সের মায়া কাটিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে।

মন না চাইলেও ইতালির মায়া ছাড়তে হয়েছে। শেষ হইয়াও হইল না শেষ―ছোটগল্পের সংজ্ঞার মতোই এক টুকরো বর্ণিল ইতালি আবার আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকল। বিশ্বখ্যাত ‘পিসা টাওয়ার’-এ আমাদের যাত্রাবিরতি। মধ্যযুগের স্থাপত্যশিল্পের অনন্য দৃষ্টান্ত এই টাওয়ার। তখন ইউরোপে এটিই উচ্চতম টাওয়ার। ১১৭৩ সালে নির্মাণ শুরু হয়ে সমাপ্তি ঘটে ২০০ বছর পর। স্থপতির নাম আজও অজানা।
পিসার টাওয়ার মানুষের তৈরি এক আশ্চর্য অসম্পূর্ণতা। মূলত ভুল নির্মাণ কৌশলে তৈরি এ পিসার টাওয়ার, যা নির্মিত হয় আজ থেকে প্রায় কয়েক শতাব্দী আগে। পৃথিবীর আশ্চর্য স্থাপত্যের মধ্যে অনন্য এক স্থাপত্য হচ্ছে পিসার টাওয়ার। পিসা ইতালির প্রাচীন এক গৌরবময় প্রসিদ্ধ নগরী। ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে শহরটি ছিল খুবই সমৃদ্ধশালী। এটা সেই শহর যেখানে ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি জন্ম নিয়েছিলেন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলেই। সেই পিসা নগরীর ঐশ্বর্যময় জাঁকজমক ও উৎকর্ষ পৃথিবীর মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য নির্মাণ করা হয় সূক্ষ্ম কারুকার্যে পূর্ণ অপূর্ব এক স্থাপনা। পিসা শহরের ক্যাথিড্রাল স্কয়ারের তৃতীয় প্রাচীনতম স্থাপনার একটি পিসার হেলানো টাওয়ার। অনেকের কাছে এটি ‘লিনিং টাওয়ার অব পিসা’ নামে পরিচিত। স্থাপত্যটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সার্চিও ও আর্নো নামের দুই নদী।
প্রথম থেকেই কিন্তু এ টাওয়ারটিকে হেলানোভাবে তৈরি করা হয়নি। তিন তলা পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর থেকেই টাওয়ারটিকে ঘিরে ঘটে অদ্ভুত এক ঘটনা। হঠাৎই হেলতে শুরু করে টাওয়ারটি। বিশেষজ্ঞরা দেখতে পান, টাওয়ারটির নির্মাণ কৌশলে ভুল ছিল। টাওয়ারের নিচের নরম মাটি ও অগভীর ভিত এই অস্বাভাবিক হেলে পড়ার জন্যে দায়ী বলে ধারণা করা হয়। অদ্ভুত উপায়ে সেই হেলানো অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে রইল টাওয়ারটি, ভেঙেও পড়ল না। স্থপতিরাও হাল ছেড়ে না দিয়ে হেলে যাওয়ার মধ্যেই গড়তে থাকেন একের পর এক তলা।
এ সময় পিসা রাজ্য পার্শ্ববর্তী স্থানীয় রাজ্যগুলো―জেনোয়া, লুক্কা এবং ফ্লোরেন্সের সঙ্গে নানা ছোটখাটো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে এক শতাব্দী সময় জুড়ে এ টাওয়ারের নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল। যুদ্ধ শেষে শান্তি এলে আবার শুরু হলো টাওয়ার তৈরির কাজ। বহুদিন কাজ বন্ধ থাকার ফলে টাওয়ারটি মাটিতে ভালোভাবে গেঁথে যায়। তাই উপরের ফ্লোরগুলোও তৈরি হয়ে যায় ধীরে ধীরে এবং ১৩৭২ সালে সম্পন্ন হয় এই অনন্য স্থাপনা নির্মাণের কাজ।
বিখ্যাত ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের জন্য টাওয়ারটি ব্যবহার করেছিলেন। টাওয়ারের মাঝের ছাদ থেকে ঝুলে থাকা এক ঝাড়বাতি দেখে গ্যালিলিও তার বিখ্যাত দোলন সূত্রগুলোর কথা প্রথম চিন্তা করেন বলেও জানা যায়। গ্যালিলিও তার বিখ্যাত সূত্র ‘বায়ুশূন্য পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ভরের পড়ন্ত বস্তুর গতিবেগ সমান’ প্রমাণের জন্য এই টাওয়ারটি বেছে নিয়েছিলেন। গিনি ও পালকের পরীক্ষার একটি অংশ তিনি দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভরের কামানের গোলার সাহায্যে হাতে কলমে পরীক্ষা করেছিলেন পিসার টাওয়ার থেকেই।
একদিকে হেলে থাকা এই টাওয়ারকে ঘিরে কৌতূহলের শেষ নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনী খবর পায় জার্মান সৈন্যরা এই টাওয়ারকে তাদের পর্যবেক্ষণ স্থল হিসাবে ব্যবহার করছে। যুক্তরাষ্ট্র তার সেনাবাহিনীর এক সার্জেন্টের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠায় সেখানে এ খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য। সেই সার্জেন্ট এই টাওয়ারের সৌন্দর্য দেখে এত মুগ্ধ হন যে তিনি তার সৈন্যদের নিষেধ করেন সেই টাওয়ারে আক্রমণ না করতে। টাওয়ারের আভিজাত্য ও সৌন্দর্য বেঁচে যায়। ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের কারণে ইউনেসকো ১৯৮৭ সালে একে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করে। এভাবেই সমাপ্তি ঘটে ইতালি ভ্রমণের। শিল্প ও সৌন্দর্যের তীর্থস্থান ইতালির অবিস্মরণীয় স্মৃতি আজও হাতছানি দিয়ে ডাকে।