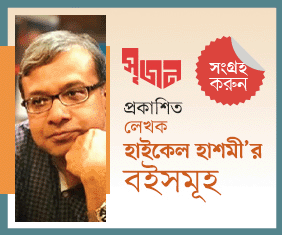অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের কবিতায় ধ্রুপদি আদর্শের একচেটিয়া প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একে বলা যায় একমেরুকেন্দ্রিক সাহিত্যাদর্শ। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তার বিরুদ্ধে একটি নতুন সাহিত্যাদর্শের জন্ম হয়, যার নাম রোমান্টিক সাহিত্যান্দোলন (১৭৫০-১৮৪৮)। রোমান্টিক আন্দোলনের শতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থে আর্নেস্ট ফিসার উল্লেখ করেন, ফরাসি দার্শনিক রুশোর (১৭১৪-১৭৭৪) ডিসকারজেস (ডিসকোর্স, ১৭৫০) থেকে শুরু করে মার্কস-এঙ্গেলসের কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ে (১৭৫০-১৮৪৭) রোমান্টিকতা ছিল ইউরোপের নিয়ন্ত্রক চেতনা। কাজেই এ আন্দোলন বিকশিত হওয়ার পর সাহিত্য দ্বিমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে বিভক্ত হল। আনন্দ ও বেদনা, শুভ ও অশুভ, সুখ ও দুঃখ যেমন দুটি সার্বজনীন বিপরীতধর্মী সত্য; সে রকম বিপরীতধর্মী সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক আদর্শ। নিটশে (১৮৪৪-১৮১৮) তার ট্র্যাজেডির জন্ম গ্রন্থে (১৮৭২) গ্রিক দুই দেবতার প্রতীক ব্যবহার করে এই দুটি আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, অ্যাপোলো হচ্ছে ক্লাসিক সভ্যতার প্রতীক আর ডায়োনিসাস হচ্ছে সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস বা রোমান্টিকতার প্রতীক। জার্মান নাট্যকার লেসিং (১৭২৯-১৭৮১)-এর লাওকুন (১৭৬৬) গ্রন্থে ক্লাসিক্যাল সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে ট্রয়ের পুরোহিতের ছবি এঁকেছেন। সেখানে অ্যাপোলোর সমাহিত মূর্তি হচ্ছে ক্লাসিক্যাল তত্তে¡র প্রতীক আর আর্তনাদরত তার দুই পুত্র হচ্ছে রোমান্টিসিজমের প্রতীক।
রোমান্টিসিজমকে বলা হয় ‘ইউরোপীয় বিবেকের এক চীৎকার’ বলে— যার আঘাতে ভেঙে পড়ে জনসনের যুর্গে নিয়ন্ত্রিত আবেগের সৌধ। রোমান্টিকতার উৎস ও ইতিহাস আলোচনার করতে গেলে ফিরে যেতে হয় মধ্যযুগে। সে উত্তরাধিকার বহন করে মধ্যযুগের, তার নাড়ির সম্পর্ক ও আত্মীয়তা মধ্যযুগের সঙ্গে। ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও নিও ক্লাসিজিসজমের আত্মীয়তা যেমন প্রাচীন যুগের গ্রিস ও রোমের সঙ্গে। ইউরোপীয় রেনেসাঁর ঐতিহ্য হল প্রাচীন আলেক্সান্দ্রীয় রেনেসাঁ, তেমনি রোমান্টিকতার ঐতিহ্য হল মধ্যযুগ। স্মারণ করা যেতে পারে হোরেসের কথা— যিনি বলেছেন অনুসরণ করতে হবে ঐতিহ্যকে। তবে সার্বজনীন সত্য হচ্ছে, কোনো কাল অনুসরণ করে না তার সমসাময়িক কালকে। নতুন কাল তার জীবনরস সংগ্রহ করে দূরবর্তী উৎস থেকে। সমসাময়িক কালের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলেই নতুন কালের জন্ম হয়। নিও ক্লাসিক্যাল কালের বৈশিষ্ট্য ছিল গতানুগতিক প্রচলিত ধারা, তার বিপরীতে রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্য হল নতুন সৃষ্টির প্রবলতা। মার্জিত, সচেতন শালীনতা, নিয়ন্ত্রিত আবেগের স্থলে মূল্যবান হয়ে উঠল স্বতঃস্ফূর্ততা। আগে ছিল সভ্যমানুষের প্রাধান্য, নতুন যুগে প্রধান হয়ে উঠল সহজ সরল গ্রামীণ জীবন। রোমান্টিক কবি হয়ে উঠলেন নিজেই তার কবিতার নায়ক। ক্লাসিক্যাল যুগে মানুষের সম্ভাবনা ছিল সীমিত, নতুন যুগে নিঃসঙ্গ বিদ্রোহী কবির সামনে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবে খুলে গেল সীমাহীন সম্ভাবনার দুয়ার।
রোমান্সধর্মী লোকসাহিত্য থেকে রোমান্টিক বিশেষণটি উদ্ভূত। একাদশ-দ্বাদশ শতকে জাত এই শব্দটা ছিল লোকজ জীবন ও ভাষার সঙ্গে সর্ম্পকিত
রোমান্টিকতার ধারা মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে হয়ে ওঠে নিওক্লাসিক ধারার প্রতিস্পর্ধী। রোমান্সধর্মী লোকসাহিত্য থেকে রোমান্টিক বিশেষণটি উদ্ভূত। একাদশ-দ্বাদশ শতকে জাত এই শব্দটা ছিল লোকজ জীবন ও ভাষার সঙ্গে সর্ম্পকিত। ইতালির সাধারণ মানুষের কথ্য লাতিনের সাথে আক্রমণকারী বর্বরদের ভাষার সংমিশ্রণে তার জন্ম। শঙ্কর রোমান্স ভাষা ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন্ত ভাষা, ক্লাসিক্যাল পরিশীলিত মার্জিত ভাষার তুলনায়। এই ভাষা উন্নতি লাভ করে দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রভাসঁ প্রদেশে। যেমন ভাবে আধুনিক কালে নেপলসের দক্ষিণে ফ্লোরেন্সে বিকশিত হয়েছিল রেনেসাঁ; ভূমধ্যসাগরের তীরে যোগোযোগব্যবস্থার কল্যাণে। মধ্যযুগীয় বীরদের কীর্তি; খ্রিষ্টধর্মের কাহিনীর অদ্ভূত, রহস্যময় অতিপ্রাকৃত জগৎ মধ্যযুগের লোকমানসকে সঞ্জীবিত করে রাখেছিল। মধ্যযুগের ইতালি ও ফ্রান্সে রোমান্স সাহিত্যের ঘটে ব্যাপক বিস্তৃতি। রোমান্স শব্দটি আঠারো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মন্দার্থে ব্যবহৃত হত, দ্বিতীয়ার্ধে ভালো অর্থবোধক হয়ে ওঠে। যেমন ‘বার্ড’ শব্দটি স্থ’ূল অর্থে ভবঘুরে বোঝাতো, সূক্ষার্থে চারণ বা কবি অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে রোমান্টিক আন্দোলনের পরে। ভোজবাজিকর শব্দটা সম্মানার্থক বীণাবাদক হিসাবে মূল্য পেতে শুরু করে।
রোমান্স যুগের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে এনে রোমান্টিক আন্দোলনের সূত্রপাত করে অগ্রপথিক জার্মান জাতি। ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) এবং দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের (১৭২৪-১৮০৪) কল্পনাতত্ত্বের ডানার ওপর ভর করে তার আবির্ভাব। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আন্দোলনের উদ্বোধক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন লেসিং (১৭২৯-১৭৮১)। যিনি ১৭৫৫ সালে মিস সারাহ স্যাম্পসন নাটকে সাধারণ জীবনভিত্তিক ট্র্যাজেডি রচনা করে জার্মান নাটকের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করেন। হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩) ছিলেন ‘স্টুর্ম উন্ট ড্র্যাঙ্গ’ সাহিত্য আন্দোলনের প্রধানপুরুষ। তিনি সহিত্যবিচারে ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। ১৭৭২ সালে এসে ‘অন অরিজিন অব ল্যাঙ্গুয়েজ’ রচনা করে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা করেন, যাতে উন্মোচিত হয় রোমান্স ভাষার উৎস ‘অরিজিন অব স্পেসিজ’। প্রতিভার যুগের মূল কথা হল প্রতিভার সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস, মধ্যযুগের প্রতি আকর্ষণবোধ, শৃঙ্খল থেকে কল্পনার মুক্তি, প্রকৃতির নতুন সর্বেশ্বরবাদী ধারণা, সর্ববিষয়বাদী ধারণা। ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, রাজনীতি সবই কবিতার মধ্যে উঠে এল— যাকে বলা যায় ‘কসমিক এক্সেনশন অব দ্য মিনিং অব পোয়েট্রি’। জার্মানরা যখন এগিয়ে যায় নতুন আন্দোলন নিয়ে, তখন ইংল্যান্ডে চলছিল নিও ক্লাসিসিজম যুগের সূর্যাস্তের সময়, যার অপর নাম ছিল জনসনের যুগ (১৭৪৫-১৭৯৮)। ড. জনসন যুক্তির ওপর কল্পনার প্রাধান্যকে অস্বীকার করেছিলেন। তার যুগের কবিরা অগাস্টান পোপের কালের (১৭০০-১৭৪৫) নিয়ন্ত্রিত দুর্গ ভেদ করে মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালেন। ইংরেজি সাহিত্যে এ যুগকে প্রি-রোমান্টিকদের যুগ বলা হয়। তাদের সময়টা ছিল দুই বিশাল যুগের মধ্যবর্তী উপত্যকা।
ফরাসি বিপ্লবের পরে শিল্পকলার সব ক্ষেত্রে রোমান্টিক আন্দোলনের প্রভাব বেগবান হয়ে ওঠে। ১৭৯৮ সালের পর ইউরোপীয় চিত্রকলায় স্টাইলের যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার বিশালতা একমাত্র রেনেসাঁ ছাড়া আর কখনো দেখা যায় নি
সে সময়ের কবিদের মধ্যে সবার আগে উচ্চারিত হয় টমাস গ্রে (১৭১৬-১৭৭১) ও উইলিয়াম কলিন্স (১৭২১-১৭৫৯)-এর নাম। স্কটল্যান্ডের সেরা কবি রবার্ট বার্নসের (১৭৫৯-১৭৯৬) মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভর করে তার স্বদেশী দার্শনিক ডেভিড হিউমের কল্পনাতত্ত্ব। আয়ারল্যান্ডের কবি উইলিয়াম ব্র্যাক (১৭৫৭-১৮২৭) কল্পনাকে ঈশ্বর সমতুল্য মনে করতেন। যিনি ছিলেন ইয়েটসের পূর্বসূরি, বিখ্যাত বাগ্মী এডমন্ড বার্ক ছিলেন যার স্বদেশী। ইংল্যান্ডে নিও ক্লাসিক্যাল যুগের অবসানের পর ১৭৯০-এর দশকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ আদর্শ হিসাবে বেছে নেন আদি বিপ্লবী জার্মানিকে। কারণ তখন ইংল্যান্ডের প্রি-রোমান্টিক কবিদের চেয়ে জার্মান কবি শিলার, শ্লেগেল, গ্যেটে ছিলেন বেশি প্রভাববিস্তারকারী। ১৭৭৫-১৮২০ কালে জেনা গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তখন শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়। শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়কে বলা যায় কল্পনার বরপুত্র, গ্রিম ব্রাদার্সকে যেমন বলা হয় রূপকথার জাদুকর। জ্যাকব গ্রিম (১৭৮৫-১৮৬০) এবং উইলহেম গ্রিম (১৭৮৬-১৮৫৯) মায়েদের মুখে মুখে প্রচলিত লৌকিক উপাখ্যান সংগ্রহ করেন— যার মধ্যে অন্যতম সিন্ডারেলা, ঘুমন্ত সুন্দরী, হ্যান্সেল ও গ্রেটেল। গ্রিম ব্রাদার্স ফিরে গিয়েছিলেন রহস্যময় অতীতে। একই রকমভাবে শ্লেগেল ব্রাদার্স আরোহণ করেন অতীন্দ্রিয় অপার্থিব জগতে, তবে অবশ্যই কল্পনার ডানায় ভর করে। তাদের তুলনা করা যায় রাইট ব্রাদার্সের সাথে, যারা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আকাশে উড়েছিলেন বাস্তবে।
ফরাসি বিপ্লবের পরে শিল্পকলার সব ক্ষেত্রে রোমান্টিক আন্দোলনের প্রভাব বেগবান হয়ে ওঠে। ১৭৯৮ সালের পর ইউরোপীয় চিত্রকলায় স্টাইলের যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার বিশালতা একমাত্র রেনেসাঁ ছাড়া আর কখনো দেখা যায় নি। নতুন যুগে আবির্ভূত হন ইউজিন দেলাক্রোয়া, টার্নার, গোইয়া, ডাভিড, এডওয়ার্ড মানে, পল সেজান প্রমুখ। ১৭৯৮ সালে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ দুই বন্ধু মিলে প্রকাশ করেন লিরিক্যাল ব্যালাডস। এ বছর রোমান্টিকতার মুখপত্র শ্লেগেলের ডাস এথিনাকাম পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে দুই বন্ধু ভ্রমণ করেন শ্লেগেলের জার্মানি। তাদের কাব্যের ভূমিকায় অনুকরণ নয়, জায়গা দখল করে নেয় আবেগের উপপ্লব। মধ্যযুগীয় রোমান্স ব্যালাডের জগতে ফিরে যায় লিরিক্যাল ব্যালাডস, যেখানে সহজ সরল গ্রামীণ জীবন, সাধারণ মানুষের ভাষার প্রাধান্য দেখা যায়। যাকে অভিহিত করা যায় ‘এপিক অব পারসোনাল এক্সপেরিয়েন্স’ বলে। কোলরিজের ‘এনসিয়েন্ট মেরিনার’ যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পালতোলা জাহাজের নাবিক, যার দল ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করে ১৭৫৭ সালে। ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের পর পরাজিত সেনাপতি ওয়ারেন হেস্টিংস যেনো ভারতে এসে নতুন সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করে। অস্ট্রেলিয়াতে ক্যাপ্টেন কুক অভিযান পরিচালনা করে ১৭৮৮ সালে, কানাডায় উপনিবেশ স্থাপন করে ১৭৯১ সালে।
ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় শোনা যায় কোকিলের ডাক, কোকিল হল প্রসন্নতার প্রতীক; শেলির কবিতায় শোনা যায় স্কাইলার্কের উদ্দাম পক্ষধ্বনি, কীটসের নাইটেঙ্গেল হয়েছে সৌন্দর্যের প্রতীক আর বায়রনের ঈগল বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি। কোলরিজের আলবাট্রস প্রতীক স্বপ্নের
লর্ড বায়রনের এডভেঞ্চারের প্রকাশ রক্ষণশীলতা নয়, বহন করে নতুন যুগ বিপ্লবের বাণী। কোলরিজের বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া (১৮১৭) কাব্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করে। সেইন্ট বেরি বলেিেছলেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামালোচক ত্রয়ীর অন্যতম হলেন কোলরিজ। প্রাচীনকলের অ্যারিস্টটল ও লঙ্গাইনাস, আধুনিক কালে কালরিজ। কোলরিজ জার্মানিতে গিয়ে কান্ট, শিলার, রিকটার এবং শ্লেগেল ভ্রাৃতৃদ্বয়ের কাছ থেকে ভাবরসে পুষ্ট হয়ে এসেছিলেন। তিনি বিখ্যাত হন সমালোচনাতত্ত্বে ইমাজিনেশনের আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে এবং তার দার্শনিক ভিত্তি তৈরি করে। উনিশ শতকে মনস্তত্ত্ববিদ্যার জন্মের প্রেক্ষাপটেই এটা সম্ভব হয়। শেলি ছিলেন বিপ্লবী রোমান্টিক কবি, তাকে বলা যায় রোমান্টিক যুগের প্রমিথিউস আনবাউন্ড (১৮২০)। কীটসের (১৭৯৫-১৮২১) কবিতায় বিষয়মুখ্যতা নয়, স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা; কাহিনি নয়, মিথ, প্রতীক, স্বজ্ঞা, অবতেচতন প্রাধান্য পায়। জে. আইজাকস বলেন, বিশুদ্ধ কবিতার প্রথম তরঙ্গ রোমান্টিক আন্দোলন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ তার অগ্রপথিক; শেলি ও কীটস সর্বোচ্চ সীমা আর টেনিসনে অবক্ষয় ।
ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় শোনা যায় কোকিলের ডাক, কোকিল হল প্রসন্নতার প্রতীক; শেলির কবিতায় শোনা যায় স্কাইলার্কের উদ্দাম পক্ষধ্বনি, কীটসের নাইটেঙ্গেল হয়েছে সৌন্দর্যের প্রতীক আর বায়রনের ঈগল বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি। কোলরিজের আলবাট্রস প্রতীক স্বপ্নের। এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকায় বিজয়ের প্রেক্ষাপটেই রচিত হয় কোলরিজের এনসিয়েন্ট ম্যারিনার এবং তার কুবলাই খান জানাডা চীন অভিযান এবং উত্তরমেরু অভিযানের স্মারক। কোলরিজের নাবিকের জয়জয়াকারের পরপরই ভারতবর্ষে আবির্ভূত হন ‘ভোরের পাখি’ বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)। তার স্বপ্নদর্শন, নিসর্গ সন্দর্শন, প্রেম প্রবাহিনী, মায়া দেবী, দেব রানী— এসব কাব্যের নামের মধ্যেই ধরা পড়ে রোমান্টিকতার সব বৈশিষ্ট্য। সারদামঙ্গলে খুঁজে পাওয়া যায় শেলির নায়িকার প্রতিচ্ছবি, স্বপ্নদর্শনের মধ্যে পাওয়া যায় কোলরিজের আলবাট্রস পাখির ভেসে বেড়ানোর চিত্র। স্বপ্নদর্শন প্রকাশের পরপরই জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার চতুর্দশবর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ১৮৭৫ সালের ৬ ডিসেম্বর বোটে করে শিলাইদহের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। পূর্ববঙ্গে প্রথম সফরে হল নিসর্গ সন্দর্শন, যার দেখা পেয়েছিলেন বিহারীলাল ১৮৭০ সালেই। তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হয়েছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটসের সৌন্দর্যবোধ দিয়ে। সন্ধ্যাসঙ্গীত-প্রভাতসঙ্গীত পর্বের কবিতা (১৮৮১-১৮৮৩), ছবি ও গান-মানসী পর্বের কবিতা (১৮৮৪-১৮৯০) নিভৃতবাসের সঙ্গে যুক্ত হয় সঙ্গীত ও চিত্র। তবে পূর্ববঙ্গে আসার পর হল কর্মের অভিষেক। কর্মের পথ প্রসারিত হল এভাবে যে রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ জীবনের প্রতি রোমান্টিক ভালবাসার অংশ হিসাবে তার পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে কৃষিবিদ্যা ও গোপালনবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য আমেরিকায় পাঠান ১৯০৬ সালে। পুত্র ও জামাতা আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যা শিখে এলে সপরিবারে বসালেন শিলাইদহে।