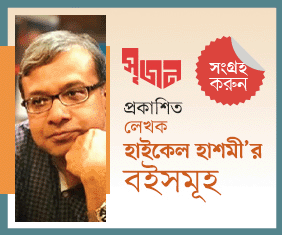ছাত্রাবস্থায় লোকাল ট্রেন বা বাসে চড়ার অভিজ্ঞতা হয়নি এমন মধ্যবিত্ত সন্তান বিরল। কলেজের হোস্টেলে সিট পাওয়ার আগ পর্যন্ত কিছুদিন সকাল বেলায় ডেলি প্যাসেঞ্জার আর ভিক্ষুক বোঝাই করে ফেনী শাটল নামের যে ট্রেনটি চট্টগ্রাম পর্যন্ত যেতো, সেই ট্রেনে চড়ে কলেজে হাজিরা দিয়েছি বহুদিন। স্থানীয় লোকজন মজা করে এই ট্রেনের নাম দিয়েছিল ‘ফইন্নির ট্রেন’। ফেরার সময় প্রায়ই আসতে হতো শুভপুরের লোকাল বাসে। কারণ চট্টগাম থকে ফেনী বা নোয়াখালির লংরুটের বাসে আমরা লোকালরা ছিলাম অন্ত্যজ শ্রেণীর যাত্রী। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরও হলে সিট পাওয়ার আগে কয়েক মাস শ্যামলী থেকে গাবতলী-গুলিস্থান লোকাল বাসে চড়ে নীলক্ষেত নেমে তারপর ক্লাস ধরতে হতো।
এই সব অভিজ্ঞতা প্রায় যখন ভুলতে বসেছি, তখন এরকম লোকাল সার্ভিসের দেখা পাওয়া গেল আকাশপথে। আমাদের গন্তব্য উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ। এক কাকভোরে ঢাকা থেকে উড়ান দিই বাংলাদেশ বিমানে, সেটি প্রথমে যায় চট্টগ্রাম, এটি ছিল আমাদের জন্য এক ‘বিপন্ন বিস্ময়’, কারণ ফ্লাইটটি প্রথমে চট্টগ্রাম যাবে জানার পর আমাদের কিছুই করার ছিল না। চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের রানওয়েতে আমরা প্লেনের পেটের মধ্যে বসে থাকতেই সেখান থেকে যাত্রীরা ওঠে। বলাবাহুল্য, সবসময়ের মতো কয়েকজন পরিচিত যাত্রীর দেখা মিলে যায়। তারা এই কলকাতাগামী ফ্লাইটে আমাদের অপেক্ষমান দেখে অবাক হলেও কিছু বলে না। অবশেষে ঠিক সময়ে চট্টগ্রাম ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করে বিমান এবং নির্ধারিত সময়েই কলকাতা নামিয়ে দেয় আমাদের। বিমানও যে কাঁটায় কাঁটায় শিডিউল রক্ষা করতে পারে, তার প্রমাণ পেয়ে অবাক হই। কলকাতায় কয়েকঘণ্টা যাত্রাবিরতির পর ধরতে হয় দিল্লিগামী ফ্লাইট। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছি তখন শেষ বিকেলের আলো স্তিমিত হয়ে এসেছে। হোটেলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। সে রাত দিল্লিতে পার করে পরদিন আবার দুপুরের পর দিল্লি থেকে চড়তে হয় তাসখন্দগামী ফ্লাইটে। অবশেষে তাসখন্দ পৌঁছা গেল সেদিন সন্ধ্যার পর। ছত্রিশ ঘন্টার এই দীর্ঘ ও ভাঙা ভাঙা যাত্রাপথের বর্ণনা এত সহজে লিখে ফেলতে পারি, কারণ সিল্করুটের একটি অংশে প্রথমবারের মতো পা রাখার উত্তেজনা দীর্ঘ এই যাত্রার ক্লান্তিকে মুছে দিয়েছিল। উল্লেখ করা দরকার, তাসখন্দ নামের অর্থ ‘পাথর নগরী’, এই নামটি প্রথম ব্যবহার করে তুর্কিরা। বিখ্যাত সিল্করুটের সংযোগস্থল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ এক নগরী হয়ে ওঠে তাসখন্দ এবং পরিনত হয় মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী নগরীতে।
তাসখন্দ এয়ারপোর্টে আমাদের নিতে আসে স্থানীয় ট্রাভেল এজেন্টের দুই প্রতিনিধি মোহাম্মদ ও আলিশের বাইসভ। উল্লেখ্য নায়কোচিত চেহারার যুবক আলিশের নিজেই এই এজেন্সির মালিক। স্বয়ং মালিক এয়ারপোর্টে আমাদের নিতে এসেছেন দেখে আমরা যারপরনাই অবাক। আমাদের গন্তব্য আমির তিমুর স্ট্রিটের ওপর দাঁড়ানো সিটি প্যালেস হোটেল। হোটেলের লবিতে ঢুকেই চোখ জুড়িয়ে যায়। লবির দুপাশ দিয়ে উঠে গেছে তিনতলা সমান উঁচু দুই থাম, তার একটিকে লতার মতো পেঁচিয়ে ধরে সিড়ি উঠে গেছে মেজনাইন ফ্লোর পর্যন্ত। আরেকটি নিঃসঙ্গ থাম ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। দুটো থামের গায়েই টাইলসের ওপর জ্যামিতিক নকশা আর ফুলের কারুকাজ। লবির অন্য দেয়ালগুলোতেও ময়ুরকন্ঠি নীলপ্রধান একই ধরনের নকশা। পরে ঠিক এরকম নকশার কারুকাজ দেখতে পাই বুখারা সমরকন্দের বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপত্যে। ভবনটির আধুনিক স্থাপত্যের ভেতর এরকম প্রাচীন অন্তঃসাজ প্রত্যাশার অতীত।

হোটেলে চেক ইন করার আনুষ্ঠানিকতা সারার পর আমাদের রাতের খাবার খেতে নিয়ে যায় আলিশের। হোটেল থেকে বড় রাস্তায় নামার পর মাথার ওপর ছোট ছোট বাতির সাজ সজ্জা দেখে মনে হয় কোনো বিশেষ উপলক্ষে এই আলোকসজ্জা। আলিশেরকে মজা করে জিজ্ঞেস করি, এই আয়োজন কি আমাদের সম্মানে? ও জবাবে বলে, সেটা আমরা ভাবলেও ভাবতে পারি, কারণ কোনো বিশেষ উপলক্ষ নয়, এই আলোকসজ্জা নগরীর নৈশশোভা বর্ধনের জন্যই। কাছাকাছি যে রেস্তোঁরায় আমাদের খেতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেটিতে রাতের এই প্রহরেও জনসমাগম দেখে বোঝা যায় খুব মশহুর ওটা। ওসব দেশে ডিনার সারা হয় সন্ধ্যার পরপরই। খাওয়া শেষে যখন আমরা বের হয়ে আসি, তখন প্রায় টেবিলই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাইরের ৪ ডিগ্রি ঠান্ডায় সামনের চত্বরটায় কিছুক্ষণ চড়ে বেড়াবো, সে উপায় নেই।
তাসখন্দে যাওয়ার আগেই ভেবে রেখেছিলাম পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিখ্যাত তাসখন্দ চুক্তিটি যেখানে হয়েছিল সেই জায়গাটা দেখতে যাবো। উল্লেখ্য ১৯৬৫ সালের সেই যুদ্ধ ১৭ দিনের বেশি চলেনি, এর মধ্যে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করে। অথচ এই যুদ্ধের প্রায় তিরিশ বছর আগে মুসোলিনি আফ্রিকার আবিসিনিয়া (বর্তমানের ইথিওপিয়া) দখল করে নিলেও বর্তমান জাতিসংঘের মতো ঠুঁটো জগন্নাথ তখনকার লিগ অভ নেশনস কিছুই করতে পারেনি। যা-ই হোক পাকভারতের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হলেও পরবর্তী সময়ে অমিমাংসিত বিষয়গুলো নিষ্পত্তির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই কোসিগিনের উদ্যোগে তাসখন্দ শহরে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরের রাতেই শাস্ত্রীকে হোটেলের রুমে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আকস্মিক এই মৃত্যুকে অনেকেই স্বাভাবিক মনে না করলেও এটি অপমৃত্যু ছিল কি না, তার সুরাহা হয়নি আর।
কিশোর বয়সের দেখা সেই যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরের জায়গাটি নিয়ে আমাদের চারভ্রমণসঙ্গীরই বিশেষ আগ্রহ ছিল। গুগলে অনেক খুঁজেও জায়গাটার হদিস পাইনি, আলিশেরকে জিজ্ঞেস করলে ও মাথা চুলকে সেখানেই জায়গাটা খোঁজার চেষ্টা করে। বুঝতে পারি এদের জন্ম ষাটের দশকের পরে বলে দুই বিদেশী যুদ্ধবাজ নেতার চুক্তির খবর এদের জানা নেই। আমরা ওকে বলি, বয়স্ক কাউকে জিজ্ঞেস করে যাতে আমাদের জানায়। আমাদের উজবেকিস্তানে থাকা অবধি বয়স্ক কোনো লোককে ও খুঁজে পায়নি বলেই মনে হয়।
তাসখন্দ চুক্তির ঐতিহাসিক জায়গাটা বের করতে না পারলেও জন্য আরও প্রাচীন একটা ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখানোর ব্যবস্থা ছিল আমাদের ভ্রমণসূচিতে। ঝকঝকে রোদের মধ্যে আমরা যেখানে গিয়ে গাড়ি থেকে নামি, সেটি এক চমৎকার স্থাপত্যমন্ডিত মসজিদচত্বর। বরফশুভ্র দেয়ালের গায়ে পরিমিত নীল লতাপাতার নকশা, তার পাশে দীর্ঘ মিনার, ফিরোজা রঙের গম্বুজ— সবকিছু এতটাই পরিচ্ছন্ন, যেন মনে হয় মাত্র গতকাল শেষ হয়েছে মিনর মসজিদ নামে পরিচিত এই স্থাপনার কাজ। প্রকৃতপক্ষেই মসজিদটি একেবারেই আনকোরা নতুন, মাত্র সেদিন অর্থাৎ ২০১৪ সালে এটির উদ্বোধন করা হয়। সেকারণে এর সাথে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বা কিংবদন্তির গল্প জড়িত নেই। প্রাচীন স্থাপত্যের মসজিদগুলোর সাথে এটির কোনো মিলও নেই। এর শ্বেতপাথরের দেয়াল পুরো আবহে ছড়িয়ে দিয়েছে এক পবিত্রতার আমেজ। প্রখর সূর্যালোকে এই শুভ্রতা আরও বেশি ঝকঝক করে যেন। দুপাশে দুটো দীর্ঘ মিনার মেঘমুক্ত নীলাকাশের দিকে তর্জনী তুলে দাঁড়ানো, মূল মসজিদের ওপর একটা আকাশি নীল গম্বুজকে দূর থেকে উল্টানো এক বিশাল গামলার মতো দেখায়। বিশাল উঁচু তোরণের গায়ে শ্বেতপাথরের ওপর লতাপাতার কাজ। মেহরাবের মতো ভেতর দিকে অবতল অংশের শীর্ষে প্রাচীন যুগের সাংকেতিক চিহ্নের মতো নানান নকশা আঁকা। তার ওপরের চাঁদওয়ারিতে দীর্ঘ কোরানের আয়াত উৎকীর্ণ। তোরণের পায়ের কাছের বেমানান কাঠের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে প্রশস্ত চাতাল, তার দুপাশে টানা বারান্দার মতো করিডর। বিপরীত প্রান্তে মসজিদে ঢোকার প্রায় একই ধরনের নকশাশোভিত একই উচ্চতার আরেকটি তোরণ। সেটির মাঝখানের মূল কাঠের দরজাটি কেবল মহিলা নামাজী ও দর্শনার্থীদের জন্য সংরক্ষিত, দুপাশে দুটো করে আরও চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট দরজা, সেগুলো পুরুষদের জন্য। প্রায় আড়াই হাজার মানুষ একসাথে নামাজ পড়তে পারে এই মসজিদে। ভেতরে গম্বুজের বিশাল ঘেরের নিচে প্রশস্ত হলরুম, হলরুমের দেয়াল জুড়ে মেঝে থেকে উঠে যাওয়া দরজার দ্বিগুণ উচ্চতার বিশাল সব জানালা গলে ঢুকছে দিনের আলো। গম্বুজের ঘের জুড়ে নকশার সুষম কাজ, তার ওপরের অংশে বাঁকানো খিলানের গবাক্ষের বৃত্তাকার সারি, সেখান থেকেও ঝরে পড়ছে স্নিগ্ধ দিবালোক। গম্বুজের ছাদের তলার কেন্দ্র সূক্ষ্ম নকশায় পরিপূর্ণ। কেবলামুখি মেহরাবটি সোনার গিল্টিকরা নকশা আর আরবি ক্যালিগ্রাফিতে পরিমিতভাবে সাজানো।

মসজিদটির নাম মিনর মসজিদ হলেও এটি ‘শ্বেত মসজিদ’ নামেও পরিচিত। হোটেল থেকে রওনা হওয়ার সময় গাইড মোহাম্মদ যখন জানায় আমাদের পরবর্তী গন্তব্য খাস্ত ইমাম কমপ্লেক্স, ভেবেছিলাম তুষারশুভ্র এই মসজিদটিই খাস্ত ইমাম। অবশ্য এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে খাস্ত ইমাম কমপ্লেক্সে পৌঁছার পর সে ভুল ভাঙে। কমপ্লেক্সটির পোশাকি নাম খাজরাতি ইমাম। এখানে আছে বারাক খান মাদ্রাসা, তিল্লা শেখ মসজিদ, মুই মুবারক মাদ্রাসা, কাফ্ফাল শাশির মাজার ইত্যাদি। উল্লেখ্য এই কাফ্ফাল শাশির পুরো নাম আবু বাকার আল-কাফ্ফাল আল-কাবির আশ-শাশি। তাঁর ছিল কোরান, হাদিস ও ইসলামি আইন সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান। তিনি ছিলেন কবি ও গীতিকার এবং ব্যতিক্রমীভাবে ছিলেন এক দক্ষ তালার কারিগর (কাফ্ফাল), তাই তাঁর নামের সাথে আল কাফ্ফালও যুক্ত হয়েছে। ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর প্রায় সাতশ বছর পর তাঁর কবরের ওপর তৈরি দরগা পরিনত হয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের তীর্থভূমিতে।
খাস্ত ইমাম কমপ্লেক্সের তিল্লা শেখ মসজিদের সামনে দিয়ে বেশ কিছুদূর হেঁটে গেলে মুয়ি মুবারক মাদ্রাসা ও কুতুবখানা, যেখানে রক্ষিত আছে হজরত উসমান (রাঃ)এর সময়ে তাঁর হাতে লেখা কুফি কোরানের প্রাচীনতম পান্ডুলিপির একটি। কুফি হচ্ছে আরবি হরফের প্রাচীনতম রূপ, যা সপ্তম শতাব্দীতে কুফা নগরে প্রবর্তিত হয়। এটি যখন উজবেকিস্তানে আসে তখন ধারণা ছিল যে এটিই কোরানের প্রাচীনতম পান্ডুলিপি। কিন্তু গবেষকদের মতে এটি লেখা হয়েছিল অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে। কিন্তু হজরত উসমান (রাঃ) নিহত হয়েছিলেন ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে, সুতরাং গবেষকদের ধারণা যদি সঠিক হয় এটি তাঁর হাতে লেখা এমনকি তাঁর আমলের হওয়াও সম্ভব নয়। কিংবা যদি সত্যিই তা-ই হয়, তাহলে গবেষকদের ধারণা ভুল। তবে এই বিতর্ক বা বিভ্রান্তির সুরাহা করা এখানে সম্ভব নয়।
ইস্তাম্বুলের তোপ কাপি প্রাসাদের জাদুঘরেও এরকম প্রাচীন কোরানের পান্ডুলিপি রক্ষিত আছে। সেটির ছবি তুলতে গেলেই প্রহরীরা ‘রে রে’ করে ছুটে আসে। এটিকেও প্রাচীনতম পান্ডুলিপি বলে দাবী করা হয়, গবেষকরা এখানেও বাগড়া দিয়ে বলেছেন এটি প্রাচীনতম না হলেও উসমানীয়া কোরানের চেয়ে অন্তত এক শতাব্দী আগের।
কোরানের প্রাচীনতম সংস্করণ নিয়ে এযাবত যেসব তথ্য পাওয়া যায়, সে হিসেবে ব্রিটেনের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পান্ডুলিপির দুটি পাতাই এযাবত পাওয়া সবচেয়ে প্রাচীন সংস্করণ বলে মনে করা হয়। কার্বন পরীক্ষার মাধ্যমে ধারণা করা হয় চামড়ার তৈরি পাতায় এটি লেখা হয়েছে ৫৬৮ থেকে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদ (সঃ)এর নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম দিকে। কালের হিসেবে ইয়েমেনের রাজধানী সানায় পাওয়া চামড়ার তৈরি কাগজে দুই পাতার পান্ডুলিপিটি দ্বিতীয় প্রাচীনতম বলে গবেষকদের মত। মনে করা হয় এটি লেখা হয়েছে ৬৪৬ থেকে ৬৭১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। গবেষকদের হিসেবে তোপ কাপি প্রাসাদে রক্ষিত কোরানের পান্ডুলিপিটি ৭৬৫ থেকে ৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছে। এটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ পান্ডুলিপি হলেও দুটো পৃষ্ঠা নেই। সে হিসেবে তাসখন্দে আমাদের দেখা পান্ডুলিপিটি চতুর্থ প্রাচীনতম কোরান।
নেপোলিয়নের মিসর জয়ের পর এটি দুই অংশে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্যারিসে চলে আসে। একাংশ নিয়ে আসেন নেপোলিয়নের সাথে যাওয়া শিল্প বিশারদ জাঁ জোসেফ মার্শেল। পরবর্তী সময়ে আরও কিছু পৃষ্ঠা নিয়ে এসেছিলেন সে সময় কায়রোতে ফরাসি ভাইস কনসাল হিসেবে কর্মরত জোঁ লুই শেরভিল। এই দুই অংশ এঁদের উত্তরাধিকারীরা বিভিন্ন সময়ে বিক্রি করে দেওয়ার পর এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছড়িয়ে আছে ফ্রান্সের ন্যাশনাল লাইব্রেরি, সেন্ট পিটার্সবার্গে রাশিয়ার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ভ্যাটিকান লাইব্রেরি এবং লন্ডনের খলিলি কালেকশানে
পরবর্তী পান্ডুলিপিটা এক সময় রক্ষিত ছিল মিসরের আমর ইবনে আস মসজিদে। নেপোলিয়নের মিসর জয়ের পর এটি দুই অংশে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্যারিসে চলে আসে। একাংশ নিয়ে আসেন নেপোলিয়নের সাথে যাওয়া শিল্প বিশারদ জাঁ জোসেফ মার্শেল। পরবর্তী সময়ে আরও কিছু পৃষ্ঠা নিয়ে এসেছিলেন সে সময় কায়রোতে ফরাসি ভাইস কনসাল হিসেবে কর্মরত জোঁ লুই শেরভিল। এই দুই অংশ এঁদের উত্তরাধিকারীরা বিভিন্ন সময়ে বিক্রি করে দেওয়ার পর এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছড়িয়ে আছে ফ্রান্সের ন্যাশনাল লাইব্রেরি, সেন্ট পিটার্সবার্গে রাশিয়ার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ভ্যাটিকান লাইব্রেরি এবং লন্ডনের খলিলি কালেকশানে। পরবর্তী সংস্করণের পান্ডুলিপিগুলোও যথাক্রমে রক্ষিত আছে তিউনিসের বারদো জাতীয় যাদুঘর, আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে চেস্টার বেটি লাইব্রেরি এবং জার্মানীর মিউনিকের ব্যাভারিয়ান স্টেট লাইব্রেরিতে।
মুয়ি মুবারক কুতুবখানায় ঢোকার সময় টিকিট কিনতে হয়, তবে সেসব গাইড মোহাম্মদের মাথাব্যথা। মূল দরজার মুখে জুতা খুলে রেখে ঢুকতে হয়। বড় হলরুমের মাঝখানে উঁচু বেদির ওপর কাচের বড় কাসকেডের ভেতর মেলে রাখা বিশাল পাতা জুড়ে ভারি হরফে লেখা বারোশ বছরের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থটি দেখে যে অনুভূতি হয়, সেটি ছাপিয়ে অনুভব করি এটি কেবল প্রাচীন একটি পান্ডুলিপিই নয়, বিশ্বাসী মানুষের কাছে পরম আবেগ ও সম্মানেরও। হরিণের চামড়ার কাগজে লেখা ৩৫৩ পৃষ্ঠার এই পান্ডুলিপির পাতার ওপর রয়েছে রক্তের দাগ, প্রচলিত ধারণা ছিল, এই কোরান পাঠরত অবস্থায় হজরত উসমান (রাঃ)কে হত্যা করা হয়। কিন্তু গবেষকদের হিসেব অনুযায়ী এটির যে বয়স তাতে বোঝা যায় এটি লেখা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর। সুতরাং রক্তের দাগের উৎসটিও অমীমাংসিত। গাইড মোহাম্মদ আমাদের জানায়, এই পান্ডুলিপি থেকে অনেকগুলো পাতা খোয়া গেছে।
এযাবৎ পাওয়া তথ্যমতে উসমানীয়া কোরানটি রক্ষিত ছিল বাগদাদে। সেখান থেকে সমরকন্দে আসার বিষয়টি অস্পষ্ট। হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণ (১২৫৮), পাইকারি হত্যাযজ্ঞ লুটপাটের সময় মঙ্গোল সৈন্যরা মসজিদ, প্রাসাদ, হাসপাতাল লাইব্রেরি— কিছ্ইু বাদ দেয়নি। বাগদাদের ছত্রিশটি পাবলিক লাইব্রেরি থেকে অমূল্য বইগুলো ছিঁড়ে সেগুলোর চামড়ার মলাট দিয়ে তারা চপ্পল বানায়। বাগদাদের গ্র্যান্ড লাইব্রেরিতে ছিল অগনিত ঐতিহাসিক দলিল এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা সহ বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যবান গ্রন্থরাজি। সেসব ধ্বংস করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা পরে জানায় টাইগ্রিস নদীর পানি ফেলে দেওয়া বইয়ের কালিতে কালো এবং হত্যা করা বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের রক্তে ছিল লাল। সেই ডামাডোলে পান্ডুলিপিটি ইরাকের কোনো নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান রক্ষা করেছিলেন হয়তো। তা না হলে তৈমুর লং পান্ডুলিপিটি ইরাক থেকে সমরকন্দ নিয়ে এসেছিলেন বলে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে তার কোনো ভিত্তি থাকে না। এটি সমরকন্দের মসজিদেই রক্ষিত ছিল প্রায় চারশ বছর। ১৮৬৮ সালে সমরকন্দ রাশিয়ান সাম্রাজ্যের করতলগত হয়। এই মূল্যবান পান্ডুলিপিটির কথা জানতে পেরে জেফারশানের জেলা প্রশাসক জেনারেল আব্রামভ মসজিদের তত্ত্বাবধায়কদের ১০০ স্বর্ণমুদ্রা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়ে এটিকে তাসখন্দ পাঠিয়ে দেন। পরের বছর গভর্নর জেনারেল ভন কাউফম্যান এটি পাঠিয়ে দেন সেন্ট পিটার্সবার্গের ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতে। অক্টোবর বিপ্লবের পর লেনিন পান্ডুলিপিটি রাশিয়ার বাশকর্তোস্তানের মুসলমানদের দান করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯২৪ সালে এটির মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া হয় উজবেকিস্তানকে।
বাগদাদের ছত্রিশটি পাবলিক লাইব্রেরি থেকে অমূল্য বইগুলো ছিঁড়ে সেগুলোর চামড়ার মলাট দিয়ে তারা চপ্পল বানায়। বাগদাদের গ্র্যান্ড লাইব্রেরিতে ছিল অগনিত ঐতিহাসিক দলিল এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা সহ বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যবান গ্রন্থরাজি। সেসব ধ্বংস করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা পরে জানায় টাইগ্রিস নদীর পানি ফেলে দেওয়া বইয়ের কালিতে কালো এবং হত্যা করা বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের রক্তে ছিল লাল। সেই ডামাডোলে পান্ডুলিপিটি ইরাকের কোনো নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান রক্ষা করেছিলেন হয়তো
মুয়ি মুবারক কুতুবখানার ভাবগম্ভীর পরিবেশে অতি সন্তর্পনে কাচের বাক্সটির সামনে গিয়ে দাঁড়াই। নিজেদের মধ্যে কথাও বলি ফিসফিস করে, এটা কেউ বলে দেয়নি, কিন্তু এমন জায়গায় গেলে আপনা থেকেই গলা নিচু হয়ে আসে, হাঁটা হয় পা টিপে টিপে। কাসকেডের ভেতর বিশাল গ্রন্থটির পাতায় পাতায় হাতে লেখা ঐশী বাণী নিজের হাতে লিপিবদ্ধ করা লেখকের নিষ্ঠার প্রতি নিজের অজান্তে মাথা নুয়ে আসে। ঘরটির এক কোণে চেয়ারে বসে সতর্ক চোখে আমাদের গতিবিধি লক্ষ করে এক নিরাপত্তা কর্মী। আমরা কিছু সময় কাচের বিশাল বাক্সটির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সরে আসি। লোকটির দৃষ্টি এড়িয়ে একখানা ছবি তোলার সাহস করি না। তুলতে পারলেও কাচের বাধার কারণে ভালো ছবি আসবে না জানি। গুগলে গেলে বরং এই পান্ডুলিপির অনেক ছবি পাওয়া যাবে। পাশের অপেক্ষাকৃত ছোট রুমে ঢুকলে দেখা যায় কাচের শোকেসের ভেতর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কোরান সাজানো আছে দর্শনার্থীদের জন্য। বাংলা একটা কোরানও সেখানে থাকার কথা, কিন্ত চোখে পড়েনি।
মুয়ি মুবারক কুতুবখানার পেছনে খাস্ত ইমাম মসজিদের সুদৃশ্য ভবন, তার দুপাশে দুটো উঁচু মিনার, ভেতরের পাশে দুটো ফিরোজা রঙের গম্বুজ। এই মসজিদটির নির্মাণকাজ শেষ হয়েছিল মাত্র চার মাস সময়ের মধ্যে, ২০০৭ সালে। ভেতরের স্তম্ভগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে ভারত থেকে আনা চন্দন কাঠ, তুরস্কের সবুজ মার্বেল পাথর, ইরানের নীল টাইলস।
এর সামনের খোলা বাঁধানো চত্বরের উল্টো পাশে ষোড়শ শতাব্দীর বারাক খান মাদ্রাসা ও মসজিদ। মূল প্রবেশদ্বারটি বুখারা সমরকন্দের বিভিন্ন মাদ্রাসার মতো বিশাল উঁচু পোড়া ইটের তৈরি, তার ওপর বর্ণিল জ্যামিতিক নকশা, চাঁদওয়ারিতে গাঢ় নীল পটভূমিতে লতানো ফুলের কারুকাজ। ভেতরে অবতল প্রকোষ্ঠে ইসলামি স্থাপত্যের নিদর্শন বাঁকানো খিলানের দুই তলা কুলুঙ্গি। মাঝখানের মূল দরজার ওপর জাফরি কাটা গবাক্ষ। ফটকের দুপাশে দুটো নীল রঙের গম্বুজ। ভেতরে ঢুকলে আরেকপ্রস্ত চাতাল পার হয়ে কেন্দ্রের মূল প্রশস্ত ঘরটিতে নানান স্যুভেনিরে ঠাসা দোকান। ঢোকার মুখেও সাজিয়ে রাখা উজবেকিস্তানের ট্রাডিশনাল হস্তশিল্পের নানান পণ্য, পেইন্টিং, পোশাক। ভেতরের বিভিন্ন পণ্য দেখে আমরা যখন ওদের সাথে দর কষাকষি করি, তখন গাইড মোহাম্মদ সবার কানের কাছে এসে আস্তে আস্তে বলে যায়, এখান থেকে কিছু না কেনাই ভালো, অনেক দাম নেবে। আপনাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাবো, সেখান থেকে কিনতে পারবেন। মোহাম্মদের এই উপদেশের পর থেকে বেশ কয়েকটা জিনিস পছন্দ হওয়ায় কিনতে মনস্থ করার পরও সেগুলোর দাম অহেতুকরকম বেশি মনে হতে থাকে। তাই দরকষাকষি করে নামিয়ে আনা দামেও সে সব আর কেনা হয় না।
লেখক: গল্পকার, অনুবাদক এবং ব্যাংকার