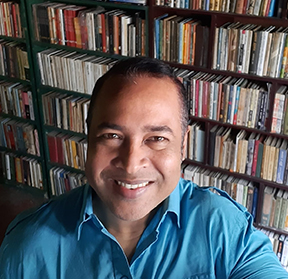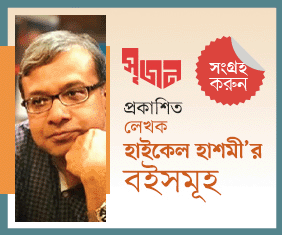বায়ো শব্দটি গ্রিক, যার অর্থ হচ্ছে জীবন। বায়োসেন্ট্রিজম শব্দটার অর্থ করা যেতে পারে জীবনকেন্দ্রবাদ। এই টার্মটি দার্শনিকরা ব্যবহার করেছেন দর্শনের ইতিহাসে। সাম্প্রতিক এটা আবারো আলোচিত হচ্ছে চিন্তার জগতে। পুঁজিবাদের উন্নয়নের লেলিহান আগুনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এটি জীবন-প্রকৃতি রক্ষার কথা বলে। বিশেষ করে উন্নয়নের লাগামহীন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে দুনিয়ার পরিবেশের যে ক্ষতি হয়ে চলেছে, তার সমালোচনা করে বায়োসেন্ট্রিজম। সবার উপরে মানুষ সত্য তথা মানবতাবাদ জগতের নিরন্তর ক্ষতি করে চলেছে। মানবতাবাদে দেখা যাচ্ছে সব মানুষ সবার উপরে সত্য নয়, কিছু মানুষ সত্য যারা হয়তো নিৎসের মানুষ, হয়তো ডারউইনের মানুষ। যারা ফিট এটা পুঁজিবাদের সঙ্গে বেশ খাপ খায়। বায়োসেন্ট্রিজম এর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, খানিকটা ভারতীয় দর্শনের সর্বপ্রাণবাদের মতো। সমকালীন বিজ্ঞানী রবার্ট ল্যানজা তার বই ‘বায়োসেন্ট্রিজম’-এ কোয়ান্টাম থিওরিকে আত্মা নির্ধারণের উপায় বলে দেখাচ্ছেন। এর আগে তিনি স্টেম সেল ও অ্যানিমেল ক্লোনিং নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছেন। এখন কোয়ান্টাম ফিজিক্স নিয়ে ব্যস্ত। তিনি বলছেন, আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা আমরা পর্যবেক্ষণের আগেই সূত্রের ধার ধারছি আরসেখানে সবচেয়ে ভিত্তিপূর্ণ ভুল হলো সচেতন অবস্থার সচেতনতা, যাতে কিনা প্রয়োগ হচ্ছে পূর্বোক্ত শেখা সূত্র। সেখানে নিজে দেখা, নিজে জানার বিষয়টা লুকিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো বলছেন, এই মহাবিশ্ব, আকাশ, সময় এগুলো আর আমরা সবটুকু মিলেই আত্মিক স্তর, সচেতনতার স্তর। আর এখানে জন্ম-মৃত্যু একটা মিডিয়া মাত্র। যেমন কচ্ছপ আর তার কঠিন ক্যারাপেস। ক্যারাপেস খোলাই থাক আর বন্ধই থাক, কচ্ছপ আর এর প্রাণ এখানে প্রতিমুহূর্তে রয়েছে। তেমনিই সচেতনতা, জন্ম, মৃত্যু এগুলো চিহ্নিতকরণের উপায় মাত্র। আসলে দেহ থাক বা না থাক, দেহজ প্রাণ আগে ও পরে অস্তিত্বশীল। না হলে মৃত্যুকে ধ্রুবক মানতে হয়, আর মৃত্যুই একমাত্র সত্য হলে জীবনচক্রই তৈরি হবে না, সব কেবল নিঃশেষ হতে থাকবে। অথচ বাস্তবে তা হছে না। শক্তি তাকে আত্মাই বলি, প্রাণই বলি আর যা-ই বলি, জন্মের আগে থেকে মৃত্যুর পর অবধি তা অস্তিত্বশীল। সে দেহ খোলাই থাক বা বন্ধই থাক।
পুঁজিবাদের উন্নয়নের লেলিহান আগুনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এটি জীবন-প্রকৃতি রক্ষার কথা বলে
ল্যানজার ধারণাগুলো বিবর্তনবাদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। আর তাই প্রাণ-প্রকৃতি তথা পরিবেশ রক্ষাটা এত গুরুত্বপূর্ণ। বায়োসেন্ট্র্রিজম মূলত এথিকস ও মোরালিটির জায়গা থেকে পরিবেশ নিধনের সমালোচনা করে। বায়োডাইভার্সিটি, অ্যানিমেল রাইটস, এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশনের পক্ষে কথা বলে। সেই হিসেবে এটির অবস্থান অ্যান্টি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ও অ্যান্টি ক্যাপিটালিস্ট। বায়োসেন্ট্র্রিজম নিয়ে আলাপ করতে চাইলে আরো কয়েকজন দার্র্শনিক অ্যাক্টিভিস্টের নাম উঠে আসবে, তাদের মধ্যে আলবার্ট শ্বোয়াইৎজার, পিটার সিঙ্গার ও পলটেইলর অন্যতম। যদিও তাদের ধারণাগুলো আমরা বুদ্ধধর্মে ও উপনিষদে দেখতে পাই। আলবার্ট শ্বোয়াইৎজার নিজের জীবন বাজি রেখে তার দর্শনের প্রতিফলন করে গেছেন তার জীবনে। অসম্ভব সম্ভাবনাময় সংগীত ক্যারিয়ার ছেড়ে তিনি ডাক্তারি পড়া শুরু করেন। ডাক্তারি শেষ করে তিনি পাশ্চাত্য ধারার ভোগবাদী জীবন পরিত্যাগ করে রওনা দেন আফ্রিকার গহিন দুর্গম এলাকায়। তিনি সেখানে দিনে দিনে গড়ে তোলেন চিকিৎসাকেন্দ্র। একই সঙ্গে সক্রিয় থাকেন লেখালেখিতেও। নোবেল প্রাইজসহ অনেকগুলো পুরস্কার পান সেসবও তিনি বিলিয়ে দেন তার চিকিৎসাকেন্দ্রে। তার নীতিবোধের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। কেবল মনুষ্য সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার মতে, সগোত্র প্রাণীর প্রতি যেমন সংবেদনশীল থাকা বাঞ্ছনীয়, ঠিক তেমনি মনুষ্যতের প্রাণীর প্রতিও সমভাবে সংবেদনশীল থাকা প্রত্যাশিত। তিনি মনে করেন সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উত্তরোত্তর অভূতপূর্ব সাফল্য মানুষকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ক্রমেই সরিয়ে এনেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সহাবস্থান করার পরিবর্তে প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করা অগ্রাধিকার পেয়ে আসছে। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত মূল সত্যটি হলো প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা, প্রকৃতিদত্ত লক্ষণ- রেখা মেনে চলা। সগোত্র প্রাণীই কেবল আত্মার আত্মীয় নয়। পশু-পাখি-গাছপালা-গুল্ম সবই আত্মার আত্মীয়। এই বোধ মানুষের উত্তরণের পথ প্রশস্ত করে এবং সামাজিক নীতিবোধের ব্যাপ্তি ঘটায়। শ্বোয়াইৎজার বলেন,যুগ ধর্ম বলে একটা কথা আছে। একেকটা যুগ আছে যখন মানুষ হৃষ্টচিত্তে এবং অবলীলায় অপরের জন্য ত্যাগ করে এবং হাসিমুখে ক্লেশ সহ্য করে। ইতিহাসে এর অনেক উদাহরণ আছে। আবার অনেক সময় যুগ-ধর্ম এমন যে মানুষ স্বার্থপরতাকে প্রাধান্য দেয়। যেমন, ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীতে খুুনোখুনি-হানাহানিতে মানুষকে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়।
প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সহাবস্থান করার পরিবর্তে প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করা অগ্রাধিকার পেয়ে আসছে
ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে যেসব যুদ্ধ হতো, তাতে যুযুধান সামরিক বাহিনীর মধ্যেই হানাহানি সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে, শত্রুশিবিরকে পর্যুদস্ত করতে আবালবৃদ্ধবনিতা কেউ-ই বাদ যায় না। তিনি বলেন, সব প্রাণের প্রতি দরদী হওয়ার ভাব আয়ত্ত করতে পারলে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে, শান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। তর্র্ক বা যুক্তি দিয়ে এই ভাব আয়ত্ত করা যায় না। গভীর মননের দ্বারা এই ভাব উপলব্ধি করতে হয়। প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে তিনি অন দ্য এজ অব প্রাইমিভাল ফরেস্ট শীর্ষক গ্রন্থটি লেখেন। এই বইয়ে তিনি উপনিবেশ স্থাপনের অনৈতিক দিক এবং আনুষঙ্গিক কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। উন্নত এবং সমৃৃদ্ধ পাশ্চাত্য দেশগুলোর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার জন্য আদিম অরণ্যবাসীদের মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়ে বহু মূল্যবান বনজ ও খনিজ সম্পদ লুণ্ঠন করা হলো উপনিবেশ স্থাপন করার একমাত্র লক্ষ্য। প্রতিদানে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার, তাদের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার কোনো প্রচেষ্টাই তাদের ছিল না। অন্যদিকে পিটার সিঙ্গার পরিচিতি পান তার প্রভাবশালী বই অ্যানিমেল লিবারেশনের মাধ্যমে। যেখানে তিনি প্রাণীদের ওপর মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। মানব শিশুর সঙ্গে মানুষ যে আচরণ করে ঠিক একই মানবিক আচরণ পশুদের সঙ্গেও করা উচিত বলে মনে করেন পিটার সিঙ্গার। তিনি বলেন, যদি আপনি কোনো ঘোড়ার পিঠে চড় মারেন, সেটি ঘোড়ার জন্য কোনো ব্যথার কারণ হবে না, হয়তো কারণ ঘোড়ার চামড়া বেশ পুরু কিন্তু আপনি সেই চড় যদি কোনো মানবশিশুকে মারেন? সেটা ভয়াবহ হতে পারে। ঘোড়ার পিঠে চড় মারার সময় আপনি মনে করেন কোনো মানবশিশুর শরীরে আঘাত করছেন। তাহলে নিজেকে সংযত করা সহজ হবে। অবশ্য দুটো কাজের কোনোটাই করা উচিত নয়। সিঙ্গারের প্রস্তাবনা আমাদের সবারই নিরামিষাশী হওয়া উচিত, শুধু এই কারণে যে আমরা কোনো প্রাণী না খেয়েই খুব সহজে ভালোভাবে বাঁচতে পারি। খামারে চাষ করা মুরগিদের রাখা হয় খুবই সংকীর্ণ খাঁচায়, কিছু শূকরকে এমনভাবে আটকে রাখা হয় যে তারা এমনকি পাশ ফিরতেও পারে না, আর গবাদি পশুদের জবাই করার পদ্ধতি খুবই যন্ত্রণাময় তাদের জন্য। সিঙ্গার যুক্তি দিয়েছিলেন অবশ্যই এটি নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এমন খামার ব্যবস্থা জারি রাখা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এমনকি মানবিক খামার ব্যবস্থাও অপ্রয়োজনীয় কারণ আমরা মাংস ছাড়া বেশ ভালোভাবেই বাঁচতে পারি। খামারে চাষ করা প্রাণীরাই শুধু মানুষের দ্বারা নির্যাতিত না, বিজ্ঞানীরাও প্রাণীদের ব্যবহার করেন তাদের অমানবিক গবেষণায়। শুধু ইঁদুর কিংবা গিনিপিগ নয়, বিড়াল, কুকুর, বানর, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদিকেও তাদের পরীক্ষাগারে দেখি, তাদের অনেককেই নানা ধরনের যন্ত্রণা আর নির্যাতনের শিকার হতে হয়, যখন তাদের শরীরে নানা ওষুধ কিংবা বৈদ্যুতিক শক দেয়া হয়।
বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প হওয়ার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ‘বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড’ ও ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ‘ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার করপোরেশন’ (এনটিপিসি), ও জাপানি বহুজাতিক জাইকা যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একটা বাগেরহাট জেলা তথা সুন্দরবনের রামপাল এলাকায়। এটা করছে ভারতের এনটিপিসি কোম্পানি। আর কয়েকটা গুচ্ছ প্রকল্প হচ্ছে কক্সবাজার জেলার মহেশখালীর মাতারবাড়ী ইউনিয়নে, বাঁশখালীসহ উপকূলীয় এলাকায়। এগুলো করছে জাপানি বহুজাতিক কোম্পানি জাইকাসহ চীন, মালয়েশিয়া, ভারতসহ আরো নানা দেশ। প্রথমে একটা প্রকল্পের কথা বলা হলেও এখন নাকি চৌদ্দ-পনেরটার মতো কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প হতে যাচ্ছে সেখানে। মাতারবাড়ীতে জমি অধিগ্রহণও হয়ে গেছে, এই অধিগ্রহণের এরিয়া ক্রমেই বাড়ছে। মহেশখালীর মানুষ এমন আশঙ্কাও করছে যে এই প্রাকৃতিক দ্বীপে আদৌ মানুষ বসবাস করতে পারবে কিনা। পর্যটন নগরী কক্সবাজারেরইবা ভবিষ্যৎ কী? যেহেতু সবই প্রায় লবণ ও ধান চাষের জমি, সেহেতু অজস্র মানুষ এরই মধ্যে বেকার হয়ে গেছে। জমির মালিক আর কয়জন? সবাই তো শ্রমিক। লবণ আর ধানের বদলে যে নতুন ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে, সেখানে দরকার প্রশিক্ষিত শ্রমিক, সেখানে এই চাষাভুষাদের কী কাজ? ফলে তারা আরো তিমিরেই চলে গেল। এরই মধ্যে সেখানে বেকারত্ব মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। আপাতচোখে দেশে কোনো একটা প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে মনে হয় দেশের উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু এই উন্নয়নের পেছনের লাভ-লোকসান, লোভ ও লুটপাটও খতিয়ে দেখা উচিত। বিশেষ করে যেখানে কয়লা বিদ্যুৎ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় গত ১০০ বছর ধরে উন্নত দেশগুলোতে এটা প্রায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। রাশিয়াতে লেনিনের শাসনামলেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এই ক্ষতিকর বিদ্যুৎ প্রকল্প। এই কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প মারাত্মক পরিবেশ দূষণ ও নানারকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটায় বলে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোয়ও জনবসতি অথবা সংরক্ষিত বনভূমির কমপক্ষে ১৫-২০ কিলোমিটারের মধ্যে অনুমোদন করে না। অথচ রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি জনবসতি থেকে মাত্র ৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর মহেশখালীরগুলো তো জনবসতির প্রায় ১কিলোমিটারের মধ্যেই। এমনকি যেই ভারতীয় কোম্পানি রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র করছে, সেই এনটিপিসি ভারতের মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের আবেদন করলে ১৯৭২ সালের ভারত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের দোহাই দিয়ে তা বাতিল করে দেয়। এছাড়াও ২০১০ সালের আগস্টে ভারত সরকারের তৈরি করা ইআইএ (এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট) গাইডলাইন অনুসারে ২৫ কিলোমিটারের ভেতর কোনো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। সেখানে ভারতীয়সহ বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে এই কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পে কেন বিনিয়োগ করছে আর বাংলাদেশের অথরিটি তা কেন করতে দিচ্ছে তা ভেবে দেখা জরুরি।
কয়লা বিদ্যুৎ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় গত ১০০ বছর ধরে উন্নত দেশগুলোতে এটা প্রায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে
একেকটা কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রতিদিন যা করা হয়, তার হদিস নিলেই মিলে যাবে হিসাব। প্রতিদিন টনটন বিষাক্ত সালফার আর নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ফেলা হবে পাশের নদীতে, যেজন্য কয়লা বিদ্যুতের স্থান শনাক্তের সময় নদী থাকাটা জরুরি। টনটন বিষাক্ত সালফারযুক্ত ছাই দূষিত করবে ভূ-উপরিস্থিত পরিবেশ। বাতাসে এই ছাই মিশে গাছপালা ও প্রাণীদের জীবনযাপনকে করে তুলবে বিপন্ন। বিদ্যুৎকেন্দ্রের চিমনি থেকে ১২৫ ডিগ্রি তাপমাত্রার ধোঁয়া নির্গমন হবে। ফলে এলাকার তাপমাত্রা বেড়ে যাবে স্বাভাবিকের তুলনায় বহুগুণ। লাখ লাখ টন আমদানীকৃত কয়লা জাহাজে, ট্রলারে বহন করা হবে নদী বা স্থলপথে। কয়লার ভাঙা টুকরো, জাহাজের তেল এসব এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিনষ্ট করবে। প্রতিদিন শত শত গভীর নলকূপের মাধ্যমে শত শত কিউসেক ভূগর্ভস্থ মিঠাপানি উত্তোলন করা হবে। এতে এ এলাকার ভূগর্ভস্থ মিঠাপানির আধার নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুন্দরবনের কাছে যেমন রয়েছে পশুর নদী, তেমনি মাতারবাড়ীর পাশের কুহেলিকা খাল যুক্ত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। অতিমাত্রায় সালফারের কারণে এসব নদীতে নিঃশেষ হবে মৎস্যসম্পদ। বিদ্যুৎকেন্দ্রের আশপাশের জমিতে উৎপাদিত ফসল, শাকসবজি খেলে মানবদেহে ছড়িয়ে পড়বে অ্যাজমা, ফুসফুসবাহিত নানা রোগ, এমনকি মহামারী আকারে দেখা দিতে পারে ক্যান্সার।
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট নিরসনের নামে দেশি-বিদেশি লুটেরা গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে অথরিটি দেশের জন্য সর্বনাশা পথ গ্রহণ করছে
রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গেলে প্রতিদিন প্রায় ১৪২ টন বিষাক্ত সালফার ও ৮৫ টন নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ফেলা হবে পশুর নদীতে। এই নদীটি সুন্দরবনের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ফলে নদীটি ধ্বংস হয়ে যাবে। বছরে ৫০ লাখ টন আমদানীকৃত কয়লা জাহাজে বহন হবে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নদীপথে। কয়লার ভাঙা টুকরো, জাহাজের তেল সুন্দরবনের ইকো সিস্টেম সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের ভয়ভীতি দেখিয়ে প্রয়োজনের দ্বিগুণের চেয়ে বেশি অর্থাৎ ১৮৪৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিদিন ৭২টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে ১৪৪ কিউসেক ভূগর্ভস্থ মিঠাপানি উত্তোলন করা হবে তাপবিদ্যুতের জন্য। ভূ-গর্ভস্থ মিঠাপানির আধার নিঃশেষ হবে অতি দ্রুত। দেবে যাবে ঘরবাড়িসহ আশপাশের স্থাপনা। ৮ হাজার পরিবার তার জমি থেকে উচ্ছেদ হবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে। করমুক্ত সুবিধাসহ ভারত মাত্র ১৫% বিনিয়োগ করে বিদ্যুতের মালিকানা পাবে ৫০%। বিদেশী ৭০ ভাগ ঋণের সুদসহ ঋণ পরিশোধের দায় থাকবে বাংলাদেশের। দেশীয় কোম্পানির চেয়ে এই প্রকল্পের বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮ টাকা ৮০ পয়সা। রামপাল প্রকল্পে লাভ হবে ভারতীয় পক্ষের আর তার সঙ্গে দেশি কমিশনভোগীদের। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষতি সর্বব্যাপী। সুন্দরবন ধ্বংস হওয়া ছাড়াও প্রত্যক্ষ আর্থিক ক্ষতি হবে বাংলাদেশের। তুলনামূলকভাবে বিদ্যুতের অতিরিক্ত দামের জন্য আর্থিক ক্ষতি হবে ১লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা। এর সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সম্ভাব্য ক্ষতি যোগ করলে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৫ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া সুন্দরবন ধ্বংস, ভয়াবহ পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে খুলনা শহরসহ এই বিভাগের মানুষ ও বন্যপ্রাণীর জীবন-জীবিকা খাদ্য ইত্যাদিও ভয়াবহ ক্ষতি টাকার অংকে নিরূপণ করা অসম্ভব।
সুন্দরবনের কারণে রামপালের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রূপসী মিডিয়ায় প্রচার পেলেও মহেশখালী বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে তেমন কোনো কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না। বলতে গেলে নীরবেই সব হয়ে গেল মাতারবাড়ীতে। স্থানীয় সরকারদলীয় নেতাদের উন্নয়নের পোস্টার-ফেস্টুনে ঢেকে গেছে সেখানে সব প্রতিবাদ। মিডিয়ার নজরেও পড়েনি, আবার যারা এটা নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করছেন, তারাও জানেন বলে মনে হয় না। মহেশখালীর কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে স্থাপিত হবে প্রাথমিকভাবে। যে স্থানে এই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার কথা, তাতে লবণ ও চিংড়ি চাষ করে স্থানীয় দুই ইউনিয়নের দেড়লাখ মানুষ জীবন নির্বাহ করে। শুধু যে তারা জীবিকাহীন হবে তা-ই না, কয়লা বিদ্যুতের প্রভাবে এই দেড়লাখ মানুষ পরিবেশ উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। শুধুকি এরাই! ধীরে ধীরে পুরো মহেশখালীটাই মরুভূমি হওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশের একমাত্র কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র বড়পুকুরিয়ার মাত্র ২৫০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট। বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হওয়ার পর থেকেই নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে সেখানে। স্থানীয়দের অভিযোগের শেষ নেই। তারা বারবার এসব সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রটি ঘেরাও করছে। প্রধানতম সমস্যা হচ্ছে পানি। বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রয়োজনে ভূ-গর্ভস্থ পানি টেনে নেয়ার কারণে এলাকাবাসী চাষাবাদ ও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের পানি পাচ্ছেন না। গ্রামবাসীর অভিযোগ, বিদ্যুৎকেন্দ্র সংলগ্ন ১৪টি পাম্পের কারণে দুধিপুর, তেলিপাড়া, ইছবপুরসহ আশপাশের গ্রামে পানির তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে ছাই। মাত্র ২৫০ মেগাওয়াটের এই কেন্দ্রটি চালু রাখতে প্রতিদিন কয়লা জ্বালাতে হয় ২হাজার ৪০০টন। এতে ছাই হয় প্রতিদিন ৩০০ মেট্রিকটন। পুরো এলাকা ছেয়ে যাচ্ছে। একাধিক পুকুরে প্রতিদিন এই ছাই জমা হচ্ছে। এরই মধ্যে এই পুকুরগুলোর চারভাগের তিনভাগের বেশি ছাইয়ে ভরাট হয়ে গেছে। ফলে পুকুরের পানিও শুকিয়ে গেছে। শুধু তা-ই না, এই ছাইমিশ্রিত পানি চুইয়ে মাটির নিচে ও আশপাশের জলাভূমিতে গড়িয়ে যাচ্ছে। বড়পুকুরিয়া কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের আশপাশে গেলেই দেখা যায় কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের নালা বেয়ে কয়লা ধোয়া কালো পানির-স্রোতে মিশে যাচ্ছে আশপাশের কৃষিজমিতে। ফলে আশপাশের কৃষিজমিগুলোর রঙ এখন নিকষকালো। এই যদি বড়পুকুরিয়ার মাত্র ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিবেশ দূষণের আংশিক চিত্র হয়, তাহলে ১৩২০ মেগাওয়াটের রামপাল ও ১২০০ মেগাওয়াটের মহেশখালী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণে পরিবেশ, জনবসতি ও কৃষিজমির কী হাল হবে তা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট নিরসনের নামে দেশি-বিদেশি লুটেরা গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে অথরিটি দেশের জন্য সর্বনাশা পথ গ্রহণ করছে। সুন্দরবন-কৃষিজমি শহর ধ্বংসকারী রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত, মহেশখালীর মতো দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত, ফুলবাড়ী-বড়পুকুরিয়ার উন্মুক্ত খনির চক্রান্তঅব্যাহত রাখা, বঙ্গোপসাগরের গ্যাস ব্লক একতরফা সুবিধা দিয়ে বিদেশি কোম্পানির কাছে ইজারা দেয়া, কুইক রেন্টালের নামে ১৪ থেকে ১৭ টাকা কিংবা তারও বেশি দরে বিদ্যুৎ ক্রয়, কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি না করে, প্রয়োজনীয় সমীক্ষা না করে বিদেশি কোম্পানিনির্ভর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্যোগ ইত্যাদি সবকিছু জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে মুনাফা ও লুটপাটের আয়োজনের অংশমাত্র। এতে করে যে ব্যাপক প্রাণ-প্রকৃতির ক্ষতি হবে তা কোনো আর্থিক পরিমাপে মাপা প্রায় অসম্ভব। জীবনানন্দের কবিতার প্যারোডি করে বলা যায়, অদ্ভুত অমানবিক পুঁজির আঁধার এসেছে পৃথিবীতে আজ।