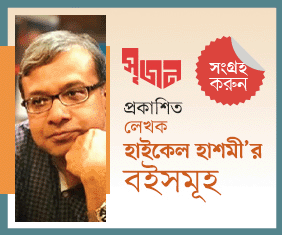প্রথম পর্বঃ কাসুভি’র সৌধ (৫)
১৮৭৫ সালে অভিযাত্রী স্ট্যানলি যখন আফ্রিকা মহাদেশকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে অতিক্রম করছিলেন তখন আটত্রিশ বছর বয়সী মিউতসাকে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে দেখেন। তার প্রতিপক্ষ ছিল ওয়েভুমা গোত্রের মানুষ। উভয়পক্ষ ভিক্টোরিয়া হ্রদের উত্তর উপকূলে মুখোমুখি হয়েছিল। মিউতসার সেনাবাহিনী ছিল বিশাল। স্ট্যানলির উপস্থিত হিসাব মতে (এবং অতিরঞ্জিতও বটে) সম্মুখ সমরে লিপ্ত ছিল প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের মত সৈন্য। এই সংখ্যার বাইরে যোদ্ধা নয় তবে অনুসারী এবং নারী (মিউতসা তার হেরেমসহ ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেন) ছিল আরও প্রায় এক লক্ষ। ফলে মিউতসার যুদ্ধযাত্রীর সংখ্য ছিল প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার।
মিউতসার বাহিনীতে সেই সময় বন্দুকধারী সৈন্য ছিল। কিন্তু সেই বন্দুকধারী সৈন্যরা তাকে উল্লেখ করার মত কোন সাফল্য দেখাতে পারছিল না। প্রতিপক্ষ ওয়েভুমা গোত্রের লোকজন যাদের বর্শাই ছিল একমাত্র অস্ত্র তারা জানত যে, মিউতসার সৈন্যদলে বন্দুকধারী সৈন্য আছে কিন্তু সেই সৈন্যদের মোকাবেলায় তারা ভিত ছিল না। কারণ পানিতে যুদ্ধ করার কৌশল বিবেচনায় ওয়েভুমারা অগ্রগ্রামী ছিল। অন্যদিকে মিউতসার সৈন্যদের দক্ষতা ছিল স্থলপথের যুদ্ধে। ফলে সেই যুদ্ধে ওয়েভুমা গোত্রের লোকেরা বেশিরভাগ সময় সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। ভিক্টোরিয়া হ্রদের দুইপাশের পাহাড়ে লোকজন সমবেত হয়েছিল সেই যুদ্ধ দেখার জন্য। স্ট্যানলির লেখা বইয়ে যেসব চিত্র অংকিত আছে তার অনেকগুলো সেই সময় স্ট্যানলি যেসব ছবি তুলেছেন তার ভিত্তিতে আঁকা। সেই সব চিত্রে দুইপক্ষের যুদ্ধ-নৌকার কাঠামো এবং যুদ্ধরত সৈন্যদের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া না-গেলেও দুই পক্ষের সাজানো নৌকা আর সুশৃংখল সেনাবাহিনীর বিষয়ে বেশ স্বচ্ছ একটা ধারনা পাওয়া যায়। তবে দর্শকদের জন্য সেই যুদ্ধ তেমন কোন চিত্তাকর্ষক ছিল না। তারা বেশ আয়েসী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। খন্ড খন্ড যুদ্ধ সমাপ্ত করার পর-পরই সৈন্যরা অবসরে চলে যেত। লম্বা বিশ্রাম শেষে আবার কখনও যুদ্ধে লিপ্ত হতো। এমনকি স্ট্যানলি স্বপ্রণোদিত হয়ে মিউতসাকে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে আবিষ্কার করেন যে মিউতসা ইতোমধ্যে যুদ্ধের বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন এবং যুদ্ধের চেয়ে ধর্ম-বিষয়ক আলোচনাতেই তিনি বেশি আগ্রহী।
মিউতসা সেই যুদ্ধে তার প্রতিপক্ষকে ভীত করতে নানারকম কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ভীতিকর শব্দ তৈরি করা। মিউতসার ছিল পঞ্চাশ জন করে ঢোল-বাদক, অর্ধ-শত বংশীবাদক এবং একশ’র বেশি যাদুকর। সেই সব যাদুকরদের মধ্যে নারী এবং পুরুষ উভয় প্রকারই ছিল। সেই সব যাদুকররা ছিল বিশেষভাবে বাছাইকৃত এবং তাদের খুব আকর্ষণীয় কাপড় পরানো হয়েছিল (নিশ্চিতভাবেই ওয়েভুমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য)। তারা নানারকম যাদু কৌশল দিয়ে শয়তানের কুদৃষ্টি থেকে মিউতসাকে রক্ষার পাশাপাশি ওয়েভুমাদের ডুবিয়ে মারতে সচেষ্ট ছিল। কোন যাদু-কৌশল প্রয়োগের পূর্বে তারা সেই সব কৌশল মিউতসার সামনে প্রদর্শন করত। যদিও মিউতসা ইতোমধ্যে আধা-মুসলমান এবং আধা-খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীতে পরিনত হয়েছে তারপরও মৃত টিকটিকি, মানুষের নখের মত আফ্রিকান যাদু বিশ্বাসের মূল্যবান উপাদানসমূহকে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছিলেন।
নিজেকে নানারকম যাদু-কৌশল দ্বারা নিরাপদে রেখে নিজের সেনাপতিদের নানারকম ভীতি প্রদর্শন করে যাচ্ছিলেন মিউতসা। তিনি তাদেরকে কাপুরুষ হিসেবে অভিহিত করে এতদিন যে সম্মান এবং আশীর্বাদ দিয়েছেন তা ছিনিয়ে নেয়ার হুমকী দিচ্ছিলেন। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, তারা কেউ আজন্ম সেনাপতি নন। সামান্য চাষীর জীবন ছিল তাদের। তার কল্যানেই তারা এমন সম্মানিত অবস্থানে উঠে এসেছেন। যুদ্ধে সফল না হলে তাদের যে আবার চাষীর জীবনেও ফিরে যেতে হতে পারে তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। কাউকে কাউকে আগুনে পুড়িয়ে মারারও হুমকী দিচ্ছিলেন (মিউতসা খুব অল্পের জন্য আগুনে পুড়ে মরা থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন বলে সম্ভবত তার মনে সেই স্মৃতি সর্বদাই খেলা করতো)। তার মুখ্য মন্ত্রী তার শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রমান স্বরূপ নিজের দেহ মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে বলেছিল, ‘আপনি যদি কাল আমার নৌকাকে পশ্চাদপসরন করতে দেখেন তবে অবশ্যই আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবেন অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলবেন।’
পরবর্তী সময় যখন স্ট্যানলি মিউতসার মুখোমুখি হয় তখন তিনি তাকে খুব পরিতুষ্ট দেখতে পান। তার সৈন্যরা ইতোমধ্যে ওয়েভুমাদের একজন বর্ষীয়ান গোত্রপতিকে ধরে আনতে সক্ষম হয়েছে। এবং মিউতসা ওয়েভুমাদের উচিৎ শিক্ষা দেয়ার জন্য সেই গোত্রপতিকে পুড়িয়ে মারার জন্য মনস্থিরও করেছেন। স্ট্যানলি দুই পক্ষের সাথে কথা বলে সেই সময় মধ্যস্থতাকারির ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছিলেন।

ঐ ঘটনাটি ছিল ১৮৭৫ সালের এবং এর নয় বছরের মধ্যে মিউতসা মৃত্যুবরণ করেন। এবং পিতা সুন্নাহ’র সমাধির আদলে তৈরি সৌধে সমাহিত হয়ে যান। মিউতসা প্রকৃতই তার পিতার প্রতিরূপ ছিলেন কারণ তার সামনে অনুসরনীয় হয়ে উঠতে পারে এমন কোন নেতা উগান্ডায় জন্ম নেয়নি।
কিন্তু ইদি আমিন এবং ওবেতো’র সামনে ছিল এক ধরনের পরাম্পরা। তারা পেয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন। ব্রিটিশ শাসনকালে আইনের শাসন ছিল। এবং সময়টা ছিল যদ্ধবিহীন। ফলে তারা তাদেরকে অনুসরন করতে পারত। কিন্তু তারা তা করেনি। বরং ব্রিটিশ শাসনের সময়টাকে এখন স্বাভাবিক ধারনার বাইরে একটি ভিন্ন নাটিকা বলে মনে হয়। আফ্রিকানরা নিজস্ব ইতিহাসের বাইরে গিয়ে বেঁচে থাকবে— তা হতে পারে কি? সম্ভবত লিখিত দলিলাদির অভাব থাকলেও মানুষের মুখে মুখে ফেরা গল্পগুলো তাদের মধ্যে মিথের জন্ম দিয়েছিল।
মেকেরে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুসান নামে এক মেধাবী কবি এবং সাহিত্যের শিক্ষকের সাথে পরিচয় হয় আমার। চল্লিশেরও কম বয়সী, আকর্ষণীয় এবং চমৎকার কন্ঠস্বরের অধিকারি ছিলেন সেই শিক্ষক। তার পারিবারিক ইতিহাসের ভাঁজে-ভাঁজে ছিল বেদনা-গাঁথা। তিনি উগান্ডার ঔপনিবেশিক শাসনের পরবর্তী সময়ে পিতা এবং পিতামহ দু’জনকেই হারান। তারা কাম্পালার উত্তরে লুইরো অঞ্চলে বাস করত। স্থানটি ছিল উর্বর, জনবহুল। উগান্ডার সবচেয়ে বড় গৃহযদ্ধটি বা গৃহযুদ্ধগুলো এখানেই সংঘটিত হয়েছে।
সুসানের পিতামহ ছিল খামারী। সে তার খামারের গরুগুলোকে পরম নিষ্ঠার সাথে ভালবাসতেন। তিনি প্রত্যেকটি গরুকে নির্দিষ্ট নামে চিনতেন এবং প্রত্যেকটি গরুর মানসিকতা, তাদের গায়ের রং, আকৃতি এমনকি তাদের শিংয়ের গঠন বিষয়েও পরিষ্কার ধারনা রাখতেন। ওবেটো’র দ্বিতীয় শাসনের সময় যে যুদ্ধ শুরু হয় সেই সময় খামার ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না। ইদি আমিনকে হটিয়ে দেয়ার পর সৈন্যরা তাদের দুশ্চরিত্র আর ধূর্ত মানসিকতা নিয়ে একের পর এক বিরোধীপক্ষ খুঁজে ফিরছিল। পলাতক জীবন কাটানোর সময় সুসানের পিতামহ বার বারই তার খামারে ফেলে আসা গরুগুলোর কথা ভাবতেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, গবাদি পশুগুলো নিজের মত করে যত্ন নিতে সক্ষম নয় ফলে তার পালিয়ে থাকা মানে গরুগুলোর দুর্দশাগ্রস্থ হওয়া। এই চিন্তা থেকে তিনি ঠিক করেছিলেন তিনি অন্তত একবার খামারে গিয়ে গরুগুলোকে দেখে আসবেন। কিন্তু তিনি গরুগুলোকে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করেন সৈন্যরা তার জন্য অপেক্ষারত। তারা কুড়ালের আঘাতে তার শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করে উগান্ডার অনেকগুলো উইঢিবির একটিতে ছড়িয়ে দেয়। তার শরীরের হাড়-গোড় যুদ্ধ শেষ হলে খুঁজে বের করেছিল পরিবার এবং যথাযথ নিয়মে দাফন করতে পেরেছিল। কিন্তু সুসানের পিতার ভাগ্য ছিল আরও খারাপ।
ইদি আমিনের শাসনকালে তাকে তুলে নেয়া হয়েছিল এবং পরে তাকে আর কখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেউ জানে না কোথায়, কিভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এই নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এক বিশেষ ধরনের বেদনার জন্ম দিয়েছে সুসানদের পরিবারকে। তারা প্রতিনিয়ত নানারকম আশংঙ্কা কথা ভাবে এবং বেদনার্ত হয়। এই বেদনা এমন এক বেদনা যে সুসানের মা কোনদিন তার বাবার নামটি উচ্চারণও করেন না।
সুসানের এই গল্প কোন ব্যাতিক্রমী গল্প নয়। এই গল্প খুব সাধারন একটি গল্প বিশেষত যারা লিউরি অঞ্চলে বসবাস করত তাদের জন্য। ওবেটো’র সৈন্যরা লুটপাট করে লিউরিকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল। “তারা ধর্ষন আর খুনের এমন এক রাজত্ব কায়েম করেছিল যে, তাদের সেই ধ্বংসলীলা এখনও বোঝা যায়। লিউরি এখন একটি জনমানবশূণ্য শহর। একরের পর একর জমি উন্মুক্ত পড়ে আছে। দেখলে মনে হয় কোন ভূতের শহর।”
সুুসানের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, ভীতির মধ্যে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা কেমন?
‘আমি তখন অনেক ছোট। আমার বয়স ছিল পাঁচ এবং আমার শুধু মনে পড়ে কোথাও তখন চিনি পাওয়া যেত না। যখন ১৯৭৯ সালে ইদি আমিনকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া হল তখন আমার বয়স ছিল আট। কিন্তু সেই সময়েরও তেমন কোন স্মৃতি নেই আমার। তবে আমার বার বছর বয়সে যখন ওবোটো’কে সরিয়ে দেয়া হলো তখনকার স্মৃতি বেশ পরিষ্কার। চারপাশের ঘটনাবলীর বিষয়ে আমি বেশ সচেতন তখন। নিজের পরিবার এবং প্রতিবেশিদের নিরাপত্তাহীনতা উপলব্ধি করতে পারতাম। অন্য সময় আপনি প্রশ্ন করলে উত্তর পাবেন কিন্তু সেই সময় কোন বিষয়ে উত্তর পাওয়া কঠিন ছিল কারণ যারা উত্তর দিবে তারাও তখন অনিরাপদ। যে সরকারের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় থাকার কথা তারা নিজেরাই তখন দানবে রূপ নিয়েছে। মনে হত শ্রষ্টা তাদের দায়মুক্তি দিয়ে ঐসব অবিচার করার সুযোগ প্রদান করে দিয়েছে। আমি এখনও জানি না কেনই-বা তাদের শাসনক্ষমতা দেয়া হয়েছিল এবং কেন-ইবা তারা ঐ অত্যাচারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।’
উগান্ডার মানুষেরা কি তাদের পরিনতির জন্য পূর্বপুরুষদের দায়ী করে? উত্তরে সুসান বলেছিল, ‘আমি স্মরণ করতে পারি যে মানুষ শ্রষ্টার উপর আস্থা রাখতে শুরু করেছিল একটি সুন্দর ভবিষ্যতের আশায়। যদিও তারা নিজেদের ধর্ম নিয়েও হতাশ ছিল। হতাশা তাদেরকে অন্য ধর্মের দিকে নিয়ে যায়। তার মানে এই না যে শত্রুর সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হবে। আমি শ্রষ্টাকে হিতৈষী জেনে বড় হয়েছি। শয়তানের নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করা শ্রষ্টার দায়িত্ব বলে জেনেছি। আমার অনেক বন্ধুই মনে করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে কিংবা পুরাতন ধর্মকে অস্বীকার করে আমরা পূর্বপুরুষদের অসন্তুট করেছি। এবং এই কর্মের প্রতিফল আমরা ভোগ করছি। আমার কথাই ধরুন, আমি খ্রিষ্টান ধর্ম নিয়ে বড় হয়েছি। কিন্তু আমি পুরনো বা ঐতিহ্যবাহী ধর্মের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করি না বা অসম্মানও করি না। আমি ঔপনিবেশিক সময়ের পরে জন্ম নিয়েছি এবং সেই সময়টিকে আমি মানসিক আঘাত হিসেবে বিবেচনা করি।’
এখানে আমরা আরেকটি নতুন সংকটের সন্ধান পাই। যে সংকটের শুরু ইদি আমিন বা ওবেটো’র শাসনের পূর্বে জন্ম নিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ব্রিটিশ প্রটেক্টরেট আইনের মাধ্যমে সেই সংকটের শুরু হলেও, সেই সংকট মূলত শুরু হয়েছে যখন মিউতসা বৃটিশদেরকে তার দেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সেই সময় থেকে।
সুসানের মতে, ‘এটা এমন একটা পরিস্থিতি যে আমি অবগত আমার অস্তিত্ব অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল। আমি নানা অভিজ্ঞতায় এমন ভাবে দ্রবীভূত একজন মানুষ যে, আমি পরিপূর্ণ সত্বায় বিকশিত হতে না-পেরে অনেকগুলো ছোট-ছোট সত্বায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি।’
আমার বাবা তার এক প্রিয় খালার নামানুসারে দিয়েছিলেন। সুতরাং আমার নামটির সাথে তিনি মানসিকভাবে জড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমি এখন জানি এটি ইহুদি-খ্রিষ্টান ধাঁচের নাম। আমি আবার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমার নামের সাথে আমার গোত্রের নাম যুক্ত করি। আমাদের গোত্রের নাম— নালুগুয়া। যার মানে ‘ভেড়া গোত্রের অন্তর্গত’। যা আমি আমার পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করি। সুসান নালুগুয়া হলেও চলতো কিন্তু আমাকে এই নামের সাথে আমার বাবার নামও জুড়ে দেয়া হয়েছে। আমার বাবার নাম ছিল কিগুলি। স্কুলে আমার নাম অন্তর্ভূক্তির সময় পিতার নামটি জুড়ে দেয়া হয়েছে
যেমন সুসান তার নিজের নাম নিয়েও চিন্তিত।
‘আমার নামের প্রথম অংশ সুসান। যা আমার বাবা তার এক প্রিয় খালার নামানুসারে দিয়েছিলেন। সুতরাং আমার নামটির সাথে তিনি মানসিকভাবে জড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমি এখন জানি এটি ইহুদি-খ্রিষ্টান ধাঁচের নাম। আমি আবার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমার নামের সাথে আমার গোত্রের নাম যুক্ত করি। আমাদের গোত্রের নাম— নালুগুয়া। যার মানে ‘ভেড়া গোত্রের অন্তর্গত’। যা আমি আমার পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করি। সুসান নালুগুয়া হলেও চলতো কিন্তু আমাকে এই নামের সাথে আমার বাবার নামও জুড়ে দেয়া হয়েছে। আমার বাবার নাম ছিল কিগুলি। স্কুলে আমার নাম অন্তর্ভূক্তির সময় পিতার নামটি জুড়ে দেয়া হয়েছে।’
আর এখন, যদিও তার বাবা ‘সুসান’ নামটি দিয়েছিল তারপরও ঐ নাম নিয়ে সুসানের মনে ভালবাসা এবং ঘৃনায় মিশ্রিত এক অনুভূতি কাজ করে।
‘আমি আমার নামটিকে কলোনিয়াল অভিজ্ঞতার অংশ মনে করি যা এখন আর আনন্দদায়ক মনে হয় না। যখন কোন ব্যক্তি বা গোত্র এসে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে নতুন কিছু চাপিয়ে দেয় তখন তা পালন করা দুঃখজনক। যদিও পশ্চিমা বা আধুনিকতা আমি পছন্দ করি তারপরও এটা ভোলা কখনই সম্ভব না যে— তা আমাদের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার নিজস্বতা ছিনিয়ে নিয়েছে। এমনকি যদি ভদ্র ভাবে বলি, তবেও বলতে হয় আমাদের অতীত নিয়ে আমাদের মধ্যে তারা দ্বিধা তৈরি করেও দিয়েছে। যেমন ধরুন, মিশনারীরা, তারা আমাদের চিরায়ত দেবতাকে বাতিল করে দিয়ে নিজের মতবাদ, তত্ত্ব এবং ধ্যান-ধারনা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। নিজেদের মতবাদকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছে। এখানে আমাদের মতামতকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে। তারা কখনও জানতে চায়নি আমরা কিভাবে ভাবি, কি আমাদের ঐতিহ্য, কি আমাদের ইতিহাস। আমি মনে করি আমাদের মানুষদেরও একটা নিজস্ব সভ্যতা ছিল। হয়তো তা পশ্চিমাদের চেয়ে ভিন্ন কিন্তু তারপরও নিজস্ব। যেমন স্কুলে পড়তে গিয়ে আমি আবিষ্কার করি আমার মাতৃভাষায় পাঠদান করা হয় না। ফলে আমাকে নিজ আগ্রহে লুগানডা ভাষা শিখে নিতে হয়েছে।’
তার বোন একটি বই লিখছিল সেই সময়। স্পেকে, গ্র্যান্ট এবং অন্যান্য মিশনারীদের উপর ভিত্তি করে। সেই প্রসঙ্গ টেনে সুসান জানায়, ‘তারা আমাদের ভূমি, ধর্ম, প্রথা, সামাজিক কাঠামো ছিনিয়ে নিয়েছিল। আমাদের রাজা ছিল আমাদের সব। যখন রাজতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল (সম্ভবত ১৯৫৫ সালে মিউতসার-২ কে ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে) তখন তিনি “আমাদের অধিকার” ফিরে পেতে চেয়েছিল।’
“আমাদের অধিকার” বলতে রাজতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত এবং বুগান্ডার নিজস্ব সংস্কৃতিকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৬৬ সালে ইদি আমিনের নেতৃত্বে কৌশলগত কারনে সেই মিউতসা-২ কে আবার লন্ডনে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। সেই স্মৃতি মনে করে সুসান জানায় “কাবাকাকে আবার প্রাসাদ ছাড়তে বাধ্য করে সাধারন জনগনকে অপদস্থ করা হয়েছে। তারা এখনও মনে করে প্রাসাদে সামরিক বাহিনী প্রবেশ করে প্রাসাদের পবিত্রতা নষ্ট করেছে। জনগণের কাছে এটা বড় একটি আঘাত যে তাদের রাজাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নির্বাসনে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। সেই কারণে হয়ত ইদি আমিন পরবর্তী সময় সেই মরদেহ ফিরিয়ে এনে দাফনের ব্যবস্থা করেছিলেন।’
আলোচনার শুরুতে সুসান আমাদের জানিয়েছিল, খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী হলেও সে নিজেদের প্রাচীন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তবে সে তার অনেক বন্ধুর মত মনে করে না যে, সনাতন ধর্ম থেকে সরে এসে তারা পূর্বপুরুষদের বিরাগভাজন হয়েছে। তার এই অনুভূতিকে শুধু একটি ধর্মীয় সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে ভুল হবে। এই অনুভূতির ভেতর লুকিয়ে আছে নানারকম মতবাদ এবং বিশ্বাস। সেই মতামত আর বিশ্বাসগুলো সুসানকে তার নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের বাইরে নতুন একজন মানুষ হিসেবে প্রকাশ করে। ফলে, আমি ইচ্ছে থাকার পরও তার কাছে আর আফ্রিকার ইতিহাস, ভাষার ঐতিহ্য এবং মিথ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিনি।
আমি জানি, খারাপ অতীত কিংবা তার প্রেক্ষিতে যে মন্দ বর্তমান বিরাজ করে তা থেকে মানুষকে সরিয়ে নেয়ার কিংবা ভুলিয়ে দেয়ার কোন আফ্রিকান কৌশল নেই। বরং মনে হয়েছে, তাদের যে পরিস্থিতি তাকে দীর্ঘদিন পুষে রাখা কোন রোগের সাথে তুলনা করা চলে। যা আচমকা একদিন নিজের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করে আর আপনি সেই রোগ থেকে মুক্ত হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। কিন্তু আপনাকে সেই রোগ এতটাই কাবু করে ফেলে যে আপনি এক সময় স্বপ্ন দেখাও বন্ধ করে দেন। তখন আপনি ঐ রোগের সংঙ্গে একধরনের সমঝোতার মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে শুরু করেন। এবং ঐ সমঝোতার জীবনই সময়ের সাথে সাথে আপনার প্রকৃত জীবনে পরিনত হয়।
[অনুবাদকের কথাঃ ভি এস নাইপলের এই পুস্তকটি কোন এক বিমানবন্দরের বুক স্টোর থেকে সংগ্রহ করা। অনেক দিন ধরে খুব ধীরে ধীরে আমি পাঠ করে যাচ্ছি। পাঠ করার সময় মনে হলো এই পাঠ-অভিজ্ঞতা শেয়ার করা মন্দ হবে না। একটা দায়িত্ববোধের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখলে বই পড়ার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সহজ হয়। সেই ভাবনা থেকে অনুবাদ শুরু করি। এই বইয়ে রয়েছে ‘আফ্রিকান বিশ্বাস’কে কেন্দ্র করে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন ভ্রমন-বিষয়ক প্রবন্ধ। প্রতিটি প্রবন্ধ আবার অনেকগুলো অধ্যায়ে বিভক্ত। পাঠকের এবং নিজের সুবিধার্থে লাইন বাই লাইন অনুবাদ না করে, মূল তথ্য অবিকৃত রেখে বইটির বিষয়বস্তুর একটি ভাবানুবাদের চেষ্টা করা হয়েছে। তিনশত পঁচিশ পৃষ্ঠার ‘দ্যা মাস্ক অব আফ্রিকা’র ঠিক কত পর্ব পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারব জানি না। মতামত জানাতে পারেন : onemasud@gmail.com]