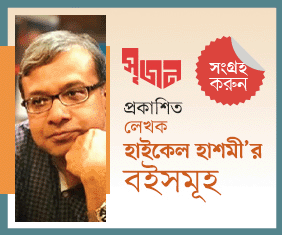গত ২৮ এপ্রিল ২০১৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশন আয়োজিত ‘জাতি ও শ্রেণি প্রশ্নে চিন্তা ও দুশ্চিন্তা উপমহাদেশে, বাংলাদেশে’ শীর্ষক আলোচনাসভা। অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. আহরার আহমদ এবং অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর পরিচিতি পাঠ করেন ঢাবির ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক গুণীজন বক্তৃতায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী’র দেয়া এ বক্তৃতাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৃজন। আজ থাকছে তার প্রথম পর্ব।
জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক গুণীজন বক্তৃতা দেবার এই সুযোগের জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও সম্মানিত। তিনি আমাদের অনেকেরই শিক্ষক ছিলেন, আমারও; যদিও ক্লাসরুমে নয়, ক্লাসের বাইরে। তাঁর দ্বারা আমি নানাভাবে প্রভাবিত। এই সুযোগে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাই।
জাতি ও শ্রেণী প্রশ্নে অধ্যাপক রাজ্জাকের আগ্রহের বিষয় আমরা জানতাম। সে আগ্রহ আমাদেরও, কারণ অন্যত্র যেমন উপমহাদেশে এবং বাংলাদেশেও তেমনি মানুষ শ্রেণীতেই বসবাস করে এবং জাতীয় পরিচয়েও পরিচিত হয়। দ্বিতীয় কারণ এই প্রশ্নের মীমাংসা আমরা এখনও করতে পারি নি। বাংলাদেশে জাতি প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে বলে মনে করা হয়, কিন্তু মীমাংসা যে সত্যি সত্যি হয়েছে তা বোধ হয় নয়। আর শ্রেণী প্রশ্ন তো রয়েছেই, কেবল আছে যে তা নয় দিনে দিনে তা প্রবল হচ্ছে, যার বহু প্রমাণের মধ্যে একটি হলো তিন ধারার শিক্ষা।
একথা বলা হয় যে একাত্তরে আমরা একটি জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছি। কথাটি ঠিক নয়, কারণ এ যুগে এক জাতি এক রাষ্ট্র এমন ব্যবস্থা সম্ভবই নয়। হ্যাঁ, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই বাঙালী, কিন্তু এখানেও ছোট আকারে হলেও অন্য জাতিসত্তা রয়েছে যারা বাঙালী নয়। আবার আমাদের জাতীয়তা বাঙালী না বাংলাদেশী এই বিতর্কও তৈরী করা হয়েছে। জাতির অনেকগুলো বাহ্যিক প্রকাশ রয়েছে, কিন্তু অন্তর্বস্তুতে জাতি হচ্ছে একটি চেতনা। এই চেতনা বিভিন্ন বস্তুগত উপাদানের ওপর নির্ভর করে। তবে প্রধান উপাদান ভাষা। অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাস, এরাও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু জাতিগত পরিচয় নির্ধারণে প্রধান উপাদান হচ্ছে ভাষা। সেই হিসেবে এই উপমহাদেশে কখনোই এক জাতির দেশ ছিল না। ইউরোপের মতোই ভারতবর্ষও বহুজাতির দেশ, ১৯৪৭ সালে এখানে অন্তত সতেরটি জাতিকে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল, যাদের প্রত্যেকেরই ভাষা আলাদা।
জাতি ও শ্রেণী প্রশ্নে অধ্যাপক রাজ্জাকের আগ্রহের বিষয় আমরা জানতাম। সে আগ্রহ আমাদেরও, কারণ অন্যত্র যেমন উপমহাদেশে এবং বাংলাদেশেও তেমনি মানুষ শ্রেণীতেই বসবাস করে এবং জাতীয় পরিচয়েও পরিচিত হয়। দ্বিতীয় কারণ এই প্রশ্নের মীমাংসা আমরা এখনও করতে পারি নি। বাংলাদেশে জাতি প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে বলে মনে করা হয়, কিন্তু মীমাংসা যে সত্যি সত্যি হয়েছে তা বোধ হয় নয়। আর শ্রেণী প্রশ্ন তো রয়েছেই, কেবল আছে যে তা নয় দিনে দিনে তা প্রবল হচ্ছে, যার বহু প্রমাণের মধ্যে একটি হলো তিন ধারার শিক্ষা।
ভারতবর্ষের বৈচিত্র্য যেমন ভৌগোলিক তেমনি জাতিগত। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে বৈচিত্র্য লুপ্ত করে দিয়ে এক করতে চেষ্টা করেছে। কাজটা মোগলরা করেছে, পরে অনেক বেশী দক্ষতার সঙ্গে করেছে ইংরেজরা। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধ হবে এটাই স্বাভাবিক, এবং ঐক্যবদ্ধ যাতে না হতে পারে তার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতাকে। হিন্দুরা ও মুসলমানরা দুই জাতি হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে, যদিও ছিল তারা দুটি সম্প্রদায়ই শুধু, জাতি নয়। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে দু’টুকরা করে ছেড়েছিল। ইতিহাস ভিন্ন রকম হতো যদি ভারতবর্ষীয় জাতিগুলো আলাদা আলাদা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়তে এবং সকলে একটি যৌথ সংস্থায় মিলিত হতে পারতো। সেটা ঘটে নি। জাতীয় স্বাধীনতার নামে ১৯৪৭-এ দেশভাগ ঘটলো, যার দরুন হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। সম্ভ্রমহানি ঘটেছে অসংখ্য নারীর। পাকিস্তানের জাতি সমস্যার সমাধানে পাঞ্জাবী শাসকেরা সম্মত ছিল না, যার কারণে একাত্তর সালে পাঞ্জাবী-নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী নির্বিচারে বাঙালী-নিধন ঘটিয়েছে। সংঘটিত হয়েছে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম গণহত্যাগুলোর একটি।
দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচারকদের ভেতর সর্বাধিক পরিচিত ব্যক্তিটি ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। নিজের কাক্সিক্ষত রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার মুহূর্তেই তাঁর মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল কাজটি ঠিক হলো কি না তা নিয়ে। ১৪ আগস্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, ১১ আগস্টে নবগঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে নিজের ভাষণটিতে তিনি বলেছিলেন ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না, তাই এই বিভাজন। বলেছিলেন কাজটা ঠিক হয়েছে কি হয় নি ভবিষ্যতেই তা দেখা যাবে। কিন্তু আরও বেশী তাৎপর্যপূর্ণ যে-কথাটি তিনি উচ্চারণ করেছেন সেটা এই যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য থাকবে না। ইংল্যান্ডের উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন যে এককালে সেখানে ক্যাথলিকে প্রোটেস্ট্যান্টে প্রবল বিরোধ ছিল, কিন্তু বিরোধের সেই আগুনে বিশুদ্ধ হয়ে এখন তারা এক হয়ে গেছে। পাকিস্তানের নাগরিকরা যদি কর্তব্যপালন ও ঐক্য গড়ে তোলার আদর্শে অটল থাকে তাহলে এখানেও দেখা যাবে যে,
in course of time Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state.1
বলা হয় যে একাত্তরে আমরা একটি জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছি। কথাটি ঠিক নয়, কারণ এ যুগে এক জাতি এক রাষ্ট্র এমন ব্যবস্থা সম্ভবই নয়। হ্যাঁ, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই বাঙালী, কিন্তু এখানেও ছোট আকারে হলেও অন্য জাতিসত্তা রয়েছে যারা বাঙালী নয়। আবার আমাদের জাতীয়তা বাঙালী না বাংলাদেশী এই বিতর্কও তৈরী করা হয়েছে। জাতির অনেকগুলো বাহ্যিক প্রকাশ রয়েছে, কিন্তু অন্তর্বস্তুতে জাতি হচ্ছে একটি চেতনা। এই চেতনা বিভিন্ন বস্তুগত উপাদানের ওপর নির্ভর করে। তবে প্রধান উপাদান ভাষা।
স্পষ্টতঃই দ্বিজাতিতত্ত্বকে তিনি আর গ্রহণযোগ্য মনে করছেন না। পাকিস্তানী বলে একটি নতুন জাতি তৈরী হবে এটাই তিনি আশা করছিলেন। সে-জাতির ভিত্তি যে ধর্ম হবে না এটা তিনি মেনে নিয়েছিলেন। ওই বক্তৃতা দানের ছয়-সাত মাস পরে ঢাকায় এসে রেসকোর্স ময়দানে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন তাতেও পাকিস্তানী জাতির কথাই আছে, কিন্তু এবার তিনি যা যুক্ত করলেন সেটা হলো ভাষা। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে, এবং উর্দু ছাড়া আর কিছুই হবে না বলে দিয়েছেন তিনি। ভাষা দিয়ে জাতিকে সংহত করতে হবে একথা তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন। এর ছয় বছর পরে, ১৯৫৪ সালে এ কে ফজলুল হকও তাঁর এক বক্তৃতাতে জাতিগঠনে ধর্মের নয় ভাষার প্রাধান্যের কথাই বললেন। পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য। পুরানোজনদের এক সম্বর্ধনা সভাতে কিছুটা আবেগাপ্লুত হয়ে তিনি বলেছিলেন,
রাজনৈতিক কারণে বাংলাকে বিভক্ত করা হতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি আর আকাঙ্ক্ষাকে কোন শক্তিই কোন দিন ভাগ করতে পারবে না। দুই বাংলার বাঙ্গালী চিরকাল বাঙ্গালীই থাকবে।২
তাঁর বিরুদ্ধে সরকার তখন রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছিল। সে-অর্থে তো জিন্নাহও রাষ্ট্রদ্রোহী। তাঁরা দু’জনেই তো দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিতটাকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন, যে-তত্ত্বের ওপর ভর করে পাকিস্তানের সৃষ্টি। ইতিহাসের কৌতুকে পাকিস্তান প্রস্তাবের যিনি প্রণেতা ও যিনি উত্থাপনকারী তাঁরা উভয়েই মানছেন যে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করাটা ঠিক হয় নি, এবং বলতে চাইছেন যে রাষ্ট্র ও জাতি এক ব্যাপার নয়। আরও যেটা তাৎপর্যপূর্ণ সেটা হলো পরস্পরবিরোধী অবস্থান থেকে উভয়েই জানাচ্ছেন যে জাতিগঠনে ধর্মের চেয়ে ভাষার ভূমিকা অধিক শক্তিশালী। ১৯৫৪তে ফজলুল হক আর যাই হোন জাতিদ্রোহী ছিলেন না। রাষ্ট্রদ্রোহিতা ভিন্ন ব্যাপার। রাষ্ট্র অস্থায়ী, জাতি স্থায়ী।
চলবে…
তথ্যসূত্র:
১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান, ঢাকা, ১৯৮২, প্রথম খ-, পৃ ৪০-৪২১.
২. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ ১৬৪