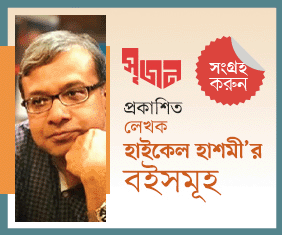পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের অত্যন্ত উজ্জ্বল প্রতিনিধি হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান। রাজনৈতিক জীবনে তিনি অব্যাহত আন্দোলন করেছেন, বহু রকমের দুর্ভোগ ও নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং বাঙালীর জাতীয়তাবাদের পক্ষে ছিলেন অনমনীয়। বাঙালী বলতে কেবল সুবিধাভোগীদের বুঝতেন না, সকল শ্রেণীর বাঙালীকেই বুঝতেন। কারাবন্দী অবস্থায় লেখা তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা বইয়ের পাতায় পাতায় এর পরিচয় পাওয়া যাবে। ১৯৬৬-তে যখন তাঁকে বন্দী করা হয় তখন তাঁর বিরুদ্ধে মামলা ছিল ১১টা, তাঁকে রাখা হয়েছিল অন্যসকল কয়েদী ও বন্দীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে। সন্ধ্যা হলেই সেলের দরজা তালাবন্ধ হতো। সময় কাটানো অত্যন্ত কঠিন। কষ্ট হয়েছে, কিন্তু হতাশ হন নি। কারাজীবনটা দাঁড়িয়েছিল নির্জন দ্বীপে রবিনসন ক্রুশোর দিনযাপনের মতো। এর মধ্যেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে তাঁর সংবেদনশীলতা। বাইরের মানুষের কথা তো ভাবছেনই, ভেতরে যারা আছে, কয়েদী ও সিপাহী-জমাদার, যারা তার আশেপাশে থাকে তাদের সঙ্গে নিজের খাবার ভাগ করে খান; রোজনামচায় লেখেন, ‘আমি না খেয়ে থাকতে রাজি, কিন্তু ওদের না দিয়ে খেতে পারব না।’ জেলখানায় কয়েদি ও সিপাহীদের কাছে মুড়ি দুর্লভ সামগ্রী। তিনি মুড়ি আনিয়ে পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ মাখিয়ে নিজে খান এবং আশেপাশের সবাইকে খাওয়ান। পাকের ঘরে মোরগ-মুরগি থাকে তিনটি। একটির অসুখ হলে কাতর হয়ে পড়েন। কবুতর ও তাদের বাচ্চাদের দেখেন, দেখেন কাকদের জীবনযাত্রা। সেলের সামনের ফুল গাছগুলোর যত্ন নেন, আগাছা পরিষ্কার করেন। পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী থেকেই এসেছেন, কিন্তু সেই শ্রেণীর সঙ্কীর্ণতা ও অসংবেদনশীলতাকে সঙ্গে রাখেন নি, সরিয়ে ফেলতে পেরেছেন, এবং সে জন্যই অতবড় হয়েছেন। কিন্তু অন্য অনেকেই তা পারেন না, পারেন নি।
১৯৬২ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে আটক ছিলেন ডা. এম এ করিম। তিনি বাম ঘরানার লোক; কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গেই তাঁর খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। কারাগারে তখন আওয়ামী লীগের বড় এক নেতা ছিলেন, এক সময়ে যিনি মন্ত্রীও ছিলেন, প্রথমে প্রদেশের পরে কেন্দ্রের। তাঁর সম্পর্কে করিম সাহেব লিখেছেন যে,
ভদ্রলোক চুলে সরষের তেল মাখতেন। জেলখানা থেকে বরাদ্দ করা ছিল। আর এই বরাদ্দ থেকে সরষের তেল বাঁচিয়ে প্রায় এক টিন জমিয়ে ফেললেন। এমনি ভাবে নিজের বরাদ্দ মাখন থেকে বাঁচিয়ে জ্বালিয়ে ঘি তৈরি করেছেন। জেল থেকে বেরুবার সময়ে সাথে করে নিয়ে গেছেন একটিন সরষের তেল ও এক সের ঘি।…বিশ্বাস করতেও কষ্ট হবার কথা। আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না।১৪
এই ধরনের জাতীয়তাবাদীদের কাছে সবকিছুই ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এমনকি জেলখানার সামান্য সুযোগ সুবিধাগুলোও। ওদিকে কারাযন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় কেউ কেউ হার মানতেন। কেউ-বা বন্ড দিয়ে বের হয়েছেন এবং রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন। শামসুল হকের কথা উল্লেখ করেছি। শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীতে আছে শামসুল হক রাতভর জিকির করতেন। তাতে অন্যদের যে অসুবিধা হয় সেদিকে তাকাতেন না, বলতেন এ তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা। জেল থেকে যখন বের হলেন তখন দেখা গেল মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। অত্যন্ত মহৎ একটি সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল।
কারাবন্দী অবস্থায় লেখা তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা বইয়ের পাতায় পাতায় এর পরিচয় পাওয়া যাবে। ১৯৬৬-তে যখন তাঁকে বন্দী করা হয় তখন তাঁর বিরুদ্ধে মামলা ছিল ১১টা, তাঁকে রাখা হয়েছিল অন্যসকল কয়েদী ও বন্দীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে। সন্ধ্যা হলেই সেলের দরজা তালাবন্ধ হতো। সময় কাটানো অত্যন্ত কঠিন। কষ্ট হয়েছে, কিন্তু হতাশ হন নি। কারাজীবনটা দাঁড়িয়েছিল নির্জন দ্বীপে রবিনসন ক্রুশোর দিনযাপনের মতো।
জাতীয়তাবাদী ধারার প্রগতিশীল অংশের ভেতর এই উপলব্ধিটা তৈরী হচ্ছিল যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুক্তি নেই, সমাজতন্ত্রেই যেতে হবে। শেখ সাহেবের বই দু’টিতে এমন চিন্তার আভাস পাওয়া যায়। ১৯৬৬-তে জেলে এসে তিনি দেখেন জেলের ভেতরেই পুঁজিবাদ কায়েম হয়ে গেছে। শিক্ষার কোনো দাম নেই, দাম টাকার, টাকা দিয়ে অনেক রকমের সুযোগসুবিধা পাওয়া যায়। আগে যখন এসেছেন দেখেছেন কিছুটা চক্ষুলজ্জা ছিল, এখন তাও নেই। আত্মজীবীনতে তিনি লিখছেন ১৯৫৩ সালে তিনি চীনে গিয়েছিলেন, বিশ্ব শান্তি সম্মেলন উপলক্ষে। চীন স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৯-এ, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৭-এ, অথচ ওই কয়বছরেই চীনের যে উন্নতি ও পরিবর্তন হয়েছে দেখে এবং কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুভূতি হয়েছিল এই রকমের :
আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না।১৫
১৯৬৬-র কারাগারের রোজনামচায় তিনি লিখেছেন, আইয়ুব খানের শাসনে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ভিক্ষুক হয়ে গেছে। আমেরিকার কাছে ভিক্ষা চাইছে। মন্তব্য করেছেন,
ভিক্ষুকের কোনো সম্মান নাই। তবে শোয়েব সাহেব (অর্থমন্ত্রী) যে অর্থনীতি এখানে চালাইতেছেন তাতে ইহা ছাড়া আইয়ুব সাহেবের উপায়ই বা কি ছিল? একমাত্র সমাজতন্ত্র কায়েম করলে কারও কাছে হেয় হয়ে সাহায্য নিতে হতো না।১৬
জেলখানায় কমিউনিস্ট রাজবন্দীরা থাকেন। তাঁদেরকে আলাদা করে রাখা হয়, পাছে তাঁদের প্রভাবে পড়ে অন্যরা কমিউনিস্ট হয়ে যায়। শেখ মুজিবকে তারা তাঁদের বাগান থেকে কুমড়ার ডগা, ঝিংগা, কাকরোল এসব পাঠান। তিনি অভিভূত হন। তাঁর প্রতিক্রিয়া, “এঁরা ত্যাগী রাজবন্দী। দেশের জন্য বহুকিছু ত্যাগ করেছেন। জীবনের সব কিছু দিয়ে গেলেন এই নিষ্ঠুর কারাগারে। আমি তাঁদের সালাম পাঠালাম।”১৭ জন্মদিনে এঁরা তাঁকে পাঠিয়েছেন একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। মুজিব লিখছেন,
তাঁদের এই উপহার আমার কাছে অনেক মূল্যবান। শুধু মনে মনে বললাম, তোমাদের মতো ত্যাগ যেন আমি করতে পারি। তোমরা যে নীতিই মানো না কেন, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তোমরা দেশের মঙ্গল চাও, তাতে আমার সন্দেহ নাই।… তোমাদের আমি শ্রদ্ধা করি।১৮
কোনো দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদীর পক্ষে এমনটা ভাবা সম্ভব নয়। তাছাড়া দক্ষিণপন্থীরা কমিউনিস্টদের কাছ থেকে এমন শুভেচ্ছাও আশা করতে পারতেন না। শেখ মুজিবেরই তো সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। জাতীয়তাবাদীও। তবে পুরোপুরি দক্ষিণপন্থী এবং পরিপূর্ণরূপে সুবিধাবাদী, নিজেকে তিনি নন-কমিউনিস্ট বলতেন না, বলতেন এ্যান্টি-কমিউনিস্ট। মোহাম্মদ তোয়াহা স্মরণ করেছেন যে ১৯৪৪-এ মুসলিম লীগ কর্মীরা যখন একত্রে কাজ করছেন তখনই দেখা গেছে দলের ভেতর ‘কমিউনিস্ট খেদাও’ তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে, এবং ঢাকায় সে-তৎপরতার নেতৃত্ব দিচ্ছেন খন্দকার মোশতাক।১৯ শেষ পর্যন্ত তিনি কোন পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছবেন তার পূর্বভাস সূত্রপাতেই দেখা দিয়েছিল।
কমিউনিস্টরা যে সঠিক পথে চলছেন না এমন কথা শেখ মুজিবও বলেছেন; কিন্তু তাঁর সুর, স্বর ও উপমা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কমিউনিস্ট ভাবাপন্নদের তিনি যা বলতেন বলে স্মরণ করেছেন তা হলো, “জনসাধারণ চলছে পায়ে হেঁটে, আর আপনারা আদর্শ নিয়ে উড়োজাহাজে চলছেন। জনসাধারণ আপনাদের কথা বুঝতেও পারবে না, আর সাথেও চলবে না। যতটুকু হজম করতে পারবে ততটুকু জনসাধারণের কাছে পেশ করা উচিত।”২৬
তা খন্দকার মোশতাকরা তো শুরু থেকেই দক্ষিণপন্থী ছিলেন, কিন্তু অলি আহাদ তো তা ছিলেন না; অন্য অনেকের তুলনাতেই তিনি ছিলেন অনেক অগ্রসর। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ যখন গঠিত হয় তখন তাতে তিনি যোগ দিতে চান নি, সংগঠনটি অসাম্প্রদায়িক নয় বলে; একই কারণে আওয়ামী মুসলিম লীগও তাঁকে আকর্ষণ করে নি। তিনি ছিলেন যুবলীগে, যেখানে আত্মপ্রকাশে-অসমর্থ কমিউনিস্টরা গোপনে কাজ করছিলেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন-প্রভাবিত পূর্ব-এশীয় যুব সম্মেলনেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন।
১৯৫০-এ নাচোলে কৃষকবিদ্রোহ হয়। নেতৃত্বে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টির স্থানীয় নেত্রী ইলা মিত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং যে-ভাবে নির্যাতন করে তাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নৃশংস চরিত্রের প্রথম উন্মোচন ঘটে। রাজশাহী কোর্টে ইলা মিত্র একটি জবানবন্দী দেন। অলি আহাদ স্মরণ করেছেন যে ‘স্পর্শকাতর ও ক্ষুব্ধ মনের তাড়নায়’ তিনি ‘সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে’ অতিগোপনে বহু কষ্টে ঢাকার একটি ছাপাখানা থেকে ইস্তেহারের আকারে জবানবন্দীটি ছাপিয়ে সন্তর্পণে সর্বত্র বিলি করার ব্যবস্থা করেন। জবানবন্দীটি ছিল ইংরেজীতে, ইস্তেহারে ইংরেজীর সঙ্গে বাংলায় অনুবাদও ছিল, এবং অনুবাদ তিনি নিজেই করেছিলেন।২০ কাজটি সামান্য ছিল না। যেমন দুঃসাহসিক, তেমনি দুঃসাধ্য, এবং ঐতিহাসিক। একসময়ে আওয়ামী লীগের তিনি সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যখন ন্যাপ গঠিত হলো তখন আওয়ামী লীগ ছেড়ে ন্যাপেই যোগ দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের ভেতর কমিউনিস্ট ঘরানার যাঁরা ছিলেন সবাই ন্যাপে চলে গিয়েছিলেন।
কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে অলি আহাদ কেবল অ-কমিউনিস্ট নন, খন্দকার মোশতাকের মতোই অঙ্গীকারবদ্ধ কমিউনিস্ট-বিদ্বেষীতে পরিণত হয়েছেন। প্রমাণ আছে তাঁর লেখা জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫ বইতে। বইটি তিনি বাকশাল গঠনের পরে জেলখানায় থাকা অবস্থাতে লিখতে শুরু করেন। এই বইতে কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ জ্বল জ্বল করছে। ধরা যাক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনাকালের বিবরণ। তিনি এমন একটি তথ্য দিচ্ছেন যা অন্যকেউ দেন নি। সেটা হলো আন্দোলনে কমিউনিস্ট-বিরোধিতা। সরকারের পক্ষ থেকে বরং উল্টোটা প্রচার করা হয়েছিল, বলা হয়েছিল যে আন্দোলন কমিউনিস্ট ও হিন্দুদের কাজ। হিন্দুদের ব্যাপারটা সর্বৈব মিথ্যা: কিন্তু কমিউনিস্টেরা যে ছিল সেটা মোটেই মিথ্যা নয়। অলি আহাদ জানাচ্ছেন যে ১৯৪৮-এর ১১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায় যে সাধারণ ছাত্রসভা হয় সেটাকে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা বানচাল করার চেষ্টা করেছিল, আর তাদের সঙ্গে ছিলেন পার্টির নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম। “কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের সচেতন সংগ্রামী চেতনা উপরোক্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।” সরদার ফজলুল করিম নাকি সেখানেই নিবৃত্ত হন নি, পরের সভাতেও (১৭ মার্চ) তিনি “কতিপয় সমর্থকের সহায়তায় গোলযোগ সৃষ্টির প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ইহা নাকি তাহাদের বিপ্লবের স্বার্থে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কর্মসূচীভুক্ত।”২১ অলি আহাদ আরও জানাচ্ছেন যে ১৯৪৮ সালের ৩০ জুন কমিউনিস্ট পার্টি সদরঘাটের করনেশন পার্কে একটি জনসভা করার চেষ্টা করে।
কিন্তু জনতার আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত কমিউনিস্ট কর্মীরা স্ব-স্ব প্রাণ বাঁচাইবার প্রয়াসে সভাস্থল হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। সরকার সমর্থক মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান বীরদর্পে বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করিয়া জনতার উদ্দেশে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। এই ভাবেই রাষ্ট্রদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক বলিয়া অভিযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীবৃন্দ ধীরে ধীরে প্রকাশ্য কর্মসূচী বর্জন করিয়া গোপন সংগঠনের দিকে মনোনিবেশ করে।২২
ভাবটা এই রকমের যে ভালোই হয়েছে, বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমন ফল।
আমাদের কিন্তু মনে হয় না এটা তাঁর ১৯৪৮ সালের অনুভূতি। এটি তাঁর ১৯৭৫-পরবর্তী অর্জন। ১৯৭৪ সালেই তিনি ‘আজাদ বাংলা’ আন্দোলনকে শক্তিশালী করা শুরু করেছেন; গ্রেপ্তার হয়েছেন ৩০ জুন ১৯৭৪-এ; মুক্তি পেতেন না ১৯৭৫-এর নৃশংস ঘটনাটি যদি না ঘটতো। মুক্তি লাভের পরে তার মনে হয়েছে, “খন্দকার মোশতাক আহমদ দিল্লীর দাসত্ব মোচনের যে বলিষ্ঠ ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা আজাদ বাংলা আন্দোলনের মর্মবাণী হইতে পৃথক নয়।”২৩
কেবল রাগের নয় মওলানা ভাসানী পাত্র হয়েছেন বিস্তর ভুলবোঝাবুঝিরও। মনে হয়েছে তিনি রহস্যময়। কেউ বলেছেন তিনি হিংসার প্রচারক, অন্যরা বলেছেন লাল রঙে রঙীন। অভিযোগ আছে তিনি ঘন ঘন দল ভাঙেন। রহস্যের মূল কারণ কিন্তু এটা যে তিনি পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে এসেও সেই শ্রেণীর চরিত্রদোষগুলো যেভাবে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন তেমনটা সাধারণত দেখা যায় না। মনে হয়েছে তিনি খাপ না-খাওয়া, তবে আসলে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার।
আটচল্লিশে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ছিলেন। তখন তিনি গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।২৪ আটচল্লিশে লিখলে অন্যভাবে লিখতেন। ইলা মিত্রের জবানবন্দী প্রচার তিনি যে শুধু করুণায় সিক্ত হয়েই করেছিলেন তা ভাববার কারণ নেই, করেছিলেন রাজনৈতিক কর্তব্যবোধের অনুপ্রেরণাতে; এবং পার্টি তাঁর সঙ্গে ছিল বলেই করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তিনি একেবারেই বদলে গেছেন। কমিউনিস্টদের নামই শুনতে পারেন না। তাঁদের সম্পর্কে অমার্জিত রসিকতা করেন। ১৯৬৮ সালে মস্কোপন্থীরা যখন ভাসানীপন্থী ন্যাপ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে তখন সমমনা জ্ঞান করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে। স্পষ্টভাবে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর মতাদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন। উক্তিটি ছিল, ‘ভলগা-ইয়াংসি নদীতে বৃষ্টি হইলে ঢাকার বুড়িগঙ্গার পাড়ে দাঁড়াইয়া আমার ছাতা খুলিবার সবিশেষ কারণ নাই।”২৫ কমিউনিস্টরা যে সঠিক পথে চলছেন না এমন কথা শেখ মুজিবও বলেছেন; কিন্তু তাঁর সুর, স্বর ও উপমা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কমিউনিস্ট ভাবাপন্নদের তিনি যা বলতেন বলে স্মরণ করেছেন তা হলো, “জনসাধারণ চলছে পায়ে হেঁটে, আর আপনারা আদর্শ নিয়ে উড়োজাহাজে চলছেন। জনসাধারণ আপনাদের কথা বুঝতেও পারবে না, আর সাথেও চলবে না। যতটুকু হজম করতে পারবে ততটুকু জনসাধারণের কাছে পেশ করা উচিত।”২৬ সত্যটা তাই দাঁড়ায় এই রকমের যে জাতীয়তাবাদের ভেতরে কট্টরপন্থায় ও উদারনীতিতে মৌলিক পার্থক্য নেই ঠিকই, কিন্তু দূরত্ব থাকে।
অলি আহাদকে যে মস্কোপন্থীরা কাছের মানুষ ভেবেছিলেন তার একটা ভিত্তি ছিল। কমিউনিস্ট-বিরোধী হবার পূর্বক্ষণে তিনি ঘোরতর স্ট্যালিনবিরোধী ও পুরোপুরি ক্রুশ্চেভ-ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি লিখছেন,
সবাই স্বীকার করিবেন, স্ট্যালিন শাসনের হত্যা ও নিধনের ভাষাকে ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত নাগরিকদের জীবনে নিরাপত্তার ভাষায় রূপান্তরিত করিবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। মানবাধিকারের ইতিহাসেও যে নিরপেক্ষ মূল্যায়নে তাঁহার নাম যথার্থ মর্যাদার সহিত উচ্চারিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।২৭
সেই সময়ে তাঁর অবিচল বিশ্বাস নিকিতা ক্রুশ্চেভ মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার স্বার্থেই সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ও ধনতান্ত্রিক বিশ্বের ‘শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান’ নীতি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালনে সচেষ্ট ছিলেন।”২৮
জরুরী প্রশ্নটা এই যে এভাবে তিনি বদলে গেলেন কেন? বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে খুব বড় দুঃসাহসী ও কর্মোদ্যমপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে ছিল পেটি বুর্জোয়া অস্থিরতা ও আত্মসচেতনতা। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি অত্যন্ত উচ্চাকাক্সক্ষী ছিলেন। যে সকল কারণে শামসুল হক মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন সেগুলো তাঁর ভেতরেও ছিল; কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ছিলেন বলে হারিয়ে যান নি। প্রথমে কমিউনিস্টদের সঙ্গে গেলেন, দেখলেন কাজ হচ্ছে না, তখন আওয়ামী লীগে গেলেন; দেখলেন সেখানে তাঁর অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই বের হয়ে গেলেন; যোগ দিলেন ন্যাপে; কিন্তু দেখা গেল ন্যাপ কমিউনিস্টদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যাদেরকে তিনি ছেড়ে এসেছেন, এবং যারা কখনোই রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে পারবে না। অন্যদিকে আবার তার সমসাময়িক রাজনীতিকরা অধিকাংশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। শেষ আশ্রয়টা ভেঙে যাওয়াতে রাগটা গিয়ে পড়েছিল কমিউনিস্টদের ওপরই। এবং ন্যাপ-প্রধান ভাসানীর ওপরও। ভাসানীর ওপর তাঁর একার নয়, অনেকেরই বিলক্ষণ রাগ ছিল।
কেবল রাগের নয় মওলানা ভাসানী পাত্র হয়েছেন বিস্তর ভুলবোঝাবুঝিরও। মনে হয়েছে তিনি রহস্যময়। কেউ বলেছেন তিনি হিংসার প্রচারক, অন্যরা বলেছেন লাল রঙে রঙীন। অভিযোগ আছে তিনি ঘন ঘন দল ভাঙেন। রহস্যের মূল কারণ কিন্তু এটা যে তিনি পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে এসেও সেই শ্রেণীর চরিত্রদোষগুলো যেভাবে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন তেমনটা সাধারণত দেখা যায় না। মনে হয়েছে তিনি খাপ না-খাওয়া, তবে আসলে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার অত্যাবশ্যতার বিষয়ে তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে সরব হয়েছিলেন। কিন্তু অন্য জাতীয়তাবাদীরা যা করেন নি, তিনি তাও করেছিলেন; শ্রেণী প্রশ্নকেও অবহেলা করেন নি। বস্তুত তিনি ছিলেন মেহনতীদের নেতা, শ্রেণীবিভাজন দূর করার ব্যাপারে তাঁর অবস্থান ছিল বৈপ্লবিক। ভাসানীর রাজনীতি দাঁড়িয়েছিল সমাজবিপ্লবের। সে জন্যও অনেকেই তাঁকে বুঝতে পারেন নি, বুঝতে চানও নি। যাঁরা বুঝেছেন তাঁরা বিদ্বিষ্ট হয়েছেন। অলি আহাদও বিরক্ত হয়েছেন মওলানা পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে কেন কাজ করছেন না সেটা ভেবে, কেন নির্বাচনে-জেতার দল খাড়া করছেন না সেটা দেখে। বুঝতে না-পেরে অলি আহাদের মনে নানা রকমের সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মনে করেছেন মওলানা কুচক্রীদের হাতে পড়েছেন। ভেবেছেন লোকটি জনপ্রিয়তালোভী। নইলে ১৯৭০-এর ঘুর্ণিঝড়ের পরে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবীকে আকস্মিকভাবে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাবেন কেন? শেখ মুজিবুর রহমান এবং অলি আহাদ, দু’জনেই মওলানার খুব কাছের মানুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁরা উভয়েই নেতা মানতেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। মওলানা যে সোহরাওয়ার্দীর প্রথমে সমালোচনা এবং পরে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করলেন তাতে তাঁদের দু’জনেরই অসন্তোষ ছিল; এবং ব্যাখ্যাও, তাঁরা একইভাবে করেছেন। ব্যক্তিগত ঈর্ষা, তথা পরশ্রীকাতরতাই দায়ী বলে তাঁদের মনে হয়েছে।২৯ সোহরাওয়ার্দীর গণতন্ত্র আর ভাসানীর গণতন্ত্র যে এক নয়, যোজন যোজন ব্যবধান, সেটা তাঁরা বিবেচনায় রাখেন নি।
মেহনতী মানুষেরা কিন্তু ভাসানীকে ঠিক ভাবেই চিনেছে। তারা তাঁকে আপনজনই মনে করেছে। ভাসানীর তোলা দাবী কেবল স্বাধীনতার ছিল না, ছিল মুক্তিরও। যে জন্য সত্তর সালে তাঁর অনুসারীদের আওয়াজটা ‘জাগো জাগো বাঙালী জাগো’ ও ‘বীর বাঙালী অস্ত্র ধরো পূর্ববঙ্গ স্বাধীন করো’তে সীমিত থাকে নি, পার হয়ে চলে গেছে আরও দূরে। আওয়াজটা দাঁড়িয়েছে ‘শ্রমিক কৃষক অস্ত্র ধরো পূর্ববঙ্গ স্বাধীন করো’। ‘তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা’র সাথে শোনা গেছে ‘তোমার আমার ঠিকানা খেতখামার কারখানা’।
মেহনতী মানুষেরা কিন্তু ভাসানীকে ঠিক ভাবেই চিনেছে। তারা তাঁকে আপনজনই মনে করেছে। ভাসানীর তোলা দাবী কেবল স্বাধীনতার ছিল না, ছিল মুক্তিরও। যে জন্য সত্তর সালে তাঁর অনুসারীদের আওয়াজটা ‘জাগো জাগো বাঙালী জাগো’ ও ‘বীর বাঙালী অস্ত্র ধরো পূর্ববঙ্গ স্বাধীন করো’তে সীমিত থাকে নি, পার হয়ে চলে গেছে আরও দূরে। আওয়াজটা দাঁড়িয়েছে ‘শ্রমিক কৃষক অস্ত্র ধরো পূর্ববঙ্গ স্বাধীন করো’। ‘তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা’র সাথে শোনা গেছে ‘তোমার আমার ঠিকানা খেতখামার কারখানা’। ‘জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো’র পাশাপাশি ধ্বনি উঠেছে ‘চলো চলো গ্রামে চলো’। আর যে আওয়াজটা উঠতি বুর্জোয়াদেরকে ভীষণ ভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে সেটি ছিল, ‘কেউ খাবে আর কেউ খাবে না, তা হবে না তা হবে না’।
ওই আওয়াজটাই কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের যাঁরা সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পক্ষে কাজ করেছিলেন তাঁদেরকে আকর্ষণ করেছে। আওয়াজের পেছনকার মানুষটিকেও তারা জানত। সে জন্য তাঁর নেতৃত্বে যখন ন্যাপ গঠিত হয় তখন সেটি বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের দল থাকে নি, সারা পাকিস্তানের দলে পরিণত হয়েছিল। পাঞ্জাবী শাসনকর্তাদের জাতিগত নিপীড়নে বিক্ষুব্ধ সিন্ধী, পাঠান ও বেলুচ, এবং সামন্ত-বুর্জোয়াদের শাসনে জর্জরিত পাঞ্জাবী মেহনতীদের নেতারা চলে এলো ন্যাপে। বস্তুত তখন ধর্মনিরপেক্ষ সর্ব-পাকিস্তানী রাজনৈতিক সংগঠন ছিল ওই একটিই। সমাজবিপ্লবের অঙ্গীকারবদ্ধ নেতা হিসেবে পাকিস্তানে ভাসানী ছিলেন অদ্বিতীয়।
তিনি কৃষকের সমস্যা জানতেন। সে জন্য ছিলেন সামন্তবাদবিরোধী। সাম্রাজ্যবাদকেও চিনেছেন। পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর যোগ ছিল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, কিন্তু পাকিস্তানী ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অন্তঃসারশূন্যতাটি ধরতে তাঁর বিলম্ব ঘটে নি। শাসকেরা তাঁকে জেলে পুরেছে, সেখানে তাঁর আলাপ হয়েছে কমিউনিস্ট বন্দীদের সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদকে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন ব্যবস্থার মর্মবস্তুকে আত্মস্থ করতে তাঁর সময় লাগে নি। ঝুঁকে পড়েছেন তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে এসেছে আন্তর্জাতিকতা। কারাগারে তাঁর সাথী ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ। হাজী দানেশ তেভাগা আন্দোলনের নেতা, এবং উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু হাজী দানেশ যেখানে দলত্যাগ করেছেন, পর্যায়ক্রমে যোগ দিয়েেিছন বাকশালে, জিয়ার দলে এবং এরশাদের দলে, ভাসানী সেখানে অনড় ছিলেন তাঁর অবস্থানে। থাকতেন গরীব মানুষের সঙ্গে; গান্ধীজির মতো নয়, কমিউনিস্টদের মতোই। পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বতন্ত্র স্বার্থ দেখেন নি, সে জন্য অনেকেই তাঁর সঙ্গে থাকতে পারেন নি, এবং তিনি নিজে যখন দেখেছেন তাঁর-গড়া দল পেটি বুর্জোয়াদের দখলে চলে গেছে, তখন বাধ্য হয়েছেন নতুন দল গড়তে। শেষ পর্যন্ত যে নিতান্ত একা হয়ে গিয়েছিলেন সে অপরাধ তাঁর নয়, তাঁর সঙ্গে যে কমিউনিস্টদের থাকবার কথা ছিল তাঁদের।
সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন অপুঁজিবাদী পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ও সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতি গ্রহণ করলো তখন তিনি মস্কোপন্থীদের সঙ্গে থাকেন নি; সম্ভব ছিল না থাকা। কিন্তু বিপরীতে পিকিংপন্থীরাও মতাদর্শিক ধর্মভ্রান্তির দরুন বিভক্ত হয়ে পড়লো, এবং নেতৃত্বদানে অযোগ্য ভেবে তাঁকে পরিত্যাগ করলো। পাঞ্জাবী শাসকদের সাথে আপোস যে মীমাংসার পথ নয়, ১৯৭০-৭১-এ ভাসানী সে-কথা একের পর এক জনসভা করে ঘোষণা করেছেন, এবং যখন গণহত্যা শুরু হয় তখন বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে যমুনা নদীতে নৌকা ভাসিয়ে চলে গেছেন প্রতিবেশী ভারতে। ভারত তাঁকে নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছিল; পাছে তিনি বাঙালী জাতীয়তাবাদের আওয়াজ তোলেন। কিন্তু সেটা করা তখন তাঁর কর্মসূচীতে ছিল না, কেননা তিনি কেবল জাতি প্রশ্ন নিয়ে ভাবছিলেন না, তাঁর চিন্তায় শ্রেণী প্রশ্নটা ছিল আরও জরুরী, এবং তিনি জাতি সমস্যার মীমাংসা চেয়েছেন শ্রেণী সমস্যার মোকাবিলার জন্যই। স্বাধীনতার পর মওলানার দল বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকল না, কিন্তু তাঁর নিজের অবস্থানটা রইলো। মস্কোপন্থীরা সুবিধায় ছিল, কারণ তারা জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগের সহযোগী হতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থানের নিরাপত্তায় দাঁড়িয়ে ১৯৭৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর ঢাকার এক জনসভায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মণি সিংহ ভাসানীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন প্রয়োজনে তাঁকে ‘টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে।’৩০ অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। অবিশ্বাস্য তো এটাও যে বুর্জোয়াদের বিরোধিতার এত কালের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ভুলে বঙ্গবন্ধুকে কমরেড মণি সিংহ বার বার তাগিদ দেবেন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ‘মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দলসমূহের সমন্বয়ে সর্বদলীয় সরকার গঠন করবার।’ সর্বদলীয় অর্থাৎ ত্রিদলীয়, আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও মস্কোপন্থী ন্যাপ; এবং ১৯৭৪ সালে আরও এগিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বলবেন : ‘আপনি কৃষক, শ্রমিক তথা মেহনতী মানুষের স্বার্থে যে কোনো পরিবর্তন আনবেন আমরা তাকে সমর্থন দেব।’৩১ এবং সত্য এটাও যে দু’মাস পরে বাকশাল গঠিত হলে নিজেদের দলকে বিলুপ্ত করে দিয়ে তাঁরা বাকশালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন।
চলবে…
তথ্যসূত্র:
১৪. ডা. এম. এ. করিম, ঢাকা সেন্ট্রাল জেল : নানা রঙের দিনগুলি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ ১৩
১৫. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৪
১৬. শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা, ঢাকা, ২০১৭, পৃ ১০৩-০৪
১৭. ঐ, পৃ ১০৫-১০৬
১৮. মোহাম্মদ তোয়াহা, পৃ ৪০
১৯. অলি আহাদ, পৃ ৪৪-৪৫
২০. ঐ, পৃ ৭৫
২১. ঐ, পৃ ৩০৮
২২. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯
২৩. অলি আহাদ, পৃ ৪৭৭
২৪. মোহাম্মদ তোয়াহা, পৃ ১০৬
২৫. অলি আহাদ, পৃ ২৪৮
২৬. ঐ, পৃ ২৪৭
২৭. ঐ, পৃ ২৪৮
২৮. ঐ
২৯. ঐ, পৃ ২৫৬; শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০
৩০. মোস্তাফিজুর রহমান, পৃ ৩২
৩১. ঐ, পৃ ২১১